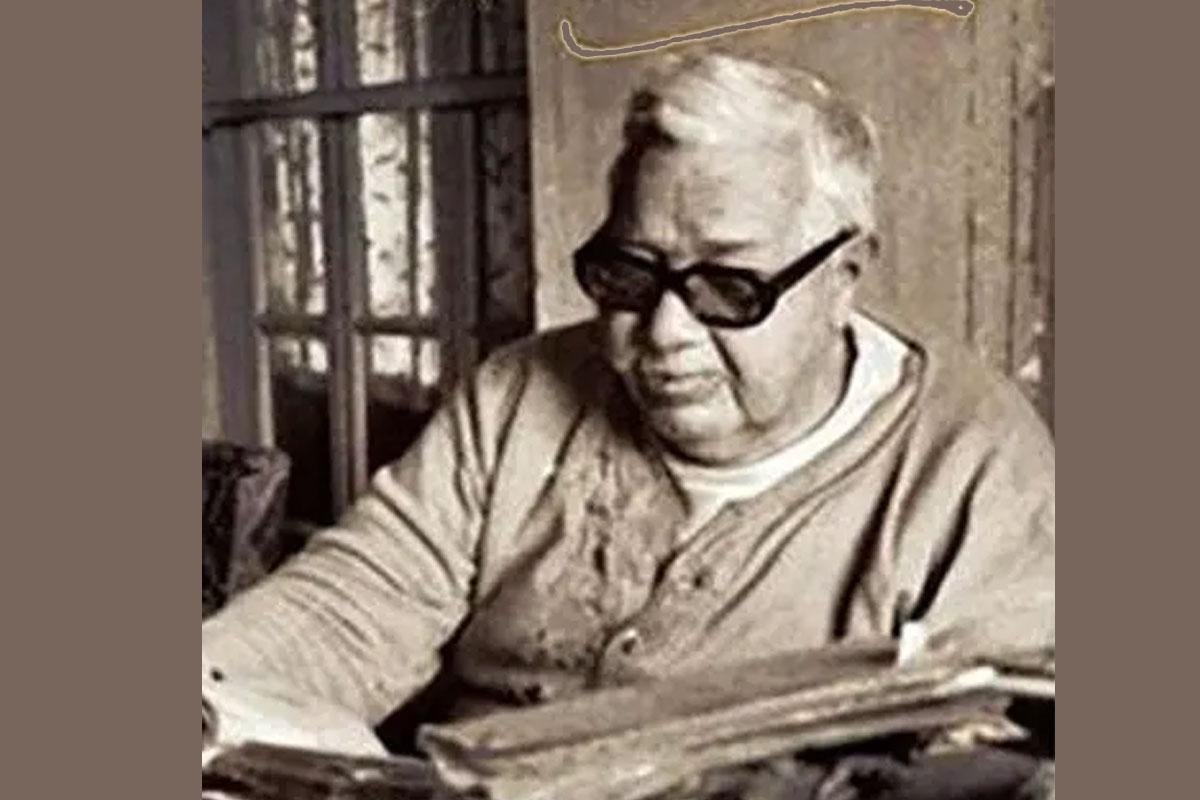অনেকটা সবুজ অনেকটা পৃথিবী নিয়ে ঝাড়্গ্রাম। দুপাশে শাল জঙ্গলের পথ চিরে মসৃণ পথ। হেমন্তের যাই যাই মরসুমে ঝাড়গ্রাম সফরটা আরও স্বপ্নিল করে তুলছিল। লাল পাথুরে জমিন, শাল, পলাশ, মহুয়া, কেন্দু, পিয়াশাল, শিমুল, সেগুনের গন্ধমাখা পথের প্রতিটি বাঁক। অদ্ভুত মায়াময় ডুলুং নামের মিষ্টি এক নদী। মুহূর্তরা বেবাক ছড়িয়ে রয়েছে শাল জঙ্গলের ওপারে। নম্রতা মেখে সকাল-বিকেল পাশে এসেচুপটি করে বসে। শহুরে কোলাহল ক্লান্ত জীবনের একঘেয়েমি ত্থেকে দিন দুয়েকের অবকাশ যাপনের আদর্শ ঠিকানা করে চলে এসেছি পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশহর ঝাড়গ্রাম। সীমানা লাগোয়া রাজ্য ঝাড়খন্ডও ওড়িশা। উত্তরে বেলপাহাড়ি কাকড়াঝোড়ের কাছে লাকাইসিনি, জামাইমারি, গাররাসিনি ইত্যাদি পাহাড়ের সারি ও দক্ষিণে সুবর্ণরেখা নদী তাকে নিরিবিলি দিচ্ছে।
কলকাতা থেকে বেশ ভোর থাকতেই রওনা হয়েছি ঝাড়গ্রামের পথে। দূরত্ব খুব বেশি কিছু নয়, মাত্র ১৬৩.৩ কিলোমিটার। কার্তিক-অঘ্রাণের একটা আমেজ রয়েছে। একটু একটু শীত জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ভালোই লাগছে। আজ কালিপুজো। বিদ্যাসাগর সেতু, কোনা এক্সপ্রেস-ওয়ে, উলুবেড়িয়া ইত্যাদি পেরিয়ে কোলাঘাটের এক পথচলতি ধাবায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে জমিয়ে প্রাতরাশ সারতে সারতেই ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা। অপূর্ব মসৃণ পথ। খড়গপুর পেরতেই লালমাটির পথ শুরু হলো। দুইধারে ঘন বুনোট, লোধাশুলি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সড়ক ৬ ধরে চলেছি। ডানদিকে বাঁক নিয়ে, রাজ্য সড়ক ধরে কিছুটা গেলেই ঝাড়গ্রাম। অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রামের হাতছানি আহ্বানকে উপেক্ষা করার সাধ্য কী। জম্পেশ এক আস্তানা আগেই ঠিক করা ছিল। ‘ঝাড়গ্রাম প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র’। চমকের তখনও বাকি ছিল, যখন বনদপ্তরের খাতায় সইসাবুদ করে আমাদের নির্ধারিত কটেজ ‘সুবর্নরেখা-২’ তে সেঁধোলাম। সাজানো গোছানো পরিপাটি বেশ বড় ঘর। পেছনে শাল জঙ্গলের মুখাপেক্ষী একচিলতে বারান্দা। কটেজের সামনেও লাল সিমেন্ট বাঁধানো একফালি বসার জায়গা। এখানে মোট তিনটি যুগল কটেজ রয়েছে। তাদের নামগুলি এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলা তিনটি নদীর নামে। সুবর্ণরেখা, ডুলুং, কংসাবতী। বেশ একটা অরণ্য অরণ্য ভাব রয়েছে সমস্ত পরিবহে।
সাঁওতাল, কুড়মালি, মুন্ডা, লোধা, ভূমিজ, শবর প্রভৃতি আদিবাসীদের বাস ৭৯ গ্রাম পঞ্চায়েতসহ পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশহর ঝাড়গ্রামে। ঝাড়গ্রামের অতীত ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। ১৫৯২ সালে আকবরের সেনাধিপতি অম্বরের রাজা মানসিংহ যখন বাংলা দখল করতে আসেন, তখন অঞ্চলটির নাম ছিল ‘ঝাড়ি খন্ড’। মল্লদের রাজত্ব ছিল তখন এখানে। গুপ্ত ও মৌর্য যুগেও মল্ল রাজাদের খ্যাতি ছিল খুব। মান সিংহের সেনাপ্রধান রাজপুত সর্বেশ্বর সিংহ যুদ্ধে পরাজিত করেন মল্লরাজকে। ফলত বাংলা-বিহার-ওড়িশার বহুলাংশই মান সিংহের আয়ত্বে আসে। পুরস্কারস্বরূপ মান সিংহ, এই জঙ্গলখণ্ড ও সংলগ্ন কিছু অঞ্চলের দায়িত্ব সর্বেশ্বরকে দিয়ে ফিরে যান। মল্লরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন বলে সর্বেশ্বরের নতুন নামকরণ হয়, রাজা সর্বেশ্বরমল্ল উগল সণ্ড দেব। ইদানিং আধুনিক শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু কিছু অঞ্চলে গাছপালা নিধন করে বাড়িঘর, রিসর্ট, হোটেল গড়ে উঠছে ক্রমশ।
বাইরে বেড়াতে এসে দিনের আলো থাকতে থাকতে হাতে পাওয়া সময়টুকু নষ্ট করতে মোটেই ইচ্ছে নেই। দুপুরে বনআবাসের খাবার ঘরে কাচের বাসনে ধোঁয়াওঠা গরম সরু চালের ভাত, ঝিরিঝিরি আলুভাজা, মুসুর ডাল, আলুপোস্ত, কাতলা মাছের ঝাল, টম্যাটোর চাটনিসহ মধ্যাহ্ন আহারের পর বিছানায় একটু গড়িয়ে, গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম ‘ঝাড়গ্রাম জুয়োলজিকাল পার্ক’। যেটি ‘ডিয়ার পার্ক’ নামেই সমধিক পরিচিত। ১৫ টাকা প্রবেশমূল্য। প্রথম দিকে এটি একটি চিড়িয়াখানা ছিল। বর্তমানে আয়তন বেড়েছে, স্থান হয়েছে আরও কিছু নতুন বণ্যপ্রানীর। বিশাল এলাকা জুড়ে গাছগাছালি ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রায় শতাধিক হরিণ। এছাড়াও রয়েছে নীলগাই, সজারু, কালো খরগোশ, বাঁদর, ময়ূর, চিতা, ভাল্লুক, এমু, কুমির, গন্ধগোকুল, হাতি ও বিভিন্ন পাখি। প্রতি বৃহস্পতিবার মিনি চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে।
পরের গন্তব্য ঝাড়গ্রাম থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে জামবনিতে প্রাচীন কনকদুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণ। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি খোদাই করা ঝাড়গ্রাম চৌরাস্তার মোড় থেকে বাঁদিকে বেঁকে গেল গন্তব্য পথ। ঝাড়গ্রাম-জাম্বুনি রোড ধরে চলেছি।
কংসাবতী ক্যানেল, দুবরাজপুর মোড়, ধরমপুর, টেংগা, শুষনি, কেন্দুয়া ইত্যাদি জনপদকে একে একে পেরিয়ে যাচ্ছি। তিন বা টালির চাল দেওয়া দোতলা মাটির বাড়ি। মাঝেমাঝেই পথ কেটে দ্রুত ছুটে এপার ওপার করছে গৃহস্তের মুরগি বা মোরগ। মুখ্যমন্ত্রী সড়ক যোজনা ও পি. ডবলু. ডি. দ্বারা নির্মিত দুপাশে সাদা বর্ডার দেওয়া অপূর্ব মসৃণ কালো পিচ পিছলানো পথ। কিছু গাছ পথের দুইধারে এমনভাবে ঝুঁকে রয়েছে, দূর থেকে ঠাহর হয়, যেন গাছের তোরণ। এককালে এই অঞ্চলগুলিই মাওবাদীদের উপদ্রুত ডেরা হিসেবে খ্যাত ছিল। এখন শান্ত। ঝাড়গ্রাম থেকে ৯ কিলোমিটার এসে, কেন্দুয়া নামের এক জনপদ। গড়শালবনী ও কেন্দুয়ায় পরিযায়ী পাখিদের শীতকালের আগে-পিছে মাস কয়েকের অস্থায়ী আস্তানা। মে মাস নাগাদ এরা আগাম বর্ষার খবর নিতে আসে, তারপর ফিরে যায়। তারপরই শীতের আগেই চলে এসে মৌরুসিপাট্টা জমায় কেন্দুয়ার জলচরে। পথের দুইপাশে অঘ্রাণের সোনালি ধানজমি। দেরিতে লাগানো ফসল কোথাও সবুজ হলেও, এই হেমন্তকালে ধান পেকে পুরুষ্ট হয়ে আছে হলুদ মাঠঘাট। কোথাও সোনালি ধান তোলা হচ্ছে। কোথাও ধানের আঁটি বেঁধে জড়ো করে রাখা। আসলে গ্রামীণ পথে যেতে যেতে সবুজ ধান খেত দেখতেই অভ্যস্ত চোখ। তাই হলুদ ধানজমি দেখে অন্যরকম লাগছে। এরপর ডেবরা, জাম্বুনি থানা, পোস্টঅফিস পেরিয়ে একটা মোড় এলো। তারপর পথনির্দেশ দেখে বাম দিকে আবার ঘুরে গেল আমাদের গাড়ি। কনকদুর্গা মন্দিরের ফটক পেরিয়ে গাড়ি ঢুকল পার্কিং-এর চৌহদ্দিতে। গাড়ি পার্কিং ফি বাবদ ৫০ টাকা ও জনপ্রতি ৫ টাকা প্রবেশমূল্যে ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলল।
প্রাচীন এই মন্দিরের অনেক অতীত গল্প। মন্দিরের পরতে পরতে ইতিহাস। লোকালয় বর্জিত মন্দিরের চারদিকে ৩৬৫ প্রজাতির বৃক্ষ ও ভেষজ লতাগুল্ম রয়েছে। আর রয়েছে রঙবেরঙের প্রজাপতি ও পাখি। টিকিট কাউন্টার থেকে মন্দির পর্যন্ত দুইধারে তারের জালির ওপারে লতাপাতা জড়ানো হরেক প্রজাতির বহু প্রাচীন কাষ্ঠল লতা, শাল, মহুয়া, আমলকী, হরতুকি, বহেড়া, কেন্দু, চালতা, রুদ্রাক্ষ, অশ্বথ, বট, পিপুল ছাড়াও বহু দুষ্প্রাপ্য ভেষজ তথা ঔষধি উদ্ভিদ। পরিচর্যার অভাবে মহার্ঘ্য সব ভেষজ উদ্ভিদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বর্তমানে বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। কথিত আছে দেবী মহামায়ার স্বপ্নদৃষ্ট হয়ে ১৭৪৯ সালে তৎকালীন রাজা শ্রী গোপীনাথ সিংহ মওগজ, স্ত্রীর হাতের কাঁকন দিয়ে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী এখানে ত্রিনয়নী, অশ্বে আরোহিণী। অষ্টধাতুর চতুর্ভুজা মূর্তি। ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে কিছু মিথ। স্থানীয়দের বিশ্বাস, গভীর জঙ্গল আচ্ছাদিত সামন্ত রাজাদের এই মন্দিরে আজও দুর্গাপুজোর অষ্টমীর রাতে দেবী নিজেই নিজের ভোগ রান্না করেন। দুর্গাপুজোর সময় ভিড়ে ছয়লাপ থাকে মন্দির চত্বর। বিজয়াদশমীর দিন ধুমধাম হয় প্রচুর। নবনির্মিত মন্দিরের সামনে হাঁড়িকাঠ। একসময় কনকদুর্গা মন্দিরে নরবলি হলেও এখন মোষ ও পাঁঠাবলি হয়। যে মন্দিরে পুজো হয়, গোলাপি রঙা সেই মন্দিরটি নতুন। পাশেই ৩০০ বছরের জীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। শোনা যায় ভয়াবহ বজ্রপাতে মন্দিরের মাঝ বরাবর ফাটল ধরে যায়। যেটি মন্দিরগাত্রটি দেখলেই বোঝা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়াও পার্শবর্তী ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি শুভকার্য সম্পাদনের জন্যও এই মন্দিরে এসে থাকেন।অশ্বথের ডালে বাঁধালাল হলুদ মনস্কামনার সবুজ-স্বপ্ন সুতোয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মুচলেকা পাঠানো। এখানে হনুমানের দৌরাত্তি খুব, ফলে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হয়।
ডুলুং নদীর ওপারেই ঐতিহাসিক চিলকিগড় রাজপ্রাসাদ। ধলভূমগড়ের সামন্ত রাজাদের বিশাল দোতলা রাজপ্রাসাদ। জামবনির ভূমিপুত্র ছিলেন সামন্তরাজ গোপীনাথ সিংহ। তাঁর একমাত্র জামাই, অর্থাৎ কন্যা সুবর্ণমনি স্বামী ধলভূমগড়ের রাজা জগন্নাথ দেও ধবলদেব জঙ্গলগড়ের এই রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। চিলকিগড় ছিল তাঁর রাজধানী। জগন্নাথ ধবলদেবের পুত্র কমলাকান্ত দেও ধবলদেবের সময়কে চিলকিগড়ের স্বর্ণযুগ বলা হতো। ডাইনে মূল রাজপ্রাসাদ, বাঁদিকে পরিত্যক্ত আরেকটি বৃহৎ বাড়ি, তাতে পরপর অনেকগুলি ঘর। তদানীন্তন বর্গি দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চারদিকে প্রাচীর ও তোরণদ্বার। উন্মুক্ত প্রান্তর অনেকটাই। বাঁদিকে এক প্রাচীন অশ্বথ গাছ। তার শেকড়ের কারিকুরি এমন যে গাছের কাণ্ডের এক জায়গায় গনেশ মূর্তির আদল নিয়েছে। সেখানেই ফুল মালা জল ঢালেন সংলগ্ন মন্দিরত্রয়ীর পুরোহিত। প্রচুর টিয়াপাখির বাসা সেই গাছে। চত্বরের মধ্যেই রয়েছে শিবমন্দির, গায়ত্রী মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির। সবচেয়ে বড় রাধাকৃষ্ণের মন্দির বা নবরত্ন মন্দির। প্রধান ফটকের পাশেই শিবমন্দির। অন্যটি গায়ত্রীমাতা মন্দির। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরগুলি একেবারে জরাজীর্ণ। তবু প্রাচীনত্বের ছাপ থাকায় ছবি তোলার পক্ষে বেশ আদর্শ। মোঘল ও ব্রিটিশ শৈলীর মিলিত স্থাপত্যে তৈরি রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে অন্যান্য কারুকাজের সঙ্গে বঙ্গীয় রীতির কল্পা কাজও নজরে পড়ে। এককালের জৌলুশ নিয়ে দ্বিতল অট্টালিকাটি সর্বত্র অবহেলার ছাপ নিয়ে আজও টিকে আছে। মূল প্রাসাদে বাস করেন রাজ পরিবারের বংশধরেরা। সেখানে প্রবেশ নিষেধ। ভেতরে এক কাঠি-আইস্ক্রিমওলা বিক্রির জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজেই জানাচ্ছিলেন মন্দিরগুলির ইতিকথা। এখানে অনেক সিনেমারও শুটিং হয়েছে। রাজবাড়ির বাইরে একটি বড় রথের কাঠামো রাখা রয়েছে। অন্য একটি ইতিহাসও প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই রাজপ্রাসাদের সঙ্গে। ঐতিহাসিক ‘চুয়াড় বিদ্রোহ’ চলাকালীন রাজা জগন্নাথ দেও এই চিলকিগড় রাজবাড়ি থেকেই ১৭৬৯ সালে ‘ধল বিদ্রোহ’ ঘোষণা করেছিলেন। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই বিদ্রোহ দমন করতে সফল হয়।
সুর্যাস্ত হবো হবো করছে। ডুলুং নদী এখন শান্ত নিরিবিলি। ফেরার পথ গাড়ি একপাশে রেখে নেমে পড়ি। ডুলুং সেতুর পাড়ে। নদীর জলরঙে সূর্যাস্তের নৈসর্গিক আলো। শেষ বিকেলের স্তিমিত রোদ্দুরের ওম্ জড়িয়ে তিরতির করে বয়ে চলা জীর্ণ নদী, অথচ বর্ষার সময় এই নদীরই কী রূপ। বড্ড ইচ্ছে করে নদীর কাছে দু’দণ্ড থাকার। ডুলুং-এর সঙ্গে গল্প করার সাধ হয় আমার। ফিরতি পথে আরও যেন রূপ খুলেছে এই পথের। সূর্য অস্ত গেলেও আলোর রোশনাই এখনও মজুদ। দূরে দূরে কিছু গ্রাম। গ্রাম শেষ হতেই আবার শালবনের শুরু। কখনও ধানখেত। সন্ধে নামার মুহুর্তে ফিরে আসি প্রকৃতি পর্যটনের অস্থায়ী ডেরায়। এক কাপ কফি নিয়ে জুত করে ঘর লাগোয়া পেছনের বারান্দায় বসি। মফস্বলি কোলাহলকে পেছনে ফেলে রাখা জঙ্গল ঘেরা পরিবহ। ঝিঁঝিঁর অস্ফুট ঐক্যতান। হেমন্তের সন্ধেকে বড় একা মনে হয়।
পরদিন সকালে পায়ে পায়ে চলে গেলাম ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি। মূল ফটক থেকে লাল ধুলোমাটির অনেকখানি পথ হেঁটে রাজবাড়ির দেউড়ি।
রাজকীয় ঠাটবাট নিয়ে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি। কিন্তু সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। যারা রাজবাড়ি প্রাঙ্গণেই থাকেন, তাদের জন্যই কেবলমাত্র রাজবাড়ির দ্বার খোলা। ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি ও পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এখানে পর্যটকাবাস নির্মিত হয়েছে। পিছনের প্রাসাদে রাজা সর্বেশ্বরের উত্তরসূরিদের বসবাস। ইসলামিক ও ইতালিয়ান গোথিক শৈলীতে অট্টালিকাটি নির্মিত। রাজবাড়ির ভেতর মন্দির, বাগান, বাঁধানো পুকুরঘাট ইত্যাদি রয়েছে। রাজবাড়ির ভেতর চার-মস্তক বিশিষ্ট শিবমন্দির, লোকেশ্বর, বিষ্ণু এবং মনসা মন্দির। ঝাড়গ্রাম রাজপরিবারের কুলদেবী সাবিত্রীমাতা। ৩৫০ বছরের প্রাচীন এই মন্দিরে কোনও দেবী মূর্তি নেই। একখণ্ড পাথরকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয়। দুর্গাপুজোর মহালয়া থেকে দশদিনব্যাপী এই মন্দিরে পুজো ও উৎসব চলে। অতীতে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে দেবরাজ ইন্দ্রের পুজোর রীতির প্রচলন ছিল। রাজা স্বয়ং সোনার পালকিতে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরতেন, প্রজাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। বাইরে থেকেই কয়েকটি ছবি তুলে ফিরে আসি।
প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যেই আনমনা ঘুরে ফিরে বেড়াই। দোলনায় দুলি। ছায়াভরা হেমন্তের অরণ্য। আমি অচেনা এক শালবৃক্ষের ছায়ায় এসে বসে থাকি। ঝাড়গ্রাম থেকে সারাদিনের সফরে ঘুরে আসা যায় কাছেপিঠে আরও কিছু দ্রষ্টব্য স্থান। ঝাড়গ্রাম থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে শাল পিয়ালের জঙ্গল ছাওয়া বেলপাহাড়ি আরও কিছু দূরে কাকড়াঝোড়। সময় সংক্ষেপ থাকায় এবার যাওয়া হয়নি জঙ্গল ও পাহাড়ের অপুর্ব শোভা নিয়ে বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি, কাঁকড়াঝোড়। বেলপাহাড়ি থেকে বাঁশপাহাড়ির পথে খাঁদারানি জলপ্রপাত, গাররাসিনি পাহাড়, লালজল গুহা দেখে নেওয়া যায়। বেলাপাহাড়ি বাজার থেকে অন্য পথে রয়েছে তারাফেনি জলাধার, ঘাগরা জলপ্রপাত। ঝাড়গ্রাম থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে গোপীবল্লভপুরে রামেশ্বর মন্দির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিশেল। কথিত আছে সীতার অনুরোধে, ভগবান বিশ্বকর্মার সহযোগিতায় এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামচন্দ্র। মন্দিরের স্থাপত্য এমনই যে, কোনও প্রকোষ্ঠ না থাকলেও এখানে সূর্যের আলো এসে পড়ে। লোককাহিনী আছে ঋষি বাল্মীকি এখানে বসেই রামায়ণ লেখা শুরু করেন। তবে এখন পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সামনেই স্থাপিত হয়েছে নতুন একটি মন্দির। দেখা না হওয়ার তালিকায় রয়ে গেছে ক্রিস গার্ডেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের অন্তর্গত আমলাচটি ভেষজ উদ্যান, বাঁদরভোলা আদিবাসী সংগ্রহশালা।
কলকাতা ফিরতি পথে, ঢুঁ মারলাম এক লুকোনো শিল্পগ্রাম, ‘খোয়াব গাঁ’। রেলস্টেশন থেকে কদমকানন রেলগেট পেরিয়ে বাঁদিকের পথ ধরে ক্যানেল পাড়ের রাস্তায় কিছুটা দূরেই ঝাড়গ্রাম তহসিলের রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ১৩টি লোধা আদিবাসী পরিবার নিয়ে ছোট্ট এক গ্রাম লালবাজার। গ্রামটির নতুন নামকরণ হয়েছে ‘খোয়াব গাঁ’। এই গ্রামটির বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালেই হাতে আঁকা সাদাকালো অথবা রঙিন চিত্র। একটা সময় জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছিল এরা, সেই কাঠ বেচেই চলত এদের ‘নুন আনতে পান্তাফুরনো’ দিনযাপন। বিকল্প জীবিকার খোঁজে, গ্রামে সবুজায়নে মেতে, এখন তারাই কাঠ ও মাটি দিয়ে ‘কাটুমকুটুম’ বানাচ্ছে, দেওয়ালগুলি সাজিয়ে তুলেছে যেন এক একটি আস্ত ক্যানভাস। হাঁ হয়ে দেখছিলাম সব। গ্রামের শবর লোধা জনজাতির বাচ্চাগুলোও তাদের কৌতূহলী সরল চাউনিতে দেখছিল আমাদের। কলকাতা অভিমুখে গাড়ি ঘোরাই। সন্ধের মধ্যেই ফিরতে হবে। দিনযাপনের সাংসারিক জোয়ার-ভাঁটা সামলাতে ফিরতেই হয়।