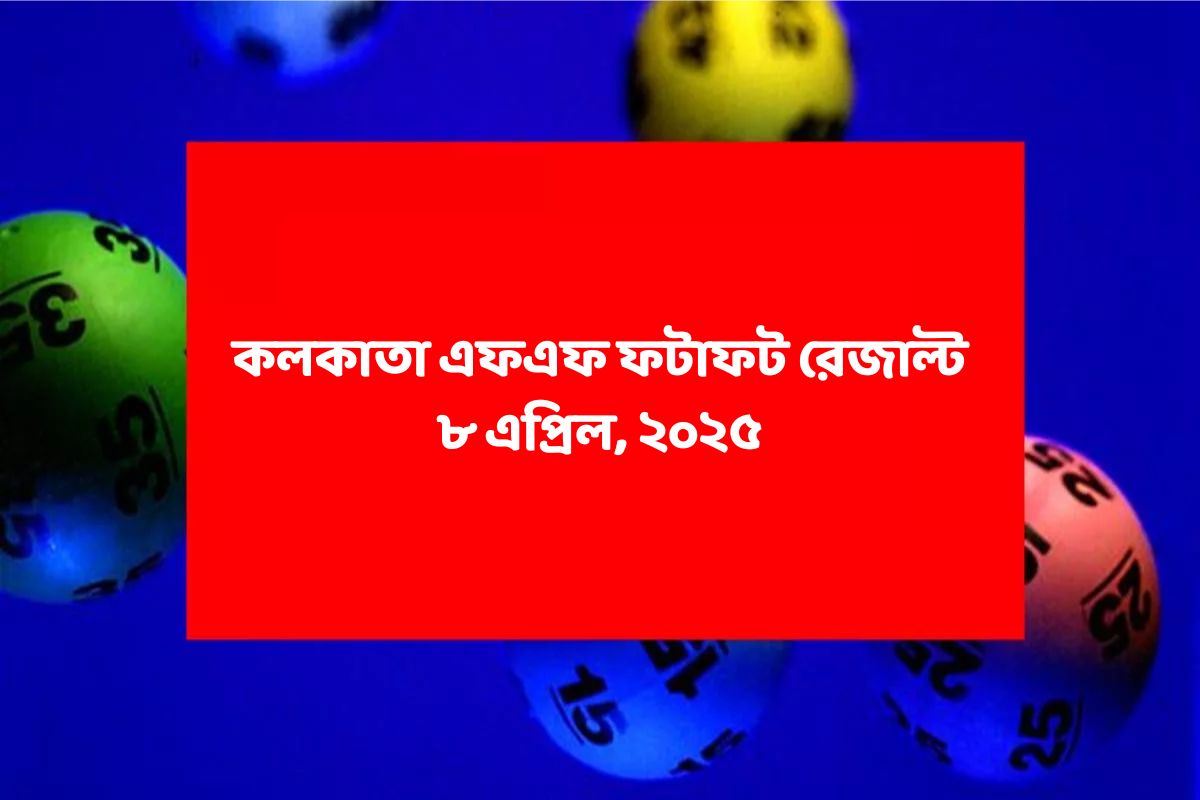বছরের প্রায় বেশিরভাগ সময়টা কখনো বা প্রখর দাবদাহ আবার কখনো বা নাভিশ্বাস ওঠা ভ্যাপসা গরমে কাটানোর পর রাঢ় বঙ্গের বাতাসে হিমেল আবেশ মানেই এক আলাদা খুশির রেশ। আর এই বড়ো আদরের মরশুমকে আরো বর্ণময় করে তুলতে প্রায় এই হেমন্ত আর শীত ঋতু জুড়েই স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে নানান লোকাচার, লোক উৎসব। রাঢ়ের এই সময়কার লোক উৎসবের এক অন্যতম উৎসব হোল ‘ইতু পূজা’।
কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত রাঢ়ের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই পালিত হয় এই উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার, বাড়ির মহিলারা সকাল সকাল স্নান করে, শুদ্ধ উপাচারে, সারাদিন নিরামিষ খাবার খেয়ে পুজো করেন ইতু দেবতার, ইতুর ঘটে জল ঢালার সময় উচ্চারণ করেন শ্লোক ‘ইতু ইতু নারায়ণ /তুমি ইতু ব্রাহ্মণ / তোমার শিরে ঢালি জল / অন্তিম কালে দিও ফল।’
সাধারণ ভাবে মনে করা হয় ইতু পূজা হোল মহিলাদের সূর্য আরাধনার এক লোকাচার। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে, এই অবস্থানে সূর্যের নাম মিত্র। বলা হয়, মিত্র শব্দটিই মিতু থেকে পরিবর্তিত হয়ে ইতু শব্দটি এসেছে। কেউ কেউ আবার মনে করেন সূর্যের অপর নাম আদিত্য, সেই আদিত্য থেকেই ইসেছে ইতু নামটি। অবশ্য ইতু পুজোকে সূর্যের উপাসনা বলা হলেও এই পুজোর রীতি ও আনুষঙ্গিক বিষয় লক্ষ করে ইতুকে অনেকেই মাতৃদেবী রূপেই মেনে থাকেন। তবে অধিকাংশের মতে, ইতু পূজা করা হয় শস্যবৃদ্ধির কামনায়, শস্যবৃদ্ধির উৎসবই হোল ইতুপুজা, কারন এই সময়টা রবিশস্য চাষের সময়, তাছাড়া ইতু পূজায় ব্যবহৃত নানান অঙ্কুরিত শস্য দানা দেখে মনে হয় ফসল বৃদ্ধির উৎসবই হোল ইতুপুজা। শস্য বৃদ্ধির কামনায়, সূর্য দেবতা ইতু ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছেন ফসলের দেবী লক্ষ্মীতে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন কালে কৃষক শ্রেণীর কাছে, কৃষিকার্যের সমৃদ্ধিতে সূর্য পূজার সাথে সাথে ইন্দ্রপূজার ভূমিকাও ছিল অপরিসীম তাই ইতু হলেন সূর্য ও ইন্দ্রের সংমিশ্রনে গড়ে ওঠা এক লৌকিক দেবী, গৃহী রমণীরা ফসল বৃদ্ধি ও সংসারের অনটন মুক্তির কামনায় যার পুজো করে থাকেন।
একটি খড়ের বিড়া প্রস্তুত করে তার ওপর একটি মাটির সরা রেখে সাধারণত বাড়ির একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে অথবা বাড়ির তুলসী তলায় স্থাপন করা হয় ইতু, স্থানীয় ভাবে যাকে বলা হয় ইতু পাতা। মাটির সরার মাঝে রাখা হয় কিছুটা পরিষ্কার মাটি, কেউ কেউ আবার গঙ্গা মাটিও মিশিয়ে দেন এই মাটির সাথে। সেই মাটিতে শেকড় শুদ্ধ ধান, মান, কচু,হলুদ, শুশনিশাক কলমীশাক, সর্ষে ইত্যাদি গাছ পুঁতে তার চারদিকে ছোট ছোট পাঁচটি বটের ডাল পোঁতা হয়, আর ঠিক তার মাঝখানে স্থাপন করা হয় একটি জলপূর্ন ঘট। সেই ঘটে বাড়ির মহিলারা কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে শুধু করে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবার জল ঢেলে পূজা করেন। অবশেষে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন নিকটবর্তী কোন নদী বা পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয় ইতুর ঘট।
ইতু পূজা হোল একান্ত ভাবেই মহিলা কেন্দ্রিক পূজা। এমনকি ইতু পূজায় কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না,নেই কোন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারন। বাড়ির মহিলারাই করে থাকেন এই পূজা। ইতু পুজোর নৈবেদ্য হোল চাল আর কলাই। ভোগ হোল চাল-কলাই ভাজা, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয়, ভাজাপোড়া। সংক্রান্তির দিন অবশ্য ইতুর বিশেষ ভোগ হিসাবে থাকে আঁসকা পিঠে বা আঁসকা বড়া, যা মহিলারাই প্রস্তুত করেন মাটির সানকি-সরায় এক সুন্দর পদ্ধতিতে।
কোথাও কোথাও আবার ইতু পূজা শেষে আছে ব্রত কথা শোনার নিয়ম, সাধারণ ভাবে পাড়ার কোন ব্রাহ্মণীর কাছে মহিলারা সকলে মিলে শুনতে যান ইতুর ব্রতকথা। ব্রতকথা বলা শুরু করার আগে, ব্রাহ্মণী ছড়া কাটেন, ‘অষ্টচাল অষ্টদূর্বা কলস পাত্রে থুয়ে / ইতুর কথা শুন সবে মনপ্রাণ দিয়ে।/ইতু দিলেন বর/ পুত্র পৌত্র ধনধান্যে বাড়ুক তাদের ঘর।’
ইতু পূজার ব্রতকথাটিও বেশ আকর্ষণীয়। কোনও এক গ্রামে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও তাদের দুই মেয়ে উমনো আর ঝুমনো। একদিন সেই ব্রাহ্মণ জোগাড় করে নিয়ে আসেন আঁসকা পিঠের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ব্রাহ্মণীকে নির্দেশ দেন পিঠে বানানোর জন্য, সাথে এও বলেন যে যতগুলি পিঠে হবে তার সবগুলিই যেন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণী শুরু করেন পিঠে বানাতে, ওদিকে অন্য ঘরে বসে ব্রাহ্মণ শুনতে থাকেন তপ্ত মাটির সরায় পিঠে তৈরি করার ছেঁক ছেঁক শব্দ। যতবার শব্দ হয় তার মানে ততগুলি পিঠে প্রস্তুত, আর সেই হিসাবে ব্রাহ্মণ একটি কাপড়ে দিতে থাকেন একটি একটি করে গিঁট। পিঠে তৈরি করতে করতে ব্রাহ্মণী দেখেন পিঠে গুলির দিকে করুন নয়নে তাকিয়ে আছে উমনো আর ঝুমনো। কেঁদে ওঠে মায়ের মন, ব্রাহ্মণের নির্দেশ ভুলে একটি পিঠে তুলেদেন মেয়েদের হাতে। রাত্রে খেতে বসে ব্রাহ্মণ হিসেব করে দেখেন যে একটি পিঠে কম। কুপিত ব্রাহ্মণ সেই রাত্রে আর কারোকে কিছু না বলে, পরের সকালে উমনো ঝুমনোকে তাদের পিসির বাড়ি নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে এক গভীর জঙ্গলে। গভীর জঙ্গলের মাঝে অসহায় দুই মেয়ে কান্নাকাটি করতে করতে অবশেষে এক বটবৃক্ষের কোটরে রাত কাটিয়ে, পরের সকালে আবার উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথ চলা শুরু করার পর, এক স্থানে গিয়ে দেখেন কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে কোনোকিছুর পুজো করছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে উমনো ঝুমনো বল নিজেদের দুঃখের কথা, সেই মহিলারা তখন তাদের জানায় ইতু দেবীর মাহাত্ম সম্পর্কে ও পরামর্শ দেন তাদেরও ইতু পূজা করার। সেই মহিলাদের কথা শুনে উমনো ঝুমনোও করে ইতুপুজা, ইতু দেবীর কাছে বর চান নিজেদের ও পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। পুজো করার পর বাড়ি ফিরে আসে উমনো ঝুমনো, এর পর আরো ওঠাপড়া ও নানান ঘটনাপঞ্জির মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দুই বোন, ইতু দেবীর কৃপাদৃষ্টিতে সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয় তাদের পরিবার, ধীরে ধীরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ইতু পূজার মাহাত্ম।
ইতু পুজো জুড়ে আরো রয়েছে নানান নিয়ম, যেমন কেউ একবার ইতু পূজা শুরু করলে যতক্ষন না পর্যন্ত ইতু অন্য কারো হাতে তুলে দিচ্ছে ততদিন সে ইতু পূজা বন্ধ করতে পারে না, এমনকি কোন বাড়িতে একবার ইতুপুজা বন্ধ করলে সে বাড়িতে আর ইতু পূজা শুরুও করা যায় না। তবে বর্তমানে রাঢ় বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ইতু নিয়ে সেই জনপ্রিয়তা আর চোখে পড়ে না, মরশুম ব্যাপী ইতু নিয়ে উন্মাদনা আজ অনেকটাই অস্তমিত। আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় মানুষ আজ বর্জন করেছে তদানীন্তন ধ্যানধারণা, লোকাচার। ভাটা পড়েছে সমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে থাকা নানান লোক উৎসবে। আধুনিক সমাজের কাছে লোক দেবদেবীরা আজ যেন অনেকটাই ব্রাত্য। মোবাইল আর বোকাবাক্সের যুগে, নেই আজ শীতের আদুরে রোদ গায়ে মেখে ব্রতকথা শোনার চল। তবুও সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও, আজও রাঢ়বঙ্গে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু মানুষ এখনো বহন করে চলেছে পুরাতনী লোকাচারের ধারা। সংসারের মঙ্গল কামনায়, সেই তেমনি কিছু মানুষ এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন বড়ো আদরের নারী কেন্দ্রিক লোক উৎসব, ইতুপূজা। তাই এখনো রাঢ়ে বিশেষ করে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে কোথাও না কোথাও অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন শোনা যায়, ‘কাটি মুটি কুড়াতে গেলম/ ইতুর কথা শুন্যে আইলম/ তা শুনল্যে কি হয়? / নির্ধনেরও ধন হয়।’