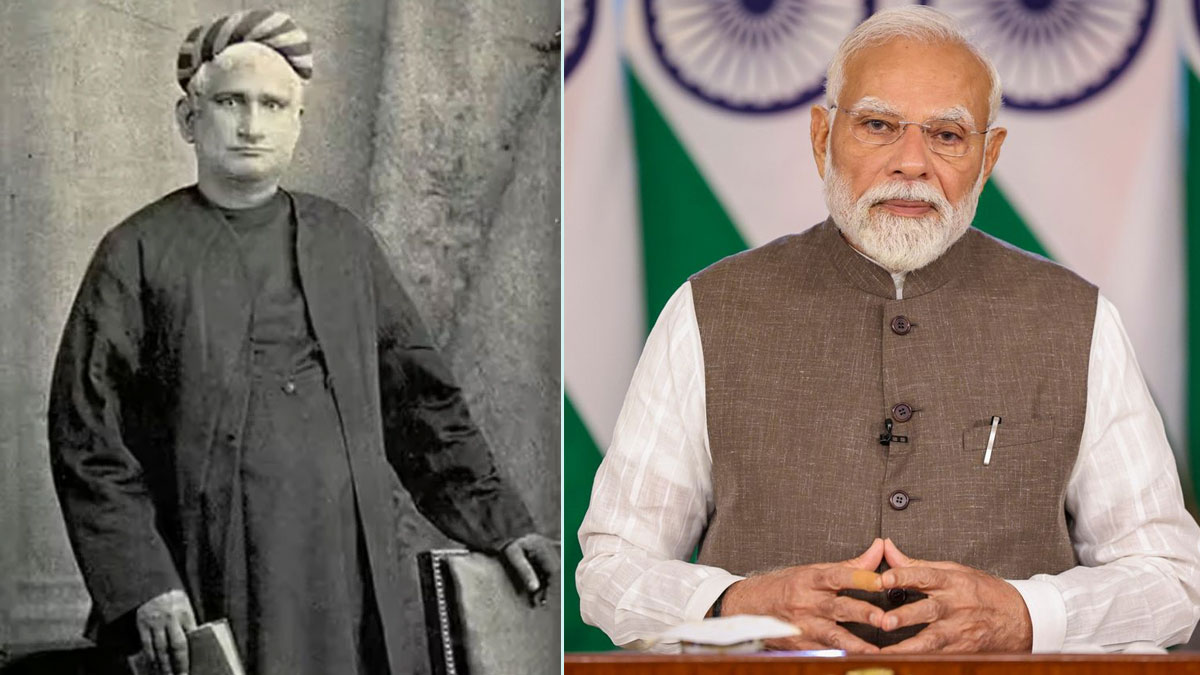মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়
বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলা৷ এদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যে প্রায় প্রতিটি মাসকে কেন্দ্র করেই উৎসব আর উৎসব৷ শহুরে মানুষের কাছে সমস্ত বাঙালি উৎসবের বার্তা হয়তো সেভাবে পৌঁছয় না, কিন্ত্ত জেলাভেদে অঞ্চলভেদে আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে বহুতর উৎসবের স্রোত৷ এগুলির মধ্যে কোনওটা বা ধর্মীয় উৎসব, কোনওটা সামাজিক ও নিতান্তই স্থানীয়, আবার কোনওটার চরিত্র একেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ৷ বাংলার ভূগোল আজ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে দ্বিধাবিভক্ত৷ পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, দিল্লিতে বহু বাঙালির বাস৷ বিশ্বায়নের কল্যাণে ইওরোপ-আমেরিকাতেও, এমনকি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে বসবাসরত মোট বাঙালির সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ৷ পাকিস্তান ১৯৭১-পরবর্তী কালে পূর্বপকিস্তান-বর্জিত ডানাকাটা রাষ্ট্র৷ সেখানেও কিন্ত্ত রয়ে গেছেন প্রচুর সংখ্যক বাঙালি৷
Advertisement
বাঙালির উৎসব-সংখ্যা গণনার অতীত৷ একথার প্রমাণ মিলবে যেকোনও একটি পঞ্জিকার পাতা ওলটালে৷ বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদির কথা হচ্ছে না, হচ্ছে না শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, চল্লিশা কিংবা উরস-এর কথাও৷ এ ছাড়াই প্রায় প্রতিটি দিনই দেখা যাবে উৎসবের দ্বারা চিহ্নিত লগ্ন৷ একমাত্র পৌষসংক্রান্তির দিন বঙ্গদেশময় যে জলধিপ্রতিম উৎসব, তা-ই আমাদের আশ্চর্য না করে পারে না৷ বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) সেদিন মল্লরাজদের বৈষ্ণব ধর্মমতে ব্রত উদযাপিত হয়৷ প্রসঙ্গত, বিষ্ণুপুরে মল্লরাজারা একনাগাড়ে চোদ্দোশো বছর রাজত্ব করে গিয়েছেন৷ ওইদিন বীরভূমের ইলামবাজারে আবার কদম্বখণ্ডীর ঘাটে পুণ্যস্নান উদযাপিত হয়৷ তাছাড়া কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলা তো ওইদিন সুপ্রসিদ্ধ৷ বাংলার সাঁওতাল সমাজও পৌষসংক্রান্তিতে মেতে ওঠেন ‘নাগরদোলা’ পরবে৷ পুরুলিয়ায় এসময় হয় টুসু উৎসব৷ মেদিনীপুরের কাঁথিতে রসুলপুর নদীকে কেন্দ্র করে উৎসব ও মেলা বসে, যে রসুলপুরকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে স্থান দিয়ে নদীটিকে অক্ষয় করে রেখে গিয়েছেন৷
Advertisement
তো এই গেল একটি দিনের উৎসবের বিবরণ, তা-ও আংশিক৷ উৎসব প্রধানত দু’ধরনের৷ ধর্মীয় আর সামাজিক বা ধর্মনিরপেক্ষ৷ দুর্গ কালী শিব সরস্বতী পুজো, ঈদ, মহরম (এটি উৎসব নয়, শোক উদযাপনের দিন), ফতেহা দোহাজ দাহাম, বুদ্ধজয়ন্তী, কঠিনচীবরদান, প্রবারণা উৎসব, বড়দিন, গুড ফ্রাইডে৷ অন্যদিকে রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নজরুল জন্মোৎসব, নববর্ষ (ইংরেজি ও বাংলা) হল ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক উৎসব৷
পৃথিবীতে ত্রিশ কোটি বাঙালি৷ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে, বাংলা নববর্ষ পালিত হয় আলাদা দুটি দিনে৷ তার কারণ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৮-তে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলা বর্ষপঞ্জির যে সংস্কার হয়, তাতে ইংরেজি ১৪ এপ্রিলকে বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ পয়লা বৈশাখকে স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল৷ কিন্ত্ত পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে এই সংস্কার মান্যতা পায়নি৷ তাই কখনও একদিন, কখনও দুদিনের ব্যবধান ঘটে যায় দু-দেশের যাপিত উৎসবে, বিশেষ করে যা বাংলা বর্ষপঞ্জির নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক৷ তবে তিথিভিত্তিক উৎসবগুলি একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়৷ এবং সেখানেও গোলমাল৷ যেমন ১৪২৩-এ যে দুর্গোৎসব হয়, ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী তা ছিল ৬ থেকে ১০ অক্টোবর, পঞ্চমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত৷ কলকাতা, ঢাকা দুজায়গাতেই ইংরেজি তারিখ এক রেখেই পুজো হয়েছে, প্রতিমা বিসর্জিত হয়েছে ১১ অক্টোবর (অনেকে বিলম্বিত বিসর্জন ঘটান, সেটা আলাদা৷ কিন্ত্ত বাংলা তারিখ ছিল কলকাতার ১৯-২৪ আশ্বিন (পঞ্চমী-দশমী) আর ঢাকার ২০-২৫ আশ্বিন৷ রবীন্দ্রজয়ন্তী বাংলাদেশে একদিন আগে উদযাপিত হয়, নজরুলজয়ন্তীও৷ একইরকমভাবে বাংলা নববর্ষও৷ কেন এমন বৈষম্য?
এটা বোঝার জন্য আমাদের বাংলা সনের জন্ম-ইতিহাস একটু জেনে নিতে হবে৷ কবে এবং কীভাবে বাংলা সন চালু হল?
বাংলা সনের জন্মকাহিনি
গ্রিক প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি শিশু হয়ে জন্মাননি, জন্মেছিলেন যৌবনবতী হয়ে৷ ঠিক তেমনই বাংলা সন খ্রিস্টাব্দ বা হিজরি সনের মত এক থেকে শুরু হয়নি, জন্মেই বাংলা সনের বয়স ৯৬৩৷ কীভাবে ঘটল এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটি?
এটা জানতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে ভারতেতিহাসের মধ্যযুগে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে৷ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকবরের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা বলে শেষ করার নয়৷ সর্বধর্মসমন্বয়কারী আকবর যে ‘দীন-ই-ইলাহী’ ধর্মের প্রচলন করেন, সে ধর্মীয় উদারতা আজকের দিনেও বিরল৷ ১৫০৩-এ তিনি সতীদাহ প্রথা রদের উদ্যোগও নিয়েছিলেন, রাজা রামমোহনের বহু পূর্বে৷ অক্ষরজ্ঞানহীন আকবর সম্পর্কে আরও একটি কৌতূহলকর তথ্য হল, পণ্ডিতদের মুখে মহাভারতের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে তিনি ফার্সিতে এই মহাকাব্যটি অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন৷ আকবর কথাবার্তা বলতেন ফার্সিতে, এবং মুখে মুখে বলে যেতেন, আর তা লিখে নিতেন মুনসিরা৷ হাজার ব্যস্ততায়, যুদ্ধের পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় মহাভারতের খুব সামান্য অংশই অনূদিত হতে পেরেছিল৷ আমরা তবু আকবরের উদার মানসিকতার কাছে নতজানু না হয়ে পারি না৷ আজকের ভারত আকবরের কাছে লজ্জা পাবে!
যাই হোক, আকবর দেখলেন, বার্ষিক খাজনা আদায় ইসলামি অর্থাৎ হিজরি সাল মেনে করতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে৷ কারণ হিজরি বছর চান্দ্রবৎসর বলে ৩৫৪ দিনের৷ ৩৬৫ দিনের বছর তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়ল৷ এ-জাতীয় বছর কিন্ত্ত ভারতে বহাল ছিল তখন৷ তার নাম শকাব্দ৷ প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির ও আর্যভট্টের গণনা পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিল৷ শকাব্দ সেই গণনা অনুযায়ীই বিধিবদ্ধ হয়৷ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নিয়ে ইরানের কবি ও গণিতজ্ঞ ওমর খৈয়ামও কোপার্নিকাসের বহু আগে একাদশ শতাব্দীতেই নির্ভুল নির্ঘণ্ট বের করেছিলেন৷
আকবর শকাব্দ অনুসারী হলেন না৷ আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত জ্যোতিষী ফতেউল্লাহ সিরাজীর পরামর্শে আকবর তাঁর সিংহাসন আরোহণের ইসলামি বর্ষ ৯৬৩-র সঙ্গে ‘ফসলী সাল’-কে মিলিয়ে দিলেন৷ একে ‘ইলাহী সাল’-ও বলা হত, সম্রাটের ‘দীন-ই-ইলাহী’ ধর্মমত স্থাপনের অনুকরণে৷
এ তো গেল বাংলা সনের জন্মকাহিনি৷ এরসঙ্গে বাংলা নববর্ষ পালনের যোগসূত্র কোথায়? কী মধ্যযুগে, কী ব্রিটিশ আমলের গোড়ায়, বাঙালি পয়লা বৈশাখ যে নববর্ষ পালন করেছে, তার প্রমাণ নেই৷ একদা ভারত তথা বাংলায় বর্ষ শুরু হত অগ্রহায়ণ মাস থেকে৷ চৈত্র মাস থেকেও বর্ষগণনা প্রশস্ত ছিল৷ শকাব্দ সেই চৈত্রমাসের বছরকেই মান্যতা দেয় আজও৷ তাহলে পয়লা বৈশাখে যে নববর্ষ, তার উদ্ভব কবে থেকে এবং কীভাবে? মধ্যযুগে নারীদের বিরহবেদনা বিধৃত হয়ে আছে অসংখ্য কবির বারোমাস্যায়৷ সেখানকার বর্ণনায় বৈশাখের কথাও রয়েছে, কিন্ত্ত উৎসবপালনের কথা নেই একেবারেই৷ মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারোমাস্যায় (ইনি প্রবলভাবে আকবরের সমসাময়িক) আশ্বিনে দুর্গাপূজার উল্লেখ করছেন— ‘আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে৷/ ছাগ মেষ মহিষ দিয়া বলিদানে৷৷’ কিন্ত্ত বৈশাখে কোনও উৎসবের উল্লেখ নেই৷ রয়েছে মাংসভক্ষণের নিষেধ-বার্তা,— ‘বৈশাখ হৈল বিষ গো বৈশাখ হৈল বিষ৷/ মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ৷’ যেমন মাঘ মাসে শাকপাতা বর্জন করত লোকে, ‘নিদারুণ মাঘমাস, নিদারুণ মাঘ মাস৷/ সর্ব্বজন নিরামিষ কিংবা উপবাস৷৷’ একই সময়ে শ্রীচৈতন্য দোল-উৎসবে মাতোয়ারা, কিন্ত্ত কী চৈতন্য ব্যক্তিজীবনে, কী সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যে পয়লা বৈশাখ আদৌ উল্লেখযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত নয়৷ বৈশাখে নালিতা খাওয়া প্রশস্ত, আর মধ্যযুগে মুসলমান মহিলা কবি রহিমুন্নিসার ‘ভ্রাতৃবিলাপ’-এ অন্য একধরনের বারোমাস্যায় পাই কেবল এই তথ্য, ‘বৈশাখ মাস কাটাইলাম আমি বৈসারে বৈসারে৷’
তাহলে বাংলা নববর্ষপালনের সূচনা কবে?
আমাদের ধারণা, ওই যে খাজনা আদায়ের সুবিধের জন্য ফসলী সন হিসেবে বাংলা সনের প্রবর্তন, তারই বিবর্তিত রূপ ‘পুণ্যাহ’৷ ঔপনিবেশিক আমলে কঠোরভাবে জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হত, ‘সূর্যাস্ত আইন বা ‘Sunset Law’-এর মাধ্যমে৷ জমিদাররাও তাই বাধ্য প্রজাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট তারিখে অর্থ আদায়ে, খাজনা হিসেবে৷ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-য় চড়কের বিচিত্র ও বিশদ বর্ণনা দিচ্ছেন, আর পয়লা বৈশাখ বর্ণনা করছেন একটিমাত্র বাক্যে, ‘খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন৷’ খাতাওয়ালা, অর্থাৎ জমিদার এবং তৎসহ সদ্য গড়ে ওঠা বেনিয়া সম্প্রদায়৷ পয়লা বৈশাখ তাই গোড়ায় ছিল জমিদার-মুৎসুদ্দির বার্ষিক দেনাপাওনার হিসেব মেলানোর দিন৷ মুঘল আমলে ইরানীয় প্রভাবে ‘নওরোজ’ পালিত হত ধুমধাম করে, পাঞ্জাবে এসময়ে ‘বৈশাখী’ পালিত হওয়া শুরু হয় গুরু গোবিন্দ সিংয়ের ‘খালসা’ গঠনের মাধ্যমে, আর আসামেও ‘রঙ্গালি বিহু’ বৈশাখ মাসকে কেন্দ্র করে৷ বাংলায় নবান্ন ছিল, নববর্ষের উদযাপন সেই অর্থে ছিল না৷ তবে কৃষ্ণনগরের যে বারোদোলের মেলা, তার সঙ্গে নববর্ষের ক্ষীণ একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব৷ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত এ উৎসবে কৃষ্ণনগরের গোপ সম্প্রদায় (কৃষ্ণনগর ছিল গোয়ালা অধু্যষিত অঞ্চল৷ নাম ছিল আদিতে গোয়ারি৷) ‘কপিলাগীতি’ গেয়ে পথ পরিক্রমা করতেন৷ এর রেশ আজও কিছুটা রয়ে গিয়েছে সেখানে৷
পয়লা বৈশাখকে নববর্ষের রূপ দেওয়া এবং উৎসবে মেতে ওঠা সম্ভবত ঔপনিবেশিক রাজধানী শহর কলকাতায় ইংরেজদের ১ জানুয়ারি নববর্ষ পালনের অনুকরণে৷ পুণ্যাহ, হালখাতা হল নববর্ষের প্রাথমিক প্রয়োগ-অনুষঙ্গ এবং পরবর্তীকালে তা সর্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় আমোদ-প্রমোদে পরিণত হয়৷ বিশ শতক থেকেই মোটামুটিভাবে এর জয়যাত্রা৷ এবং বাঙালির নববর্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যকার নান্দনিকতায় রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা৷
নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ
জমিদার রবীন্দ্রনাথেরও নববর্ষ শুরু ‘পুণ্যাহ’ দিয়েই৷ ১৮৯১-তে পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে এই পুণ্যাহের দিনে তিনি যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনলেন প্রথাটির মধ্যে, তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী৷ ঠাকুরবাড়ির চিরাচরিত নিয়ম ছিল, পুণ্যাহের দিন প্রজারা হিন্দু-মুসলমান দুইভাগে বিভক্ত হয়ে আসন গ্রহণ করবেন৷ হিন্দু প্রজাদের জন্য চাদর, তার ওপর সতরঞ্চি৷ তফাতে মুসলমান প্রজা, চাদর ছাড়া কেবল সতরঞ্চির ওপর৷ আর জমিদার বসবেন ভেলভেট মোড়া সিংহাসনে৷ জমিদার রবীন্দ্রনাথের আদেশে পুণ্যাহের দিনটিতে এই ত্রিবিধ ব্যবস্থা উঠে গেল৷ একাসনে বসলেন হিন্দু, মুসলমান এবং জমিদার রবীন্দ্রনাথ৷ আর রবীন্দ্রনাথ সেদিনই সংকল্প নিলেন সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানোর৷ পূর্ববঙ্গ তথা তাবৎ বাঙালি মুসলমান সমাজ ওইদিন একটুখানি হলেও আত্মমর্যাদা ফিরে পেলেন রবীন্দ্রনাথের ওই যুগান্তকারী রাজা-প্রজা সম্পর্কের মানবিকতার অঙ্কুর প্রতিষ্ঠায়৷ আজ যখন পূর্ববঙ্গ তথা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের দিকে তাকাই, দেখি, সেখানে বাংলা নববর্ষ পালনের স্বতঃস্ফূর্ততা, যার উদ্যোক্তা ও হোতা সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাঙালি, দেখে ১৮৯১-এর পয়লা বৈশাখকে কুর্নিশ জানাতে ইচ্ছে করে৷
পুণ্যাহ থেকে যাত্রা শুরু হল, পরবর্তীকালে যে দিনটিকে জমিদার-প্রজার নিতান্ত বৈষয়িক সম্পর্কের তুচ্ছতা থেকে বাঙালির যথার্থ বর্ষবরণের দিনে পরিণত হওয়াও তো রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে৷
বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০১-এ৷ ১৯০২-তে (বাংলা ১৩০৯) পয়লা বৈশাখ আশ্রম বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ আয়োজন করেছিলেন প্রথম নববর্ষ উৎসব৷ ইংরেজি ১৯০২-এর ১৪ এপ্রিল সোমবার অনুষ্ঠিত বর্ষবরণের দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে যোগ দিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতচন্দ্র সেন প্রমুখ৷ কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গান ‘আমারে করো তোমার বীণা’ পরিবেশিত হয়৷ প্রাতঃকালীন উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ নববর্ষ নিয়ে ভাষণ দেন৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না— কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃতু্য লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়৷ বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে— তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃতু্য সেই আনন্দেরই রহস্য৷’
সেই থেকে বৈশাখের প্রথম দিনটি শান্তিনিকেতনে বর্ষবরণের দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে৷ এমনও হয়েছে, নববর্ষের দিনটিতে কবি শান্তিনিকেতনে নেই৷ তবু মন পড়ে রয়েছে সেখানে৷ ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে৷ এক পত্রে লিখছেন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে, ‘প্রত্যেকবার আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি— কিন্ত্ত এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ৷’
তারপর তো নববর্ষের দিনটিকেই কবি নির্বাচন করলেন নিজের জন্মদিন পালনের দিনরূপে৷ ১৯৩৬ থেকে৷ কবির জীবৎকালে শেষ জন্মদিন পালিত হয়েছিল, এবং এখনও শান্তিনিকেতনে সেদিনই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হচ্ছে৷ শেষ জন্মদিন কবির জীবিতাবস্থায় পালিত হওয়া উপলক্ষ্যে কবি গান রচনা করেছিলেন, ‘হে নূতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ৷’ বৈতালিকদলের আশ্রম পরিক্রমা, কবিকে ফুল উপহার দিয়ে প্রণাম, ভোরে ক্ষিতিমোহন সেনের উপাসনা, বেদপাঠ, এবং একদিকে নববর্ষ ও অন্যদিকে জন্মদিন পালনকে উপলক্ষ্য করে কবি সেদিন বলেছিলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে, ‘আমার মতন সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হয়েছে৷ শুধু যে আমার স্বদেশীয়েরাই আমাকে ভালোবেসেছেন তা নয়, সুদূর দেশেরও অনেক মনস্বী তপস্বী রসিক আমার অজস্র আত্মীয়তা দ্বারা ধন্য করেছেন৷ জানি না আমার চরিত্রে কর্মে কি লক্ষ্য করেছেন৷ সকলের এই স্নেহমমতাসেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি, প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি আমাকে এই আশ্চর্য্য গৌরবের অধিকারী করেছেন৷’
কেবল নববর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতাই নয়, তাঁর গানে কবিতায় গল্পে নাটকে প্রবন্ধে চিঠিপত্রে বিচিত্রভাবে নববর্ষ নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে৷ এ নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগ্রন্থ রচনা করা সম্ভব৷ আমরা আপাতত দু-একটি নববর্ষ বিষয়ক রবীন্দ্র-রচনার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গটি শেষ করব৷ কখনও নববর্ষকে তিনি অন্বিত করেন স্বাদেশিকতার আগ্নেয় আহ্বানে, ‘নববৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা,/ তব আশ্রমে তোমার চরণে হে ভারত, লব শিক্ষা৷’ (উৎসর্গ, ১৩ সংখ্যক কবিতা)৷ ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ‘গৃহলক্ষ্মী’ কবিতায় নববর্ষকে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন এভাবে, ‘নবজাগরণ লগনে লগনে বাজে কল্যাণশঙ্খ/ এসো তুমি ঊষা ওগো অকলুষা, আনো দিন নিঃশঙ্ক৷’ কখনও ‘নববর্ষ এল আজি দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে’ (স্ফুলিঙ্গ), আবার কখনও তিনি লেখেন, ‘ঐ মহামানব আসে৷’
‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থের ‘নববর্ষ’ প্রবন্ধে তিনি চিন্তায় ফেলে দেন আমাদের, যখন তাঁর লেখায় পড়ি, ‘মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়— পাখির গান তার নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়৷ তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে৷ আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভু্যদয় ঘটে৷’ বড়ই ভাববার মত কথা৷
নববর্ষ যেমন তাঁর চিন্তায়-চেতনায়, তেমনই বর্ষশেষটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তাঁর কাছে৷
১৩১৭-র (১৯১২) বর্ষশেষের দিনটিতে শান্তিনিকেতন মন্দিরে ভাষণ দিতে গিয়ে বলছেন তিনি, ‘জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলই একটি পাওয়াতে এসে ঠেকছে— সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব৷’ লিখছেন, ‘আজ আমার মন তাঁকে বলছে, বারে বারে খেলা শেষ হয়, কিন্ত্ত হে আমার জীবনখেলার সাথি, তোমার তো শেষ হয় না৷’
এই শেষ না-হওয়া অশেষকেই বছর বছর এনে দেয় নববর্ষের প্রভাত৷
বাঙালির নববর্ষের অধুনা: নানা দিক
হালখাতা এখন জাঁকিয়ে বসেছে৷ এখানে দেখি হিন্দু-মুসলমান স্বতন্ত্র৷ হিন্দুর গণেশপুজো, কালীঘাট গিয়ে মহাজনী খাতা মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে আনা৷ মুসলমানের আছে কোরান পাঠ৷ একদা জলসত্রের প্রচলন ঘটাতেন প্রখর গ্রীষ্মে পথিকের পিপাসা ও ক্লান্তি দূর করতে৷ জল, তার সঙ্গে পরিবেশিত হত ভিজে ছোলা, গুড় বা বাতাসা৷ মফস্বলে এমন জলসত্র দেখার অভিজ্ঞতা এ লেখকের হয়েছে৷ কলকাতাতেও৷ পঞ্জিকা-ক্রয় অনেক বাড়িতেই অবশ্যকৃত্য৷ একসময় যখন সাক্ষরতা তেমন ছিল না, পুরোহিতরা এসে মা-মাসিদের সামনে বসে পঞ্জিকা পড়ে শোনাতেন৷ উনিশ শতকের শেষদিকের এক ছড়ায় এই নববর্ষের দিনটিতে নতুন পোশাক পরিধানের বর্ণনা পাই— ‘নববর্ষে নববস্ত্র পরিধান যত৷/ বেটাবেটি হাসে খেলে আপনার মত৷৷’ আর হ্যাঁ, রান্নার বাহুল্যও রয়েছে এই দিনে, এমনকি ‘যে শাউড়ি বউ দুষে নিত্য মিথ্যা কাঁদে৷/ সেও এসে সকালেতে নব অন্ন রাঁধে৷৷’ এমন ছবিও সেদিনকার লেখায় পাই, যাতে জানা যায়, নেশা ও বেশ্যাসক্ত স্বামীও কাজের শেষে এদিন ঘরে ফিরছে পঞ্জিকা, মিষ্টির হাঁড়ি আর স্ত্রীর জন্য সুগন্ধী তেলের শিশি নিয়ে৷ বালক-বালিকারা নতুন পোশাক পরে গুরুজনদের প্রণাম করত, বদলে পেত থৌল খরচের পয়সা, মেলায় গিয়ে খাবার জিনিস, পুতুল ইতাদি কিনবার৷ থৌল বা থোল কথাটির অর্থ খুচরো বা সামান্য৷ ছোটদের কাছে সামান্যই অসামান্য৷
বাংলাদেশের কোনও অঞ্চলে বৈশাখ মাসে (হয়তো পয়লা বৈশাখও) হিন্দুরা ‘ক্ষেত্র ঠাকুর’ এবং মুসলমানেরা ‘কাউয়া পির’-এর আরাধনা করেন৷ এদুটিই কৃষকদের যাপ্য উৎসব৷ লোকবিশ্বাস, ক্ষেত্র ঠাকুর খেত পাহারা দেন, আর কাউয়া পিরও ফসল নষ্টকারী জীবজন্ত্ত, পোকামাকড়ের থেকে খেত রক্ষা করেন৷
নববর্ষে বাঙালিসমাজে সঙ্গীতের বিশেষ স্থান রয়েছে৷ বাবুসংস্কৃতিতে এর বিকৃত রূপ দেখি, কিন্ত্ত পাশাপাশি স্বদেশি যুগ পরিবাহিত হয়ে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চা শুরু হতে দেখি বিশ শতকের সূচনা থেকেই৷ গ্রামোফোনের আবির্ভাব গতিজাড্য দেয় একে, এবং এরই পাশাপাশি বেতারেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এক্ষেত্রে৷ কাজী নজরুল ইসলাম যেমন নববর্ষ নিয়ে বছরের পর বছর নতুন গান লিখে নিজে পরিবেশন করতেন, অন্য শিল্পীদের দিয়ে গাওয়াতেন৷ বসুশ্রী সিনেমা হলে পয়লা বৈশাখ তখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীসমন্বয়ে গানের আসর বসত৷ বাংলার সেরা গাইয়ে আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মিলিত হতেন সেদিন সেই প্রভাতী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে৷ দূরদর্শনও নববর্ষকে জনপ্রিয় করেছে৷
আর ছিল বইপ্রকাশ, প্রকাশকে-লেখকে সান্ধ্যবাসর, মিষ্টিমুখ, বইমেলা শুরু হওয়ার আগে পয়লা বৈশাখই গ্রন্থপ্রকাশের সবচেয়ে বড় লগ্ন ছিল৷ প্রকাশকরা লেখকদের প্রাপ্য রয়ালটি দিতেন, নতুন বইয়ের জন্য চুক্তি করতেন৷ কিছু কিছু প্রকাশকের কঞ্জুষপনার গল্পও শোনা যায়৷ এরকমই একটি মজার কাহিনি পড়েছি অধ্যাপক-গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের আত্মজীবনী ‘আমার সকাল আমার সন্ধ্যা’ বইয়ে৷
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির মালিক প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কিছুতেই লেখকদের প্রাপ্য অর্থ দিতে চাইতেন না৷ লেখকরা টাকা চাইলেই তিনি তাঁর তমলুকী বাংলায় তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলতেন, ‘দুবো দুবো৷’ প্রমথনাথ বিশীকেও তিনি বারবার এই বরাভয় দিয়ে গেছেন, টাকাপয়সা ছোঁয়ানোর নাম করেননি৷ স্বভাবরসিক প্রমথনাথ এই ঘটনায় মজা করে একটি চরিত্রই নির্মাণ করে ফেললেন ‘কেরী সাহেবের মুন্সী’ উপন্যাসে, মসিয়ে দুবো!
অন্তিমে বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ পালনের কথা বলতেই হবে৷ ‘ছায়ানট’ এর উদ্যোক্তা, সেই পাকিস্তান আমলে, রমনার বটমূলে৷ আজ তা বিচিত্র, বহুশাখায়িত৷ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পী ইমদাদ হোসেনের প্রণোদনায় ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’, যা আজ ইউনেস্কোর দ্বারা সংবর্ধিত, হেরিটেজ হিসেবে৷ বাংলাদেশই যথার্থ বাংলা নববর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ আর নান্দনিক উৎসব উপহার দিচ্ছে৷ পৃথিবীর সবখানে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিরা যাপন করেন এ উৎসব৷ আমরা কবে অনুরূপ
যাপন করা শিখব?
Advertisement