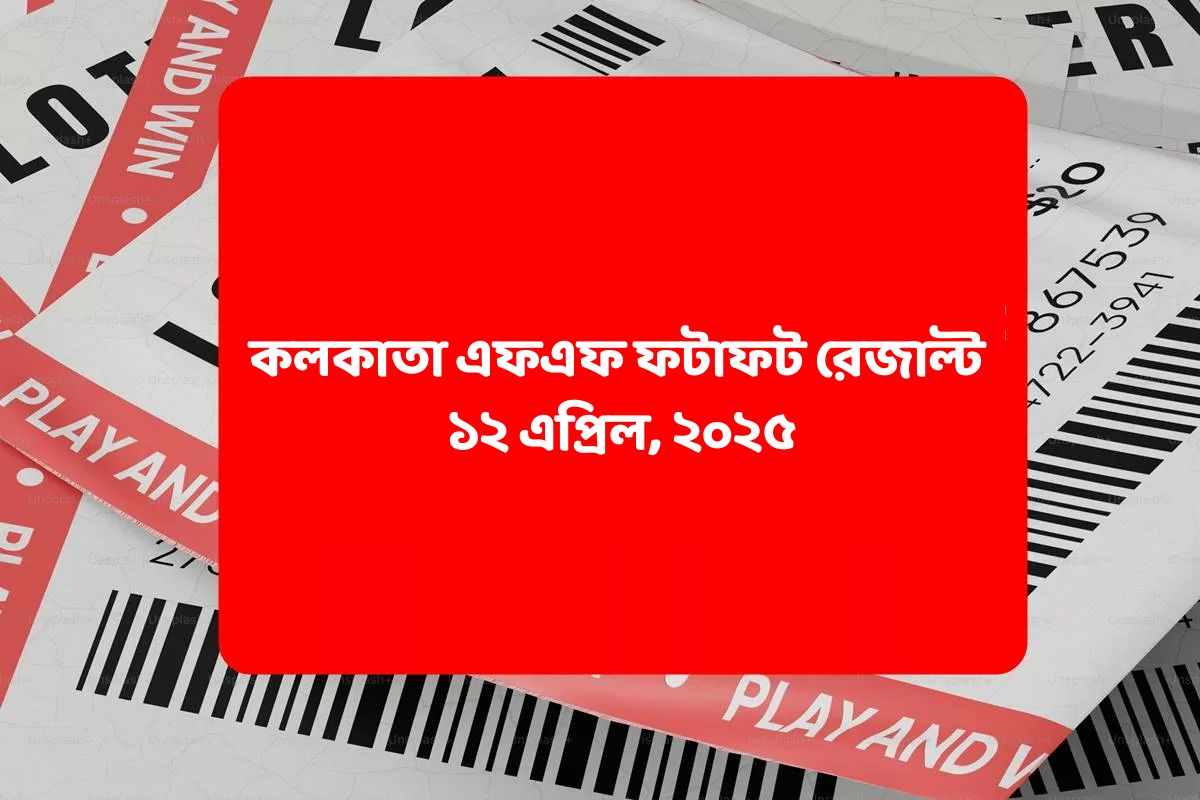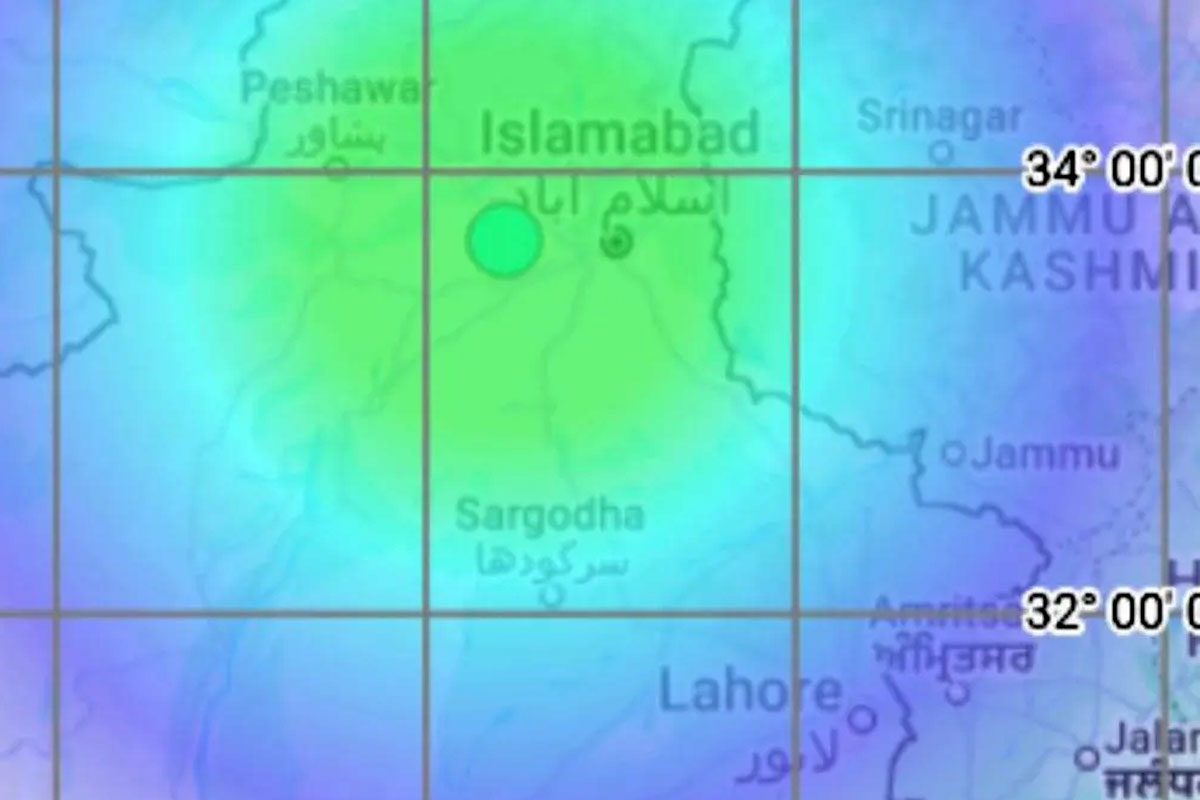সৌম্যপ্রতীক মুখোপাধ্যায়
সজল
সজল ঘোড়ুই আমার কলেজবেলার বন্ধু। বিএসসি-তে একসঙ্গে পড়তাম। সজল গ্রামের ছেলে। বাপ ঠাকুরদা চাষবাস করেই কাটিয়েছেন। কোনোভাবে সংসার চলে যায়। সজল ওদের বাড়ির প্রথম যে এতদূর পড়াশোনা করে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। সজল নিজের কিছুটা খরচ টিউশন করে মেটাত। থাকত রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের একটা আলো বাতাস না ঢোকা মেসে। কলেজ ফেরত অনেক সময়ই কাটিয়েছি সেই মেসে। কখনও পড়াশোনার জন্য, কখনও আড্ডার মেজাজে চপ তেলেভাজা সহ।
সজলের রেজাল্ট ভাল হল না। কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে একদম খারাপ করল। কপালের দোষই বলা যেতে পারে। আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলাম, সজল গেল ছিটকে। তবে একদম হতাশ হয়নি সে। আমরা জানতাম যে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল কী বিষম বস্তু। ভাগ্য সেখানে অনেক বড় ভুমিকা নেয়। সজলের ভাগ্য সহায়ক ছিল না। ভাল ছাত্র ছিল সে। আমরা সবাই যেন ঠিক জানতাম এই অবস্থা থেকে সে বেরিয়ে আসবে। সজল এবার উৎসাহের সঙ্গে চাকরির পরীক্ষাগুলো দিতে শুরু করল।
তবে যোগাযোগ রয়ে গিয়েছিল। সজল মেসেই থাকত। কলেজ ফেরতা আমিও যেতাম। আরও কিছু কমন বন্ধুবান্ধব আড্ডা, টুকরো টাকরা কথা, মাঝে সাঝে সিনেমা দেখা এইসব। এইরকম এক চৈত্র মাসের বিকালে সজলের মেসে গিয়ে শুনলাম সে দেশের বাড়িতে গিয়েছে, আর তার এক ইন্টারভিউ লেটার এসে পড়ে আছে। মেসের ঠাকুর ভজুদা দিলে। খুলে দেখলাম তিনদিন বাদেই ইন্টারভিউ। পোস্ট অফিসের চাকরির। সুতরাং যে করেই হোক সজলের কাছে পৌঁছনো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কী যে করি।
সে যুগে মোবাইল তো দূরে থাক, টেলিফোনও ছিল না সহজেই হাতের কাছে। সজলের বাড়ির ঠিকানা, আর তার মুখে শোনা কিছু গ্রামের গল্প শোনা ছাড়া আর কিছু হাতিয়ার নেই। আর হাতে মাত্র দুটো দিন। পরের দিন সকালেই আবার প্র্যাকটিক্যাল। কলেজে যেতেই হবে। ঠিক করলাম ফার্স্ট হাফে কলেজ করে, দুপুরে বাস ধরে বিকালের মধ্যেই সজলের বাড়িতে পৌঁছে যাব। দুই একজন বন্ধুকে বলেছিলাম সঙ্গী হতে। ‘চল, একসঙ্গে যাই’। কিন্তু সঙ্গ পেলাম না কারোরই।
সব প্রথম দিকে ঠিকঠাক হলেও বিকালের ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী হিসেব উল্টোপাল্টা করে দিল শেষমেশ। বাস থেকে যখন নামলাম সজলের গ্রামের স্টপেজে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামতে চলেছে।
বাস থেকে নেমে একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি এখন নেই, কিন্তু একটা সোঁদা হাওয়ার ঝটকা মাঝে মাঝেই গায়ে লাগছে। যেদিকে বাস নামিয়ে দিল, সেদিকে কিছু চোখে পড়ল না। উল্টো দিকে একটা হ্যারিকেনের আলো কোনও একটা দোকানের ভিতর থেকে আসছে বলে মনে হল। যা হয়, ঝড়ের সময় ইলেকট্রিক কানেকশন নিশ্চিত কেটে দিয়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেই দু-একটা ভ্যান শব্দ করে চলে গেল।
গাঁয়ের অতিথি
সঙ্গে কোন টর্চ জাতীয় কিছু নেই, সেটাই চিন্তার। ভাবছি রাস্তার ওপারে দোকানে গিয়ে সজলের বাড়ির রাস্তার দিশা জানব। আর যদি টর্চ জাতের কিছু পাওয়া যায় তারও চেষ্টা করব। হঠাৎই পিছন থেকে কর্কশ গলার আওয়াজ এল, ‘যাবে কোথায়?’ সজল নানান কথার মধ্যে বলেছিল অনেকদিন আগে যে, তাদের বাড়িটি বাস রাস্তা থেকে বেশ দূরে। আর বিজলিবাতির খুঁটি বাড়ির কাছে এলেও, বিদ্যুতের আলো এখনও আসেনি।
সজলের নাম বললাম। বললাম, ‘কার্তিক ঘোড়ুই মশায়ের বাড়িতে যাব।’
কর্কশ গলাটি আরও একবার বেজে উঠল, ‘ও বাপির কলকাতার বন্ধু বুঝি!’ বুঝলাম সজলের ডাক নাম বাপি। সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লাম।
‘তা উদের বাড়ি তো অনেক ভিতরে। বেশ দূরে— টর্চ নেই তো? রাতবিরেতে যাবা কী করে।’ কর্কশ গলা আবার জানান দিল।
বললাম, ‘না তাড়াহুড়োতে টর্চ আনতে ভুলে গিয়েছি। আর আসব ভেবেছিলাম বিকালের দিকেই। তাই জরুরি মনে করিওনি।’
খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসির আওয়াজ এল। ভদ্রলোকের হাতে একটি হ্যারিকেন দেখলাম এখন। উল্টো দিক থেকে কলকাতার দিকে একটি বাস এল। গতি তার মন্থর হল। কিন্তু থামল না। কেউ ওঠার বা নামার নেই বলেই বোধহয়। বাসের হেডলাইটের আলোয় লোকটিকে দেখলাম অস্পষ্ট। মাঝারি গড়ন। কুচকুচে কালো চুল। মনে হল বছর পঞ্চাশের কাছে বয়স। পরনে লুঙ্গির মতন করে বোধহয় ধুতি পরা। গায়ে হাফ হাতা স্যান্ডো গেঞ্জি। যেটি নজরকাড়া সেটি তীক্ষ্ণ চোখ। আর টিকালো নাক।
ভদ্রলোক বললেন, ‘চলো তোমাকে কার্তিকের বাড়িতে এগিয়ে দিয়ে আসি, আমার বাড়ি ওই দিকেই, না হয় কিছুটা এগিয়ে কার্তিকের বাড়ির দোরগোড়ায় তোমাকে ছেড়ে আসব! হাজার হোক তুমি আমাদের গাঁয়ের অতিথি বলে কথা।’
ওই আধাঁরের মধ্যে— বিনা টর্চের মালিক হয়ে— সেই মুহূর্তে ভাবলাম এর থেকে ভাল প্রস্তাব আর কী হতে পারে। খচখচ করছিল, কর্কশ কন্ঠস্বর আর তীক্ষ্ণ চাহনি মোটেই স্বস্তির ছিল না। কিন্তু আমল দিলাম না, দেওয়ার উপায়ও ছিল না। চলতে শুরু করলাম তার পিছনে পিছনে।
বড় রাস্তা থেকে নেমে এসে, ছোট ইটের টুকরো ফেলা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। জায়গা জায়গায় জল জমেছে অল্প অল্প। মাঝে মাঝেই সেই জলে পা পড়ছিল। দু-একবার ইটের টুকরায় হোঁচট খেলাম।
কিছুটা মন্ত্র মুগ্ধের মতন অনুসরণ করছিলাম যতীন হালদার মশাইকে। হাঁ, নামটি জানা হয়েছিল এর মধ্যেই। তিনি নাকি যজমানি করে নিজের পেট চালান। পাশের জমিদার বাড়ির কুলপুরোহিতও তিনি।
আকাশ ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মেঘ কেটে গিয়েছে। ঘন অন্ধকারের ভেদ করে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে তারার সারি দেখা যাচ্ছিল। সময়টা অমাবস্যার আশে পাশে হবে বলে মনে হল। দুরের কিছু আলো দেখা যাচ্ছিল, মনে হয় আশেপাশের বাড়ির।
ঠিক বুঝতে না বুঝতেই যতীন হালদারের বাড়ির সামনে হাজির হলাম। মাটির বসতবাড়ি, বসতবাড়ির ভেতরটা অন্ধকার, সামনের উঠোনের পাশে এক দোচালা। সেখান থেকেই কিছুটা জোরালো আলো আসছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রায় তিন হাতের এক কালীঠাকুর। সামনে পূজার ফলমূল। জ্বলন্ত প্রদীপ। হঠাৎই ভয় যেন চেপে বসল আমার ভিতরে।
যতীন হালদার এতক্ষণ সামনে হাঁটাছিলেন। বাড়ির উঠোনে তাঁকে পরিষ্কার সামনে সামনে দেখতে পেলাম। তাঁর ঘন চুল, বলিষ্ঠ চেহারা, কাটা কাটা ধারালো চোখ-নাক, কিছুটা নয়, পুরো বিহ্বল করে দিল। বাড়ির ভিতর অন্য কেউ আছে কিনা বোঝা গেল না। ভাবলাম জোরে চিৎকার করে কাউকে ডাকি। কিন্তু বুঝলাম গলা শুকিয়ে এসেছে। ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া কিছুই বেরোনোর উপায় নেই। মিষ্টি হেসে, অথচ কঠিন আদেশের সুরে তিনি বললেন, ‘মায়ের প্রসাদ গ্রহণ কর! তারপর তোমাকে তোমার জায়গাতেই পৌঁছে দেব।’ বলে প্রসাদের থালায় দুটি ফল, একটি মিষ্টি আর এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলেন। কথাগুলি হেঁয়ালির মতন মনে হল।
কর্তামশাই
জলপানের পর যেন আরও ঘোরের মধ্য তলিয়ে যেতে লাগলাম। দেবী প্রতিমার পাশে মনে হল যেন একটা ধোঁয়াশায় ভরা হাঁড়িকাঠ। যতীন হালদারের মুখ চোখ যেন আরও ভয়াবহ হতে লাগল। হঠাৎই সেই চারপাশের অন্ধকার ফুঁড়ে এক প্রৌঢ়ের আবির্ভাব ঘটল। ধবধবে সাদা ধুতি-পঞ্জাবি, পায়ে মিশকালো চকচকে নিউকাট জুতো। হাতে সরু বেতের লাঠি। তিনি যেন প্রায় উড়ে এসে পড়লেন উঠোনের মাঝ বরাবর। প্রথম দর্শনে মনে হবে যেন ছবি বিশ্বাস সিনেমার পর্দা থেকে নেমে এসেছেন। পিছনে আবার নীলচে পাগড়ি পরা দুই পাইক না পাহারাদার। লাঠি হাতে।
এদেরকে দেখেই হালদার মশাই যেন মিইয়ে গেলেন। তিনি কিছু বলার আগেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি সোজা আমার দিকে তাকালেন। শীতল সে চাহনি, কিন্তু মনে হল ভরসার। অনেক দূর থেকে যেন গম্ভীর স্বর ভেসে এল, ‘ওহে ছোকরা, চল তোমাকে কার্তিকের ঘরে পৌঁছে দি, অনেক রাত হল।’ হতভম্ব আমি, কী করে তিনি জানলেন আমি কোথায় যাবো, সেই সব মাথায় আসেওনি। হালদার মশায়ের কর্কশ গলা পাল্টে হঠাৎই অমায়িক হয়ে উঠল। ‘কর্তামশাই, আপনার কষ্ট করার কী দরকার। আমিই তো পৌঁছে দিচ্ছিলাম।’
‘ছবি বিশ্বাস’ প্রথমে এক কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। বাম হাতটা তুলে বললেন, ‘থাক। তোমাকে আর কেরামতি দেখাতে হবে না।’
তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘চল হে।’
ইতস্তত ভাব দেখে, তিনি এগিয়ে এসে শক্ত করে কবজির উপরে হাত চেপে ধরলেন। বললেন, ‘চলো’। বরফের থেকে যেন বেশি ঠান্ডা সেই হাত। হালদার মশায়ের কাছে তাও একটা হ্যারিকেন ছিল। এই তিনজনের কাছে কোনো আলোও নেই। তবুও মসৃণভাবে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে চললেন অন্ধকারের বুক চিরে। তাদের সাদা পোশাক ছাড়া আর কিছুই যেন দেখা যাচ্ছিল না। হাঁটছি না, আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে বোঝার মতন অবস্থায় নেই। কাঁধের সাইডব্যাগ কোনো রকমে ঝুলছে।
আস্তে আস্তে মনে হল, দূরের একটা আলো ক্রমশ কাছে আসছে। প্রথমে আলো, তারপর আবছা ঘরদোর, লোকজনের কথা বলার আওয়াজ। ধড়ে যেন কিছুটা প্রাণ ফিরে পেলাম। চিৎকার করে উঠলাম, ‘কে কোথায় আছো। আমাকে বাঁচাও।’ মাটিতে পড়ে যাবার আগে অনুভব করলাম— শীতল হাতটি আমার কবজির উপর থেকে সরে যাচ্ছিল।
শেষমেশ
স্বাভাবিক হতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। আমার চিৎকার শুনে সজলের বাড়ির লোকজন দৌড়ে বাইরে এসে অচৈতন্য অবস্থায় আমাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। আমি নাকি বিড়বিড় করে সজলের নাম বলছিলাম। আশেপাশে তাঁরা কাউকে দেখতে পাননি।
পরের দিন সকালে প্রায় গাঁয়ের সব লোক আমার ‘গল্প’ শুনতে এসেছিল। মোটামুটি যা উদ্ধার করতে পারলাম, যতীন হালদার নামে এক তন্ত্রসাধক এই তল্লাটে অনেক দিন আগে ছিল, এবং তিনি নাকি নরবলিও দিয়েছিলেন। আরও অনেক কাহিনীর মূল চরিত্র তিনি। প্রৌঢ়ের পরিচয় জিজ্ঞেস করার অবস্থা আমার ছিল না। শুনলাম তিনি নাকি এই এলাকার পুরানো জমিদার নীলমাধব রায়। প্রজাবৎসল, পরোপকারী, এই মানুষটি এখানে স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সেই ইংরেজ আমলেই করে দিয়েছিলেন। দু-মাইল দূরে তাঁর জমিদার বাড়ি; বাড়িটির অবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না বলে অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। ছুটিছাটায় তাঁর বংশধররা এখন মাঝে মাঝেই আসেন কলকাতা থেকে।
দুপুরে সজলের সঙ্গে কলকাতায় ফিরলাম। সেই সরু পথ দিয়েই। মিনিট দশেক লাগল। মাঝে একটা জায়গার দিকে হাত তুলে সজল বলল, ‘ওই দেখ নদীর চর, আর পাশে শ্মশান।’ শ্মশানের পাশে একটা ভাঙা আটচালা। যেন মনে হল, যতীন হালদার আটচালার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখছে।
সজল একমাস পরে পোস্ট অফিসের চাকরিটা পায়। আমার ভাগ্যে জুটেছিল— রয়ালের মাটন চাপ আর রুমালি রুটির ভোজ। তারপর আরও একবার ওর বাড়িতে গিয়েছিলেম। সজলের বিয়ের সময়। তবে আর ভুল করিনি। সকালেই পৌঁছেছিলাম। শ্মশান, নীলমাধবের জমিদার বাড়ি, সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। আরও দেখেছিলাম, আমি ওই গ্রামে বেশ বিখ্যাত একটি নাম।