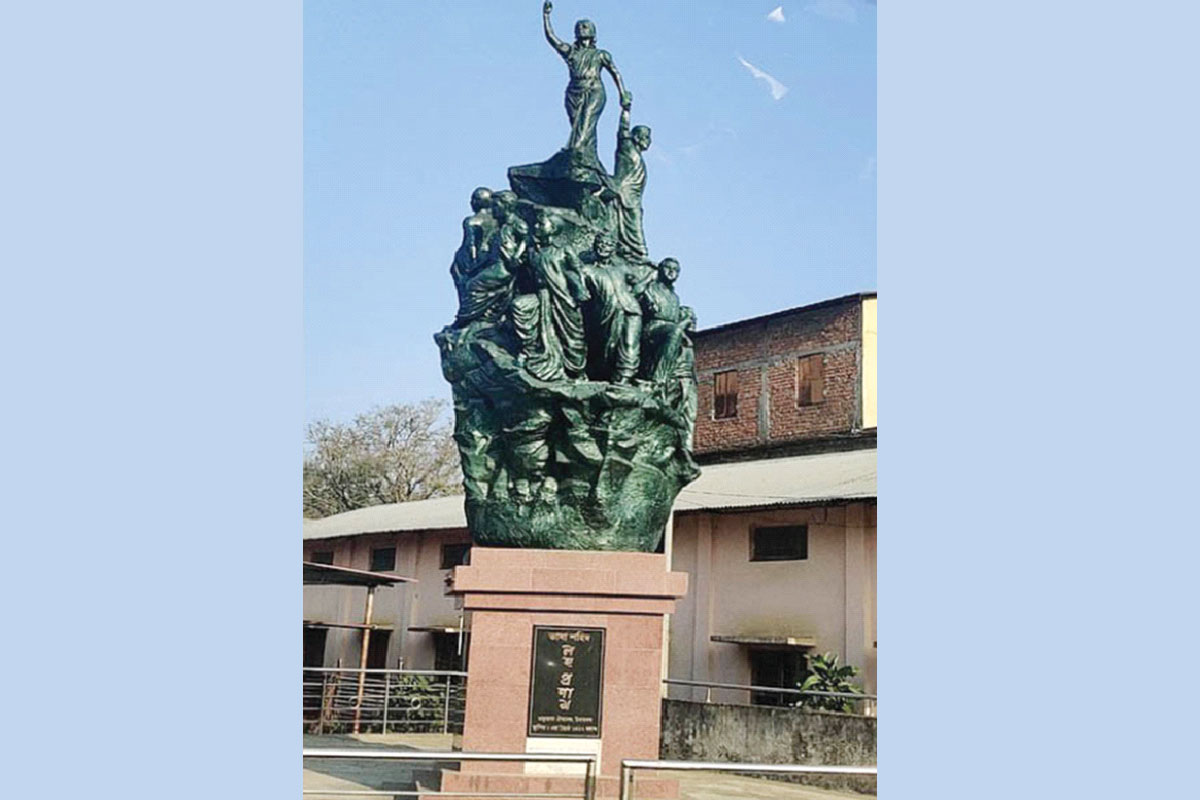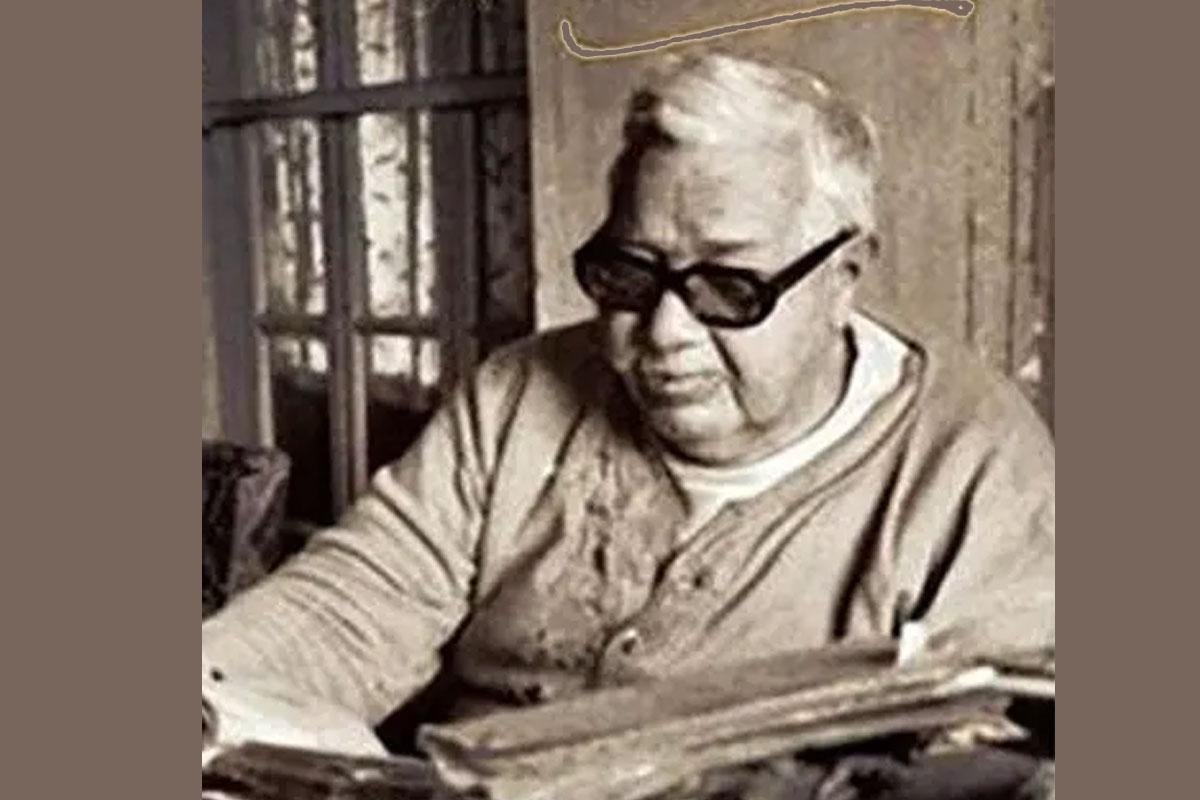বরুণ দাস
‘ধ্রুপদী স্বীকৃতি’তে কী আসে যায় যদি না খোদ বাঙালিই তাঁর নিজের মাতৃভাষাকে ন্যূনতম গুরুত্ব না দেয় কিংবা শ্রদ্ধা-সম্মানের চোখে না দেখে!
এটা যেমন একদিকে গভীর চিন্তার বিষয়, অন্যদিকে আবার এক রুঢ় বাস্তবতাকেও সামনে নিয়ে এসেছে যা অস্বীকার করার কোনও জায়গাও হয়তো নেই। একুশ কিংবা ঊনিশের আলোয় এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে আমরা বরং ওই দুই দিক নিয়েই আলোচনায় করার চেষ্টা করব যাতে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। কেন শিক্ষিত ও বিত্তবান বাঙালি তাঁদের মাতৃভাষা নিয়ে উদাসীন এবং কেন কিছু বাঙালি তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে জানিয়েছেন তাঁদের চূড়ান্ত হতাশার দিকটি। মাত্র কতিপয় মানুষ এই খবরে আনন্দিত।
এছাড়াও বেশ কয়েকজন পাঠক মাতৃভাষা বাংলার ‘ধ্রুপদী স্বীকৃতি’তে তাঁদের ভাবনার যৌক্তিক দিকটি জানিয়েছেন। এই যে হতাশা, এই যে উদাসীনতা, এই যে গুটি কয়েক মানুষের আনন্দ-তাঁর কারণও কী ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? বলা বাহুল্য, যারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের অনিবার্য আশঙ্কার কথা কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না। যদি বাস্তবের মাটিতে আমাদের পা রাখা থাকে। আবেগ কিংবা কল্পনায় হয়তো অনেক কিছুই বলা যায়; কিন্তু আজকের কঠিন বাস্তবের সঙ্গে তাঁর মিল কতটুকু?
এ নিয়ে আমাদের অবশ্যই গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেকটা জলই গড়িয়ে গিয়েছে। এখনও যদি সদর্থক পদক্ষেপ না নেওয়া যায় তো বাংলা ভাষার ‘ধ্রুপদী স্বীকৃতি’টাই হয়তো নিস্ফল হয়ে যাবে। ভাবের ঘরে চুরি তো অনেক হল। এবার বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিষয়টির চুলচেরা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শুধু বছরের বিশেষ দিনে গুটিকয়েক সভা-সমাবেশ কিংবা হলঘরে গান-কবিতা আর বক্তব্যের মধ্যে অনুষ্ঠানকে আটকে রাখলে চলবে না একথা নিশ্চিত।
একথা ঠিক যে, আজকের কোরিয়ার সর্বস্ব পড়াশোনায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত ও ‘সচেতন’ অভিভাবকবৃন্দ বাংলাভাষা নিয়ে অনেকটাই উদাসীন এবং নির্লিপ্তও বটে। আসলে ‘পড়াশোনা মানেই মোটা বেতনের চাকরি’ এমন গড়-পরতা একটা ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যেই জাঁকিয়ে বসেছে। যেখানে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারটা শুধু গৌণ নয়, একেবারেই উধাও। মুখ্য হল রোজগারের ব্যাপারটি। এই ধারণার মধ্যে অবশ্য দোষের কিছু নেই। কারণ আজকের বাবা-মা তাঁদের রোজগারের সর্বস্ব ব্যয় করে সন্তানের পড়াশোনা করান।
বিনিময়ে তাঁরা তার রিটার্ন আশা করবেন না- এ কী কখনও হয়? গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী ‘মা ফলেষু কদাচন’ এসব সংসারী মানুষের জন্য তো নয়। তাঁরা (পুঁজি) বিনিয়োগ করে (মুনাফা) ফেরৎ চাইবেন- এটাই সমাজ- সংসারের সিংহভাগ মানুষেরই স্বাভাবিক আশা। তাই তাঁদের সমালোচনা করে লাভ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় ‘ব্যবস্থাপনা’ সেভাবই নির্মাণ করা হয়েছে যাতে ‘এক দেশ, এক ভাষা, এক ভোট, এক চিন্তা, এক সরকার ইত্যাদি ইত্যাদি সরকারি ভাবনা বা ইচ্ছেগুলির বাস্তবায়ন ঘটে।
তা নাহলে এতদিনেও কেন মাতৃভাষার প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে বাঙলা ও বাঙালির সরকার বাঙলার শাসন ক্ষমতায় থেকেও তাঁদের মনে সামান্যতম আগ্রহটুকু জাগল না? যদিও একাধিকবার ‘প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত’ নিয়ে ওই যাকে বলে লোকদেখানো ব্যাপার-স্যাপার তা সেরে ফেলেছেন তাঁরা। সরকার বাহাদুর বরাবরই দোষ চাপিয়েছেন আমলাদের ওপর। ‘যা কিছু হারায় গিন্নি বলে কেষ্টাবেটাই চোর’-এর মতোই ব্যাপার আর কী! বাংলা ভাষায় অনভ্যস্ত আমলারাই নাকি এ ব্যাপারে কেবল গড়িমসি করে থাকেন।
তাঁদের প্রবল অনীহার জন্যেই নাকি বাঙলার বাঙালি সরকার বাংলা ভাষায় রাজ্যের প্রশাসনিক কাজ শুরু করতে পারছেন না। উল্লেখ্য, দেশ স্বাধীন হয়েছে সাড়ে সাত দশকের ওপর। ওই সময়েই দাবি উঠেছিল রাজ্যের ভাষাই হোক রাজ্য প্রশাসনের ভাষা। ইতিহাসের ধূসর পাতা থেকে জানা যায়, বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর মুখ্যসচিব সুকুমার সেন মশায়কে বাংলা ভাষায় নোট দিতেও শুরু করেন। কিন্তু তার পরিণতি কী তা আমরা সবাই জানি। আজও তা বস্তবের মুখ দেখেনি।
আবার পরবর্তীকালেও একই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখি আমরা। ইতিহাসের কী সেই পুনরাবৃত্তি? বাংলা ১৩৮৬-র ২৫শে বৈশাখ তৎকালীন রাজ্য সরকার জানিয়েছিলেন, ‘এ দিন থেকে রাজ্য সরকারের সমস্ত কাজকর্মে বাংলা ভাষা চালু হয়েছে।’ না, প্রশাসনিক কার্যালয় খোদ মহাকরণ থেকে প্রচারিত সরকারি ঘোষণার পরও তা আদৌ চালু হয়নি। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মান্যতা পায়নি খোদ সরকারি তরফ থেকেই! একে কী বলবেন আপনি? কাকেই বা আপনি দোষারোপ করবেন? বিভ্রান্তির চরম এখানেই।
এখানেই কিন্তু শেষ নয়। আরও আছে। এর ঠিক ২২ বছর পর ১৪০৮-এর ১লা বৈশাখ একই ঘোষণা করা হয় সরকারের তরফে। ঘোষণার সন-তারিখ দেখে সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন, খোদ বামফ্রন্ট সরকারের আমলের এই সদর্প ঘোষণা। যাঁরা একটানা চৌত্রিশ বছর মহাকরণের অলিন্দ্যে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। ক্ষমতা লাভের শুরুতে যাঁরা রাইটার্স থেকে নয়, জনতার মধ্যে থেকে সরকার চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতিরই-বা পরিণাম কী হয়েছিল- তাও পাঠক ভালোভাবেই জানেন।
রাজ্যবাসী কমবেশি জানেন, কয়েক বছর আগে ‘পরিবর্তনের সরকার’ও ওই একই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ‘কাজের কাজ’ কিছু হয়েছে কী? সরকারি ঘোষণাই সার। বাঙলা ভাষা আজও রাজ্য প্রশাসনে ঠাঁই পায়নি। আগের মতোই বরাবর ব্রাত্য থেকে গেছে। এই সরকারি এই সরকারি টালবাহানা নিয়ে রাজ্যের মানুষ তিতিবিরক্ত। বিশেষ করে যাঁরা মাতৃভাষার প্রতি আজও শ্রদ্ধা-সম্মান বোধ করেন। এঁরা অনেকেই হয়তো তথাকথিত আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষায় ততোটা পারদর্শী নন; নন সমাজের ওপরতলার তথা বিত্তশালী মানুষ।
যারা কাজের চেয়েও দেখনদারিতে বেশি অভ্যস্থ। সুযোগ পেলেই কথায় ও লেখালেখিতে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেন। যা নিজেরাও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বলতে হয় তাই বলা। কেন ‘বলতে হয়?’ আসলে নিজেদেরকে ‘প্রগতিশীল’ আর এগিয়ে থাকা’ শ্রেণির অংশ হিসেবে তুলে ধরার জন্য বলেন বা লেখেন। বাস্তবের এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ‘যা হওয়ার’ তাই হচ্ছে! কাজ নয়; কথার ফুলঝুরি। “যুক্তিপ্রিয় বাঙালি’ (অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের কথায়/লেখায় অবশ্য তর্কপ্রিয় ভারতবাসী) কাজে নয়- কথাতেই বেশি সন্তুষ্ট।
মাতৃভাষা বাঙলাতে শ্রদ্ধাবান মানুষেরা আকাশ চুম্বী উচ্চাশার মানুষ নন। কল্পনার জগতেও পা রাখেন না। যদিও সমাজ-ভাবনায় এঁরা অন্য অনেকের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। এঁরা আজও শিকড়ের টান অনুভব করেন। নিজেদের সাবেকি ঐতিহ্য-পরম্পরায় বিশ্বাস রাখেন। শিকড়-উপড়ানো মানুষ যে নিজেদেরকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখতে পারেন না- তা এঁরা জানেন। আর জানেন বলেই হাজারো ‘পরিবর্তন’-এর মধ্যেও নিজস্বতাকে আঁকড়ে নিয়ে বাঁচার আগ্রহ দেখান। কারণ সেটুকুই তাঁদের জীবনের একমাত্র পাথেয়।
এঁরা আজও মনুষ্যত্ব ও মানবিকতায় গভীর আস্থা বোধ করেন। আজকের ভোগ-সর্বস্ব পণ্যবাদি (দুঃ) সময়ের মধ্যেও এঁরা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আগুপিছু না ভেবে এগিয়ে আসেন। অনেক সময়ে নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ একদিন মানুষের সামগ্রিক স্বার্থেই তৈরি করা হয়েছিল। তাকে টিকিয়ে রাখতে না পারলে মানুষেরই ক্ষতি। যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সংকীর্ণ ব্যক্তি- স্বার্থের জন্যেই আজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে বসেছে।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতি লাভের পর রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তথা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষার ধ্রুপদী অবয়ব অর্থবহ করে তুলতে রাজ্যের বেসরকারি বিদ্যালয়স্তরে বাংলা ভাষা পঠন-পাঠনের জন্য ‘অনুরোধ’ জানিয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাই। কিন্তু একই সঙ্গে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও করতে হয়, এখানে ‘অনুরোধ’-এর প্রশ্ন আসে কেন? এ রাজ্যে কেন বাংলা ভাষা পঠন-পাঠনকে বাধ্যতামূলক করা হবে না? রাজ্যের ভাষাকে অবজ্ঞা করার অধিকার আসে কিভাবে?
আমাদের অন্যান্য রাজ্যগুলি যা অনায়াসেই পারে আমরা কেন তা পারব না? মহারাষ্ট্র, ওড়িশার মতো এ রাজ্যেও বাংলা ভাষা পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক করা দরকার। আমাদের সঙ্কোচ বা ভয়েরই বা কি আছে? তা নাহলে তো অনিবার্য প্রশ্ন উঠবেই-এদেশের অন্য রাজ্যগুলো যা পারে- আমরা তা পারব না কেন? কোথায় আমাদের পিছুটান? কাদেরকেই-বা আমরা ভয় করছি? আমরা না ‘এগিয়ে থাকা’র বড়াই করি। তাহলে এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকব কেন? বাংলা আজ পথ না দেখাতে পারলেও ‘পথ দেখুক!’
বাস্তববাদিরা নিশ্চয়ই জানেন, বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে ব্যবহার করতে না পারলে বাংলাভাষা তার অতীত ঐতিহ্য শুধু হারাবেই না, তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও হারাবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদেরকে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তা নাহলে আপসোস করা ছাড়া বিকল্প পথ থাকবে না একথা বলাই বাহুল্য। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আজ অনেক শিক্ষিত ও বিত্তবান বাঙালি নিজেদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তারা হয়তো ভাবেন, বাংলা ভাষায় কথা বললে নিজেদের আত্মসম্মান হারাবেন।
অনেকে আবার ইংরেজি-হিন্দি মেশানো বাংলা বলে এক ধরনের আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। মাতৃভাষার পক্ষে যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এ কোন দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা? মাতৃভাষার এই পিছিয়ে পড়ার জন্য অন্যদের দোষ দেওয়ার আগে আমাদের নিজেদের দিকেই ফিরে তাকানো দরকার। আমরাই তো সচেতনভাবে ব্রাত্য করে দিয়েছি নিজেদের মুখের ভাষাকে। ‘হিন্দির দাপটে মাতৃভাষা কোণঠাসা’- এমন অভিযোগ তোলার আগে একবার নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়ানো ভীষণভাবেই বোধহয় দরকার।
তা নাহলে ভাবের ঘরে চুরি’ করা হবে একথা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। আর কে না জানেন, ভাবের ঘরে চুরি’ করতে অবশ্য আমরা- বাঙলিরা বেশ পারদর্শী। আমরা কী সেদিকেই ক্রমশঃ পা বাড়াচ্ছি? আজকের রুঢ় বাস্তব কী বলে? আমাদের দীর্ঘমেয়াদি ভাবগতিক দেখে কিন্তু তেমন মনে হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক। আজ আর বলতে কোনওরকম দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই যে, এভাবে চলতে থাকলে একদিন আপসোস করে নিশ্চিতভাবেই আমাদের অনেককেই বলতে হবে, ‘একদিন আমরা বাঙালি ছিলাম বটে…।’