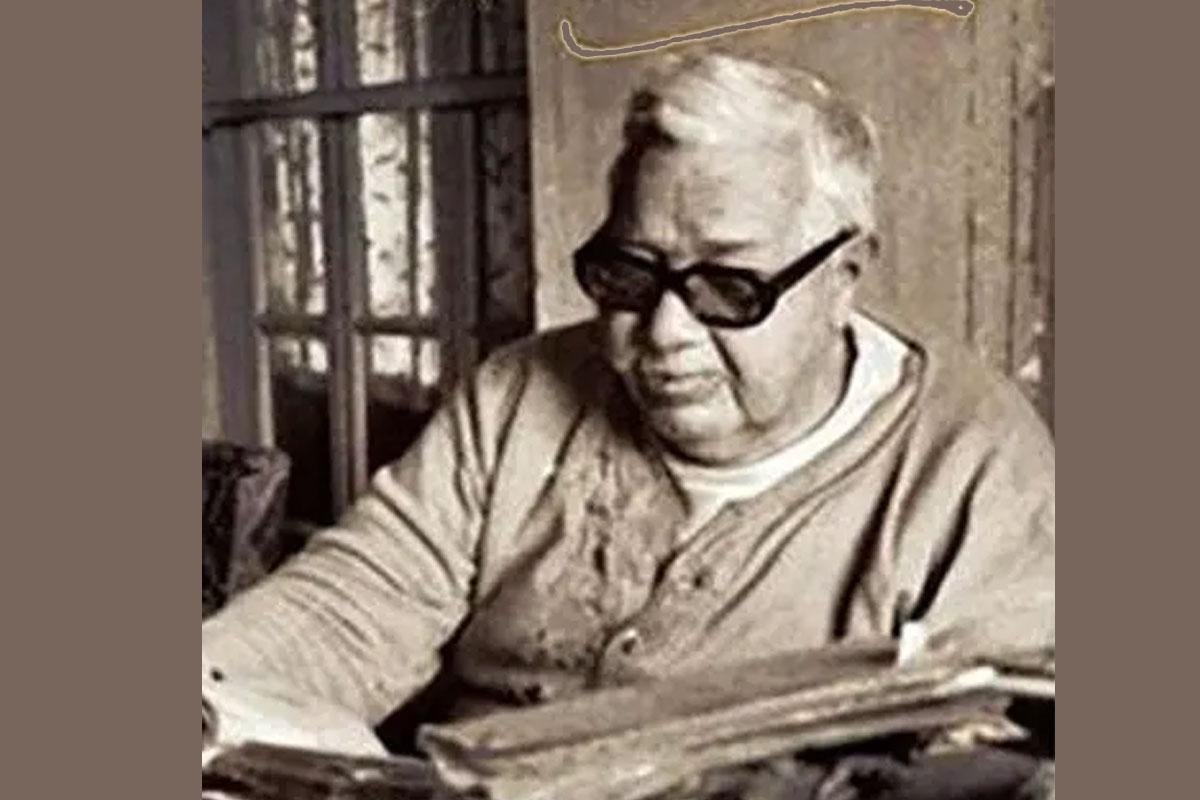স্বপনকুমার মণ্ডল
ধ্রুপদী ভাষা বললেই গ্রিক, ল্যাটিন বা সংস্কৃত ভাষাই প্রথমে মনে আসে। শেষেরটি আবার ভারতেরই ঐতিহ্যবাহী অভিজাত অথচ মৃতপ্রায় ভাষা। সেখানে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি হিসেবে আলাদা ভাবে শিহরণ জাগায়। এমনিতে ভারত উপমহাদেশে ভাষা বৈচিত্রের কথা প্রথমেই চলে আসে। কত বিচিত্র তার ভাষার বনেদি বিস্তার, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। সেখানে সরকারিভাবে ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতি তার প্রাচীনত্বের গরিমায় যেভাবে ২০০৪ থেকে শুরু হয়েছিল, তাতে দেশের দ্বিতীয় জনবহুল ভাষা বাংলার স্থান পাওয়াটা স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যাশিত ছিল। প্রথমে তামিল ভাষা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। এরপর যথাক্রমে সংস্কৃত, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম ও ওড়িয়া ভাষা সেই স্বীকৃতি পায়। অথচ বাংলার সেই গৌরব সময়ের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে থাকে।
যদিও দেশের সবচেয়ে জনবহুল ভাষা হিন্দিও তা পায়নি। অবশ্য তা বাংলার না পাওয়ার যুক্তি বা আত্মতুষ্টি লাভের অজুহাত হতে পারে না। জনসংখ্যার বিচারেও পৃথিবীতে হিন্দিভাষী মানুষের পরেই বাংলাভাষীর স্থান। অথচ বাংলা ভাষার প্রাচীন গৌরব থেকে তার মৌলিক আভিজাত্যের প্রকাশ ও প্রভাব দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। ভারতের ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস ও তার ধারা প্রবাহে বাংলা ভাষার উৎকর্ষমুখর বনেদিয়ানার পরিচয় অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। আধুনিক পরিসরেও তার বহুমুখী বিস্তার তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মধ্যেই প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি ছিল। কুড়ি বছর প্রতীক্ষার পরে আর চারটি ভাষার (মরাঠি,পালি, প্রাকৃত ও অসমিয়া) সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিল। দেরিতে হলেও বাংলা তার প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেদিক থেকে বাংলার ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি তার অস্তিত্বের প্রাচীন ঐতিহ্য ও বনেদি আভিজাত্যের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সিলমোহর মনে হয়। কেননা স্বীকৃতির মধ্যেই অস্তিত্বের সৌরভ ও গৌরব ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রণিধানযোগ্যতাও আনুগত্যহীন আভিজাত্য লাভ করে। সেদিক থেকে বাংলার ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি ছিল অত্যন্ত জরুরি।
বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব বা আভিজাত্য নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই, বরং তার বিস্তৃতি ও প্রকাশের শৈল্পিক আবেদন বিশ্বের বনেদি ভাষার সঙ্গেই একাসনে সমাসীন। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষাই বাংলা। আবার তার জন্মও হয়েছে সেই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে। এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু নোবেল পুরস্কারই পাননি, বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠাও করেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার মননচর্চা থেকে তার সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্যপ্রাচীন ইতিহাস বাঙালি জাতির স্বতন্ত্র আভিজাত্য গড়ে তুলেছে। যে পরিমাণ দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, তা দেশের অনেক বহুল প্রচারিত ভাষাতেও দেখা যায় না। তার সাহিত্যের উৎকর্ষ নানাভাবেই প্রকাশমুখর। দেশের জাতীয় সঙ্গীত থেকে জাতীয় স্ত্রোত্র দুটিতেই বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের অবদান প্রকাশমুখর। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত থেকে শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য বিস্তার বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।
শুধু তাই নয়, বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করেই আন্তর্জাতিক জাতি সংঘের ১৮৮টি দেশের সমর্থনে ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি লাভ করে। এত সবের পরেও বাংলা ভাষার প্রতি এদেশের বিরূপ মানসিকতার বিরুদ্ধে বাঙালির অভিমান যতই মুখর হোক, উদাসীনতাও কম যায় না। সবসময় ভাষার স্বকীয়তা হারানোর ভয় যত জেগে থাকে, ভাষার অস্তিত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে, তার রক্ষায় বা সুরক্ষায় কিংবা অধিকার বা দাবি আদায়ে সক্রিয় উদ্যোগের পরিচয় মেলে না। সেক্ষেত্রে অবশ্য তার বনেদি আভিজাত্য লক্ষণীয়। ধনের প্রতি উদাসীনতাতেও ধনীর প্রাচুর্য ও আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে। সেদিক থেকে বাঙালির নিজস্ব ভাষার গৌরব উদাসীনতার মধ্যেও প্রতীয়মান। যেন বাঙালির ভাষার অধিকার কেউ খর্ব করতে চাইলেও পারবে না। এজন্য তার বনেদি আভিজাত্যের প্রতি একরকমের উন্নাসিকতাবোধেই তার প্রতি উপেক্ষা বা উদাসীনতা তাকে সক্রিয় প্রতিবাদে সামিল করেনি। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্তরে হিন্দি ভাষার দাদাগিরিতে তার নীরবতার আভিজাত্য প্রদর্শন দুর্বলতার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। সেদিক থেকে বাংলা ভাষা ধ্রুপদী স্বীকৃতি হিন্দি ভাষার কলেবরে শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বাঙালির হীনমন্যতায় দাঁড়ি টেনে দিল। শুধু তাই নয়, জনসংখ্যার নিরিখে বাংলা ভাষা এখন ধ্রুপদী ভাষার মধ্যে সর্বোচ্চ জায়গায় শ্রদ্ধা আদায় করার অবকাশ পেল। কেননা স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাতে সবচেয়ে বেশি লোকে কথা বলে।
অন্যদিকে তার শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে । সেদিক থেকে তার ঐতিহ্যশালী অস্তিত্বই তার প্রগতিশীলতার রাজমুকুট হয়ে ওঠে। ওড়িয়া,বাংলা ও অসমিয়া এই তিনটি ভাষাই মাগধী অপভ্রংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে ওড়িয়া আগেই (২০১৪) ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ও অসমিয়ার দাবি স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে। অন্যদিকে এ পর্যন্ত এগারোটি ধ্রুপদী ভাষার মধ্যেই বাংলা ভাষার বিস্তার ও প্রভাব এবং প্রকাশ সবচেয়ে বেশি। সেক্ষেত্রে ধ্রুপদী স্বীকৃতির অভাবে তার সৌরভ ও গৌরব সেভাবে আলোচনার আলো হয়ে উঠতে পারেনি। ধ্রুপদী ভাষার প্রভাবে সেই অভাববোধ আর রইল না। অন্যদিকে তার বিস্তার ও সংরক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান ও স্বীকৃতির বনেদি পরিসরে বাংলা ভাষার গ্রহণযোগ্যতা নতুন করে প্রাণিত হবে,বাঙালির আত্মবিশ্বাসেও জেগে উঠবে বিশ্বাসের বাতিঘর। সেই ঘরের আলোর অভাববোধেই বাঙালি তার ভাষা হারানোর ভয়ে আঁতকে ওঠে, হীনমন্যতায় নিজেদের মধ্যেই ব্যঙ্গবিদ্রুপে, কুৎসা ও সমালোচনায় সক্রিয় হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ধ্রুপদী স্বীকৃতি তার আত্মশক্তিকে সুদৃঢ় করবে, আবার শ্রীবৃদ্ধিকে দেবে বনেদি আভিজাত্য। তাতে আধুনিক প্রগতিশীল পরিসরে তার শিল্প-সাহিত্যের গরিমা হ্রাস করবে না, উল্টে তার ঐতিহ্যের আভিজাত্যের মহিমায় অগ্রগতির পথকেই গৌরবান্বিত করে তুলবে। সম্মান ও স্বীকৃতি যে হাত ধরাধরি করে চলে নীরবে, নিভৃতে, নিরন্তর। এজন্য বাংলা ভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতিতে কোনওভাবেই ছোট করে দেখে বা অস্বীকার করে ছোট করা বা উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন নয়। তা যে বাংলা ভাষারই নয়, বাঙালিরও অনেক বড় প্রাপ্তি, সেকথা আমরা যেন স্মরণে রাখি।