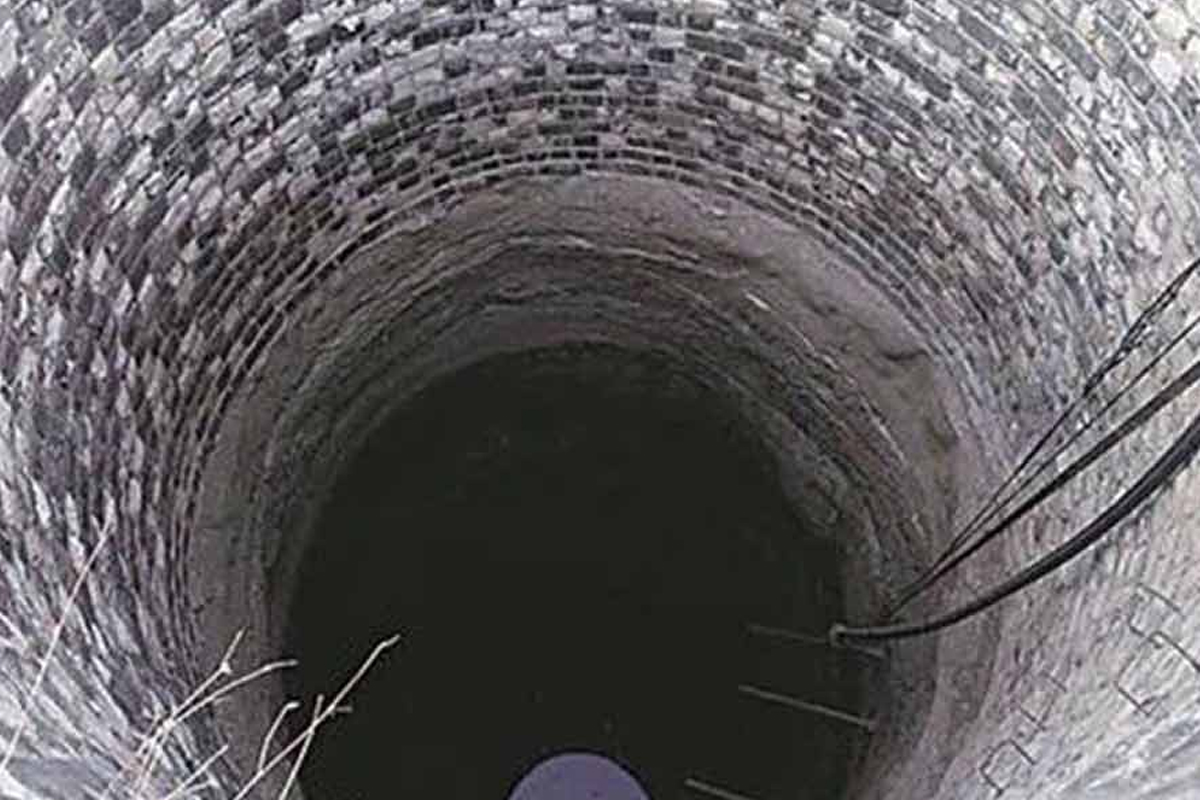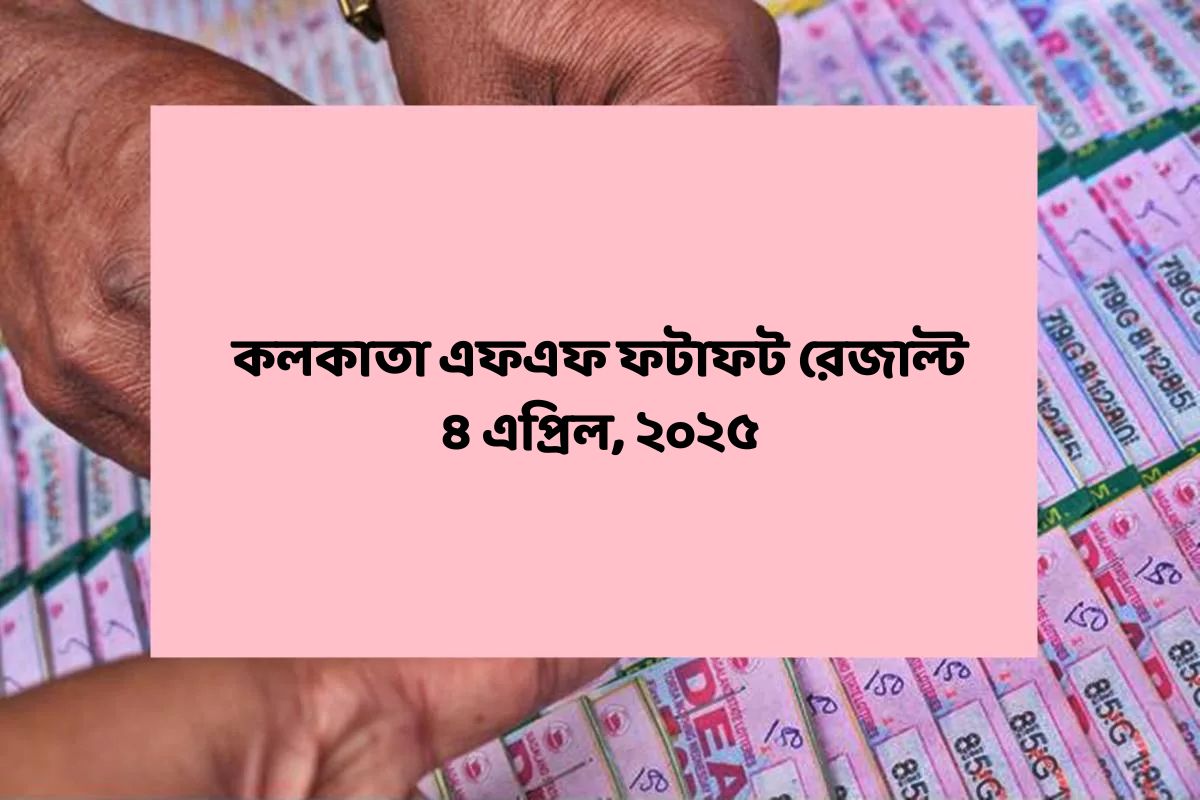মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প বহাল হওয়ার ঠিক পরেই ইজরায়েল-হামাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষনা করা হয়। ঘরে ফেরার আশায় উত্তর গাজ়ায় ভিড় জমাতে থাকেন হাজার হাজার প্যালেস্টাইনি। যদিও স্কুল, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল— যুদ্ধের জেরে ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকুও আর নেই সেখানে। কঠিন পরিস্থিতি, ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির মাঝে এক নতুন আশঙ্কা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ঘরছাড়া প্যালেস্টাইনিদের— গাজ়া নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে তাঁর অভিপ্রায় সম্প্রতি স্পষ্ট করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প— যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজ়াকে ‘সাফ’ করতে তিনি সেখান থেকে সরিয়ে দিতে চান প্যালেস্টাইনিদের। তাঁদের পাঠাতে চান মিশর, জর্ডনের মতো পড়শি রাষ্ট্রগুলিতে। তাঁর দাবি, এই পুনর্বাসন হতে পারে সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ— দুই রাষ্ট্র নীতির বিষয়ে আমেরিকার অবস্থানে কি তবে দাঁড়ি পড়তে চলেছে? প্রাথমিক ভাবে নাকচ করলেও, দুর্বল অর্থনীতি এবং আমেরিকার অনুদানের উপরে নির্ভরতার জেরে আগামী দিনে মিশর ও জর্ডনকে যে ট্রাম্পের প্রস্তাবে সায় দিতে হতে পারে— সে আশঙ্কা থাকছেই। তবে ট্রাম্প তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে, আগামী দিনে এই অঞ্চলের প্যালেস্টাইন-পন্থী মিত্র রাষ্ট্রগুলির থেকে আমেরিকার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষত, পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার অন্যতম উদ্যোগ— ইজ়রায়েল-সৌদি আরব সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা বিপন্ন হতে পারে।
ট্রাম্পের আগমনে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি তো বটেই, ভূরাজনৈতিক সমীকরণ আরও জটিল ও প্যালেস্টাইনিদের দুরবস্থা আরও দীর্ঘায়িত হতে চলেছে বটে।মানবাধিকার সংগঠনগুলি বহু কাল ধরেই ইজ়রায়েলের বিরুদ্ধে ‘এথনিক ক্লেনজ়িং’ বা জাতিগত নির্মূলকরণের অভিযোগ তুলে আসছে। এমতাবস্থায় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের এ-হেন পরিকল্পনা শুধু ইজ়রায়েল-এর চরমপন্থীদের প্যালেস্টাইনিদের উৎখাতের ভাবনাকে পোক্ত করবে না, আগামী দিনে তাঁদের উপরে আরও তীব্র আঘাত হানার পথও প্রশস্ত করবে। সম্প্রতি তেল আভিভ-কে ২০০০ পাউন্ডের বোমা সরবরাহ করার চুক্তিতেও সায় দিয়েছেন ট্রাম্প। ১৯৪৮ সালে ও তার আগে প্রায় সাত লক্ষ প্যালেস্টাইনিকে আরব-ইজ়রায়েল যুদ্ধের জেরে এই অঞ্চল থেকে হয় পালাতে, নয়তো বিতাড়িত হতে হয়। কিন্তু ইজ়রায়েল গঠনের পরে তৎকালীন সরকার উদ্বাস্তুদের পুনরায় দেশে ফিরতে দেয়নি তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে। সেই উদ্বাস্তু এবং তাঁদের উত্তরসূরিরাই আজ ছড়িয়ে রয়েছেন গাজ়া, ইজ়রায়েল অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, জর্ডন, লেবানন এবং সিরিয়ায়। প্যালেস্টাইনিদের তাই আশঙ্কা, এখন গাজ়া ছাড়লে, আর কোনও দিনই সেখানে ফেরা হবে না। অন্য দিকে, পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার ঘনিষ্ঠসহযোগী হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যত প্যালেস্টাইনিদের প্রতি সমর্থন এবং জাতীয় নিরাপত্তার কারণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে মিশর এবং জর্ডন। দুই রাষ্ট্রনেতাই বিলক্ষণ জানেন, উদ্বাস্তু প্রবাহের জেরে তাঁদের রাষ্ট্র পরবর্তী কালে ইজ়রায়েল-এর বিরুদ্ধে জঙ্গি-কার্যকলাপের মঞ্চে পরিণত হবে। উনিশশো সত্তরের দশকের লেবানন-ইজ়রায়েলের সেই ভয়ানক সংঘাতের পুনরাবৃত্তি চান না তাঁরা। মনে রাখা দরকার, গত বছরে এই সংঘর্ষের জের শুধুমাত্র ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ওই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশের কূটনীতি এবং ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। উদাহরণ: ইরান ইজ়রায়েলের সংঘর্ষ।
পশ্চিম এশিয়া দু’টি প্রভাবশালী শিবিরে বিভক্ত। এক দিকে ইরানের প্রভাবান্বিত ‘অ্যাক্সিস অব রেজ়িস্ট্যান্স গোষ্ঠী’ যার মধ্যে আছে হিজ়বুল্লা, হামাস থেকে শুরু করে ইরাকের আইআরআই গোষ্ঠী, এবং ইয়েমেন-এর হুথি মিলিশিয়া গোষ্ঠী; অন্য দিকে ইজ়রায়েল, আমেরিকা ও তথাকথিত ইউরোপীয় বৃহৎ গোষ্ঠী। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা অংশ যদি শুধু ইজ়রায়েল এবং প্যালেস্টাইন সমস্যা হয়, তা হলে অন্য অংশ জুড়ে আছে পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তর জটিল রাজনীতির আঙ্গিক যার অনেকাংশ জুড়ে আছে ইরানকে কেন্দ্র করে নানা রকম সমীকরণ।ইরানের খনিজ সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, এ সব কিছুই তাকে পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাই বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে ইরানের উপর নিয়ন্ত্রণ ‘জ্যাকপট’ পাওয়ার মতো। ১৯৫৩ সালে ব্রিটেন এবং আমেরিকা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মোসাদেককে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে রেজা শাহ পহলভিকে ক্ষমতায় বসায়। ১৯৭৯ সালে যখন আয়াতোল্লা খোমেনি-র নেতৃত্বে ইরানে ইসলামি বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই তখন তা পশ্চিমের ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর পছন্দ হয়নি।অন্য দিকে, ইরান ও বিগত শতকগুলিতে ধীরে ধীরে পশ্চিম এশিয়া যে নিজের প্রভাব ও ক্ষমতা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আমেরিকা জানে যে এই অঞ্চলে তাদের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান, ফলে তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনও সহযোগীকে খুঁজেছে। ইজ়রায়েল তার সেই সহযোগী, ইজ়রায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন করার অন্যতম কারণই এই যে, আমেরিকা কোনও ভাবেই পশ্চিম এশিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে চায় না। সুতরাং, বর্তমানে যদি শুধু ইজ়রায়েল প্যালেস্টাইন সমস্যার আঙ্গিক থেকে কেউ এই সংঘর্ষকে বিশ্লেষণ করতে চায়, তা হলে তা এই সমস্যার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরবে না। অন্য দিকে, ইরানও খুব ভাল ভাবে জানে তাদের কাছে ‘গ্রেটার ইভিল’ আমেরিকা হলেও তার সহযোগী ‘লেসার ইভিল’ ইজ়রায়েলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি এবং তার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইজ়রায়েল-বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করা।
বিগত দশক থেকেই ইজ়রায়েল এবং ইরানের মধ্যে এক ধরনের ছায়াযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, কিন্তু ইরান বা ইজ়রায়েল কেউই সরাসরি একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু ইজ়রায়েল ইরানের ভূ-খণ্ডে এবং তাদের সেনানায়কদের যে ভাবে আক্রমণ ও হত্যা করেছিল, তা ইরানকে ইজ়রায়েলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারই প্রকাশ ঘটে অক্টোবরে ইরানের তেল আভিভ আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। ফলে সমস্যা যে আরও জটিল আকার ধারণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।ইরান বর্তমানে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। ২০১৯ থেকে জ্বালানির দাম বাড়া, কিংবা হিজাব পরা, নানা কিছু নিয়ে নানা বিক্ষোভ চলছে সেখানে। বহির্বিশ্বে ইরানের যে ছবি উঠে এসেছে তা খুব একটা ইতিবাচক নয়। ফলে ইরানের রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার অন্যতম পথ এখন নিজেকে পশ্চিম এশিয়ার রক্ষাকর্তা তথা বৃহত্তর আরব স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পতনের ফলে, আলি খামেনেই যতই বলুন না কেন যে এর প্রভাব অ্যাক্সিস অব রেজ়িস্ট্যান্স-এর উপর পড়বে না। সিরিয়া ভূ-রাজনীতির দিক থেকে ‘অ্যাক্সিস’ এর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। রাশিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে একত্র হয়ে ‘আস্তানা’ প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। সিরিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতাবস্থার উপরই সে সময়ে নির্ভর করছিল ইরাক, জর্ডন, লেবানন এই অঞ্চলগুলির স্থিতি। এই পরিস্থিতিতে ইরানের সিরিয়া নীতির পুরোটাই নির্ভর করছে এইচটিএস ইরানের প্রতি কী নীতি নিচ্ছে তার উপর। এইচটিএস-এর উপর আমেরিকা, ইজ়রায়েল ও তুরস্কের প্রভাব যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে তা ইরান বিলক্ষণ জানে, ফলে সিরিয়ার পরিস্থিতির উপরও তাদের কড়া নজর আছে। সিরিয়ার পরিস্থিতি অতঃপর কোন দিকে এগোয়, সেটা ইরান তথা গোটা পশ্চিম এশিয়ার জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।পশ্চিম এশিয়া যে বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে তাতে এখনই পরিবর্তন হওয়ার আশা কম। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম এশিয়ায় ইজ়রায়েলের শক্তিবৃদ্ধি যে আমেরিকার কাছে আলাদা রকমের সদর্থক ইঙ্গিত বহন করে, সেটা বুঝতে পারা কঠিন ব্যাপার নয়— কারণ ইরানকে সামনে থেকে আক্রমণ করা বর্তমানে আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং আমেরিকা এ ক্ষেত্রে ইজ়রায়েলেরই মুখাপেক্ষী হবে। অন্য দিকে, ইজ়রায়েলও এটা বোঝে যে, ইরানকে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করার চেয়ে পরোক্ষ আক্রমণ করা বেশি ফলপ্রসূ হবে। তাই তারা ইরানের সমর্থনপুষ্ট গোষ্ঠীদের উপরই আবার নিজেদের দৃষ্টি ফিরিয়েছে। এর সুবিধে হল, এক দিকে যেমন প্রত্যক্ষ ভাবে সেই গোষ্ঠী আঘাতপ্রাপ্ত হবে, পরোক্ষ ভাবে তা ইরানকেও সমস্যার মধ্যে ফেলে দেবে। এই গোষ্ঠীগুলির শক্তি হ্রাস ইরানের কর্তৃত্বকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দেবে। ইরান সমস্যায় পড়লে শুধু ইজ়রায়েল নয়, আমেরিকার কাছে পশ্চিম এশিয়ায় এবং উত্তর আফ্রিকায় নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা অনেক সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে আমেরিকা ও ইজ়রায়েলের স্বার্থ এখানে এক ও অভিন্ন।
বাস্তবিক, আমেরিকা হয়তো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইজ়রায়েলকে এমন ভাবে সাহায্য করবে যাতে পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রটি পুনর্নির্মিত হবে। সেই পুনর্নির্মাণে সুবিধে হবে ইজ়রায়েলেরই, এবং ঘুরপথে আমেরিকারও। আবার অন্য দিকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ইরান-সহ পশ্চিম এশিয়ার অন্য অঞ্চলগুলি সহজে তা হতে দেবে না। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে গাজ়ায় যুদ্ধবিরতি আদৌ ওই অঞ্চলে দীর্ঘকালীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। এই জটিল নেতিবাচক আন্তঃসম্পর্কিত রাজনীতির আঙ্গিককে যদি খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষা আবার ধার করতে হয়: “শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াই-এর ধাক্কাতেই সেই শান্তিকে মারে; আজকের দিনে শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কালকের দিনের যে শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, আবার তারই বিরুদ্ধে পর দিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে।” তাই, সত্যিই ‘শান্তি’ প্রতিষ্ঠা হবে না নতুন কোনও শক্তি জেগে উঠবে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া হয়তো আর কিছু করারও নেই। ট্রাম্প সাহেব তো বলেই খালাস, তিনি কি গাজা ভূখণ্ড দখল নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে অবগত? মিশর, জর্ডনের মত দেশে যে মানুষগুলোকে ঠেলে পাঠাতে চাইছেন ট্রাম্প তাদের ভরণ পোষণের অর্থ যোগাবে কে? তাহলে কি গাজা ভূখণ্ড এবার হয়ে উঠবে রিয়াল এস্টেটের ভরকেন্দ্র? প্রশ্ন অনেক,উত্তর দেওয়ার কেউ আছে কি?