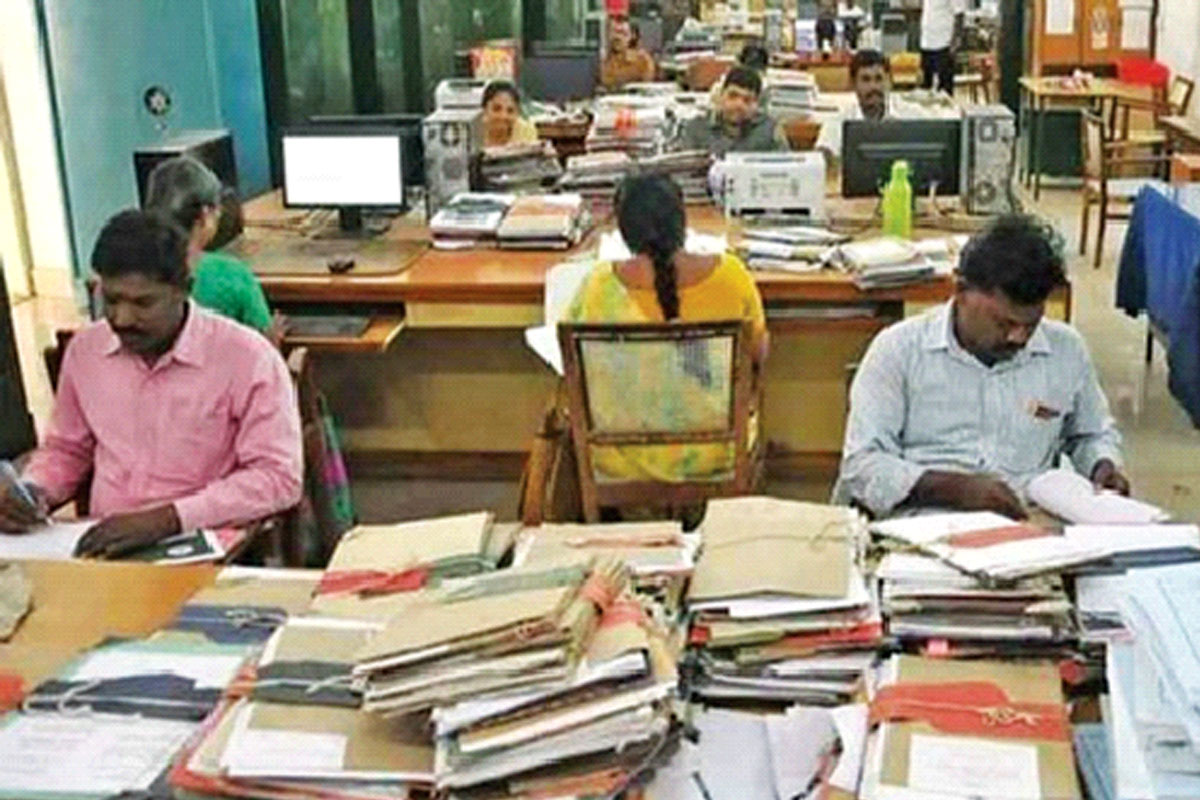শোভনলাল চক্রবর্তী
ভারতের সর্বত্র শ্রম কোড(বিধি) চালু করার দিন ধার্য হয়েছে ১ এপ্রিল, ২০২৫। নাগরিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, এ সবের খোলনলচে বদলে দেওয়ার জন্য যে পরিবর্তনগুলি আনছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার, শ্রম বিধি তার অন্যতম। এই সব সংস্কারের প্রতিবাদ করতে বিরোধী সাংসদরা সংসদের কক্ষ ত্যাগ করেছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ বয়কট করেছেন। তাতে লাভ হয়নি। প্রশ্ন ওঠে, কৃষকদের গণ-আন্দোলনের ফলে কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল কেন্দ্র, শ্রম বিধির বেলায় তেমন কিছু হল না কেন? তার অন্যতম কারণ, যে সব বিরোধী দল সংসদে শ্রমিক বিধির বিরুদ্ধে গলা ফাটাচ্ছে, সংসদ বয়কট করছে, সে সব দলেরই ভোল বদলে যাচ্ছে রাজ্যে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস, সিপিএম-এর মতো দল স্বচ্ছন্দে শ্রম বিধি পাশ করছে। এই দ্বিচারিতা যতটা বিস্মিত করছে, ততটাই হতাশ করছে বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিককে। সিটু, আইএনটিইউসি, ইউটিইউসি প্রভৃতি সংগঠনগুলি সংসদে শ্রম বিধির প্রস্তাব পেশ করার সময় থেকেই তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। মাসখানেক আগে শিলিগুড়িতে শ্রম আইনের প্রতিবাদ করে পথসভা করেছে সঙ্ঘ পরিবারের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘও। যদিও বেশ কিছু বিরোধী রাজ্য-সহ অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই শ্রম বিধি বলবৎ করার উদ্যোগ করেছে, তবু পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার-পাঁচটি রাজ্যের সরকার এখনও অনড়।
তৃণমূল সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছে, শ্রমবিধি চালু করবে না। তবে এই রাজ্যগুলিতেও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে নতুন বিধি কার্যকর হতে পারে। যার অর্থ, একই দেশে শ্রমিকদের অধিকার ও শ্রমিক কল্যাণের জন্য একাধিক আইন চালু থাকবে, শিল্প-শ্রমিক সম্পর্কে জটিলতা বাড়বে। যা কেন্দ্রীয় আইন পাশ করার যুক্তিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। ভারতে প্রচলিত দেড়শোরও বেশি শ্রম-সংক্রান্ত আইনের মধ্যে ঊনত্রিশটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চারটি শ্রমিক বিধি তৈরি করেছে। সেগুলির বিষয় ছিল মজুরি, শিল্পে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, শ্রমিকের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ, এবং শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা। উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আইনগুলিকে সহজ ও সংহত করা। অথচ, শ্রম বিধিকে কেন্দ্র করে সংসদ বয়কট, ধর্মঘট-সহ নানা প্রতিবাদ হয়ে চলেছে।
২০১৯ সালে করোনা অতিমারি চলাকালীন কোনও আলোচনা ছাড়াই সংসদে এই বিধিগুলি পেশ করা হয়, এবং মজুরি সংক্রান্ত বিধিটি চালু হয়ে যায়। বাকি তিনটি শ্রমিক বিধি সংসদের স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। ২০২০ সালে সেগুলিকে কার্যত বিনা বিতর্কে পাশ করিয়ে নেয় কেন্দ্র।শ্রম বিধি বাতিলের দাবিতে গত বছর সেপ্টেম্বরে সারা দেশে হাজার খানেক সভা করেছে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। এগুলির মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস, সিপিআইএম, সিপিআই প্রভৃতি দলের দ্বারা প্রভাবিত নানা ইউনিয়ন। সিপিআইএম-এর মুখপাত্র পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে চারটি শ্রম বিধি শ্রমজীবীদের উপর দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রকল্প, শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হামলা। এর পিছনে রয়েছে নিখাদ শ্রেণি প্রতিহিংসার মনোভাব। অথচ, কেরলে সিপিআইএম পরিচালিত বিজয়ন সরকার ২০২১ সালেই চারটি বিধি চালু করে দিয়েছে। তার কয়েক মাস পরে সিটু-র সর্বভারতীয় সভাপতি কে হেমলতা শিলিগুড়িতে এক সভায় বলেছিলেন যে, কৃষক আইন বাতিলের মতো, শ্রম বিধি প্রত্যাহারের জন্যও আন্দোলন করতে হবে। এর মানে কী? কেবল সিপিআইএম নয়, প্রশ্ন ওঠে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়েও। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম বিধি আনার আগে ২০১৮ সালে রাজস্থানে অশোক গেহলট সরকার শ্রম আইনে এমন কিছু রদবদল আনে, যা নিয়ে সারা দেশে শ্রমিক মহলে প্রতিবাদ শুরু হয়। ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট-এ পরিবর্তন করে কাজের ঘণ্টা বাড়ানো, উৎপাদন কেন্দ্রিক মজুরিকে সব ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি। এই পরিবর্তনগুলো মোদী সরকারকে ‘অনুপ্রাণিত’ করেছিল কি না, সে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।
২০১৯ সালে মজুরি সংক্রান্ত বিধি পাশ হওয়ার পরে, বাকি তিনটি বিধি ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০-তে, বিনা আলোচনাতেই পাশ হয়েছিল, কারণ সে দিন কৃষি বিলের বিরোধিতা করে সংসদ বয়কট করছিলেন বিরোধীরা। অতঃপর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিবৃতি দেন, কৃষকদের পর কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণের লক্ষ্য শ্রমিকেরা। তা হলে সংসদ বয়কট করে বিনা বিরোধিতায় শ্রম বিধি পাশ হতে দিল কেন কংগ্রেস? ২০২০-২০২৩ সালের মধ্যে বিজেপি-বিরোধী বলে পরিচিত অন্তত চোদ্দোটি রাজ্যে শ্রম বিধি চালু হয়ে গিয়েছে। কেরল, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, পঞ্জাব, তেলঙ্গানা, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্য, যেগুলি বিজেপি-বিরোধিতার জন্য পরিচিত, সেগুলিতেও চালু হয়ে গিয়েছে শ্রমিক বিধি। ভারতের আটাশটি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। সব মিলিয়ে ছত্রিশটি, চার-পাঁচটি বাদে বাকিগুলিতে গেজ়েট ঘোষণার মাধ্যমে শ্রম কোডের বিধি-নিয়ম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য শ্রম বিধি গ্রহণ করেনি। কেন্দ্র আপাতত রাজ্যকে ‘বুঝিয়ে বলা’-র নীতি নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গেও আলোচনা জারি রেখেছে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখনও নাছোড় মনোভাব দেখাচ্ছে। কিন্তু রাজ্য-রাজনীতির দিকে তাকালে মনে হয়, এ হয়তো ছায়াযুদ্ধ।অথচ, বিতর্কের প্রয়োজন কিছু কম ছিল না। শ্রম আইনে সংস্কার আনা, শিল্পের প্রয়োজনের নিরিখে আইনে নমনীয়তার প্রয়োজন অনেক দিন ধরেই অনুভূত হয়েছে। সেই সঙ্গে থাকতে হবে উভয় পক্ষের জন্য ন্যায্যতা, কার্যকারিতা। শ্রমিকের দক্ষতা অনুসারে, শ্রমজীবী পরিবারের অত্যাবশ্যক খরচ এবং সামাজিক সুরক্ষার হিসাব কষে মজুরি নির্ধারিত হয়েছে কি না শ্রম বিধিতে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কর্মক্ষেত্রে যে ধরনের নিরাপত্তা দিয়েছে সংবিধানের ধারা এবং সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন নির্দেশ, নতুন শ্রমিক আইনে তা যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে কি না, তা নিয়েওসংশয় রয়েছে।
পানীয় জল, শৌচাগার, ক্রেশ, ক্যান্টিন ইত্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে আইনি নির্দেশগুলি শিথিল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নিয়োগের নকশায় বদল হয়েছে, অথচ গিগ কর্মীদের মতো নতুন শ্রেণির কর্মীদের স্বার্থের সুরক্ষার প্রতি আইন যথেষ্ট মনোযোগী হয়নি। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক, যাঁরা শ্রমিকদের ৯০ শতাংশ, তাঁদের অবস্থা যথা পূর্বং। বিরোধী দল এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি এমন নানা ধরনের ঘাটতি বা শিথিলতার কথা তুলে ধরেছে।এসেছে নানা ধরনের বিকল্প প্রস্তাবও। যেমন, শ্রম আইনের কড়াকড়ি এড়াতে শিল্পগুলি অতি-ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র হয়ে থেকে যেতে চায়, নথিভুক্তি এড়াতে চায়। ভারতে অসংগঠিত শিল্পের অত্যধিক প্রসারের অন্যতম কারণ স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে অনীহা। তাই শ্রমিকদের সুবিধার নির্ণয়ে স্থায়ী-অস্থায়ী বিভেদ তুলে দিয়ে যদি কেবল উৎপাদনশীলতাকেই শর্ত করা যায়, তা হলে শিল্প ও শ্রমিক উভয়েরই সুবিধা হতে পারে। তেমনই, অধিকাংশ শ্রমিক যখন সরাসরি নিয়োগের পরিবর্তে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিযুক্ত হচ্ছেন, তখন ঠিকাদার সংস্থাগুলিকে শিল্পক্ষেত্র অনুসারে নথিভুক্ত করা ও সেই সূত্রে দায়বদ্ধ করার বিধি আনা প্রয়োজন। শিল্প-শ্রম সংঘাতের সাবেক মনোভাব থেকে বেরিয়ে, শ্রমিকের দক্ষতা ও নিরাপত্তার মাধ্যমে শিল্পের উন্নতির পথ খুঁজতে হবে সরকারকে।