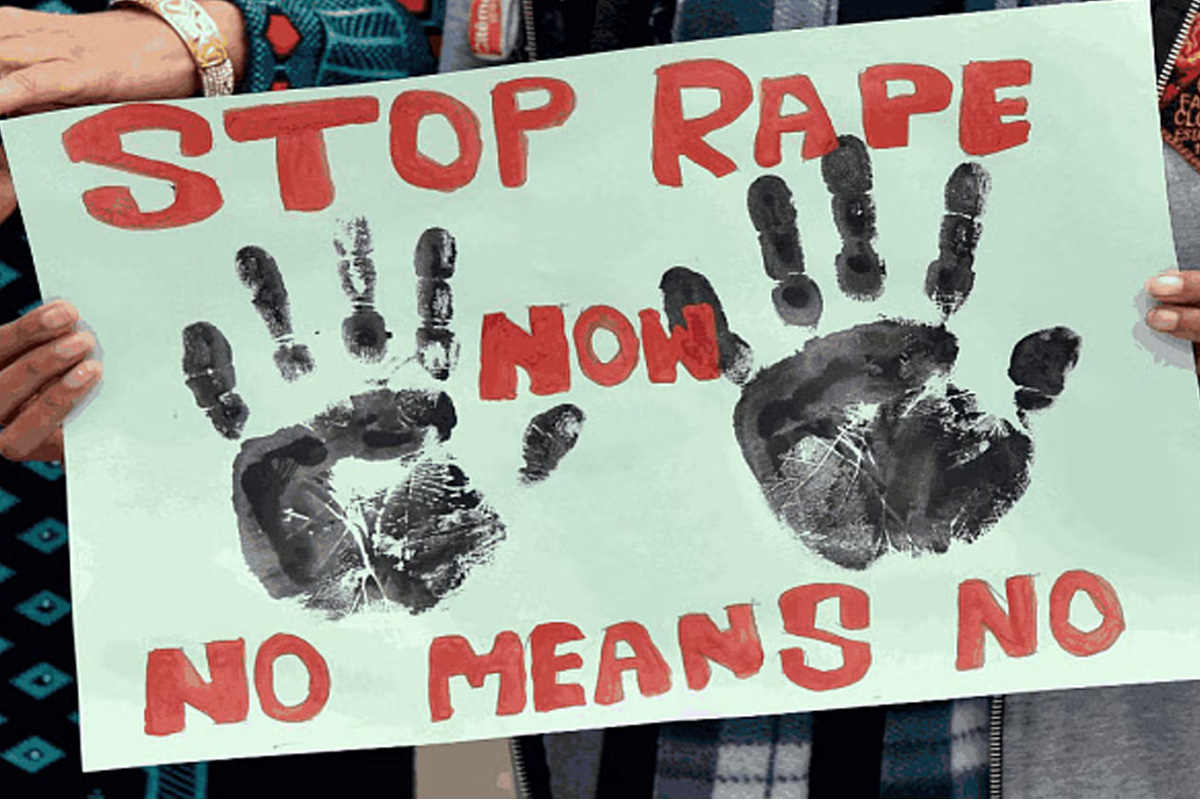জয়ন্তী চক্রবর্তী
‘গাজী মুস্কিল আসান করো দোহাই মাণিক পীর আগে যদি জানতাম বাপু তুমি মাণিক পীর, আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পিছে দিতাম ক্ষীর। গাজী মুস্কিল আসান করো’— পাড়াগাঁয়ের মাটির রাস্তা দিয়ে খালিপায়ে হনহন করে এগিয়ে চলেছেন পীর বাবা। পাশের গাঁয়ে বামুনদের বাড়ি গরুর বাছুর হয়েছে। সেই নবজাত বাছুরের কল্যাণ কামনায় গাভীর দুধ দুয়ে নতুন মালসায় জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরি মাণিক পীর। গৃহস্থের কল্যাণ হবে। গাভী ও তার বাছুর ভালো থাকবে। সন্ধ্যার মুখে দরজায় হাঁক উঠলো “মা মাণিক এয়েছে মাগো। মাণিক।” ডাক শুনে যে যেখানে ছিল ছুটে এলো। মুহুর্তের মধ্যে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরলো বালক বালিকার দল। মাণিক পীর সবার মাথায় চামর বুলিয়ে দিতে দিতে মাণিক পীরের মাহাত্ম্য গান গেয়ে চললেন ‘গাজী মুস্কিল আসান করো—’ এখন আর কোথাও দেখা যায় না সেই মুস্কিল আসান পীরবাবাদের। শুধু মুস্কিল আসান নয় কত কিছুই না ছিল সেদিন। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও দেখেছি বর্ষায় চাষের কাজ শেষ হবার পর যাত্রাপালার আসর বসতো গ্রামে গ্রামে। কারো গলায় ঝুলছে হারমোনিয়াম, কারো মাথায় সাজের বাক্স, কারো হাতে বাজনা বাদ্যির পোঁটলা, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেত পালাগানের দল। সারারাত গান হতো। গ্রামবাসীরাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল ডাল আলু পটল তেল মশলা যোগাড় করে, পুকুর থেকে মাছ ধরে যাত্রা দলকে খাওয়াতো।
তবে নায়ক নায়িকাদের নিমন্ত্রণ হতো কোনো বড় মানুষের বাড়িতে। পথের পাঁচালীর অপুর মা নিমন্ত্রণ করেছিলেন দলের এক কিশোর গাইয়েকে। সে অপুর বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তখন পূজোর দিন পনেরো আগে থেকে বোষ্টম বোষ্টমীরা আসতো আগমনি, বিজয়ার গান গাইতে। বাড়ি বাড়ি গাইত তারা একতারা বাজিয়ে গিরি গৌরী আমার এসেছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্য রূপিনী কোথা লুকালো। আর ছিল মঙ্গল চণ্ডীর গান, মনসার ভাসান, রামায়ন গান। খোলা মাঠে, বা চণ্ডীমণ্ডপে, সামিয়ানার নিচে বসতো আসর। হ্যাজাগের আলো জ্বালানো হতো। এখনকার নিয়ন আলোর মতো কিছুটা। জ্বলে উঠলেই উৎসবের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো চারিদিকে। জমায়েত হতো বাচ্ছা কাচ্ছার দল। শাড়ির পর্দা দেয়া অস্থায়ী সাজঘরে উঁকি ঝুঁকি। “ওইটা রাজা, ওই যে রাণী ওই দেখ তরোয়াল। সকালে আমাকে হাত দিতে দিয়েছিল সেনাপতি।”
সকাল সকাল রাতের খাবার সেরে নিয়ে গোটা পরিবার হাজির হয়ে যেতো যাত্রা দেখতে। কনসার্ট বেজে উঠতো। গরিব, আটপৌরে গ্রাম মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যেতো রূপকথার রাজ্যে। রামায়ন গান হতো তখন গরমকালে, খোলা মাঠের মধ্যে। একটু উঁচু বেদীর ওপর বসে একজন গাইতেন। সহকারী অভিনয় করে দেখাতেন। রাবণের মৃত্যুবাণ আনতে চলেছেন হনুমান গণক ঠাকুরের ছদ্মবেশে। দূর থেকে তাঁকে দেখে মন্দোদরির সখীরা বলছে, “দিদি গো ঠাকুর যায় উল্টো ঝুলকো পশম ঝোলে গায়। গানের সঙ্গে সঙ্গে সহকারি যুবক নামাবলী গায়ে জড়িয়ে হুপ হুপ করে লম্ফ ঝম্প করে যাকে বলে পাড়া মাথায় করতেন। দর্শক ফেটে পড়তো হাততালি তে। এখনো মনে পড়ে মনসার ভাসান গানের কথা। বেহুলা লক্ষীন্দরের পালা। গর্ভবতী হয়েছেন সনকা। চাঁদ সদাগর তখন বাণিজ্যে গেছেন। সনকার সাধ ভক্ষণ করাতে এসেছেন মা মনসার স্বয়ং সখী সেজে। সনিকা তাঁকে জানাচ্ছেন তার প্রিয় খাবারদাবারের কথা ওল ভাতে বেগুন পোড়া পুঁটি মাছের ঝাল চচ্চড়া সড়া তেঁতুল যত দিতে পারো সই গো।
আজকের দিনের যে কেউ নাক সিঁটকাবেন খাবারের ফিরিস্তি দেখে। কিন্তু সেকালের গ্রাম বাংলার রান্না ঘরে এই সবই ছিল ঘটার খাওয়া দাওয়া। হাটে বাজারে না গিয়ে ঘরের উঠোনে, খাল বিল ডোবায় যা হাতের কাছে পাওয়া যেতো, তাই দিয়ে পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াত অতীতের বাঙালি বধূরা। না তাতে পুষ্টির অভাব মোটেই হতো না। বরং রাসায়নিক মুক্ত এইসব শাকপাতায় শরীর হতো মজবুত। চৈত্র সংক্রান্তির দিন পনেরো আগে থেকে সং বের হতো। গাজনের সং। মা দুর্গা, কালী মহাদেব তাঁদের ভূত প্রেত দল সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াতেন। সমাজের নানা দোষ, অসঙ্গতি, আর ভণ্ডামির ভাঁড় ভেঙে দিতে এই সব চৈতে গাজনের সং। ভিক্ষা? না ভিক্ষা নয়। শিল্প, ধর্ম আর আনন্দকে এক সূতোয় বেঁধে এক সঙ্গে শত শত মানুষের আনন্দ ভোজের ব্যবস্থা করা হতো তখন।
ঘরে বসে একা একা পোলাও খাওয়া আর সারা গ্রামের মানুষের সঙ্গে পঙক্তি ভোজনে বসে খিচুড়ি খাবার মধ্যে অধিকাংশেরই সম্ভবতঃ শেষটা পছন্দ। কিন্তু পছন্দ হলেও, আধুনিক সমাজের ইগোর সে ভোজের আনন্দ এখন বিরল। তখন চৈত্রমাসের সন্ধ্যায় মা কাকীরা যেতেন বিবি মায়ের পূজোয়। বিবি মায়ের থানে মোমবাতি জ্বেলে, চিঁড়ে মুড়কির ফলার খেতেন সব মেয়েরা একসাথে বসে। চাঁদের আলোয় সেই ছিল তাদের বনভোজনের আনন্দ। অঘ্রাণ মাসের কুলুই মঙ্গলবার এই রকমই বনভোজনের আসর বসত ফসল ওঠা ভরা খামারের এক ধারে। সুখ দুখের কথা, স্নেহ সহানুভূতির স্পর্শ পরচর্চা পরনিন্দা সবই হতো। তবু তার মধ্যে ছিল নির্মল আনন্দ। ছিল সহমর্মীতা। সেকালে ঘরে ঘরে টিভিতে সিরিয়াল দেখার তাগিদ ছিলনা। বধূরা রিল বানাবার নেশায় নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতো না। তাঁদের যেতে হতো না অফিসেও। মেয়েদের হাতে থাকতো অঢেল সময়। কাঁথা সেলাই করতো তারা পুরানো ছেঁড়া কাপড়, চোপড় দিয়ে।
পাড়ের সুতো তুলে ফুল পাতার নক্সা করতো। শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বড়ি দিতো নানা রকমের। পোস্ত বড়ি, কুমড়োর বড়ি, গয়না বড়ি আচার, আমসত্ব, কাসুন্দি, তিলের নাড়ু, নারকেল নাড়ু, ছাতুর নাড়ু, খয়ের মোয়া, কত রকমারি খাবার বানাতো। এখন সব যেন মনে হয় কোন সুদূর পূর্ব জন্মের কথা।চাইলেও বাংলার একান্ত আদরের সংস্কৃতিকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না।হারিয়ে গেছে বাংলার পটচিত্র। আগে ঝুড়ি ভর্তি পট নিয়ে শিল্পীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পট দেখিয়ে গান শোনাতো। নানান পৌরাণিক বিষয় থাকতো গানের কথায়। ছিল বহুরূপী। পথে ঘাটে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াতো খাড়া হাতে ভয়ঙ্কর মহিষাসুর কিংবা বাঁশরী হাতে কৃষ্ণ অথবা হালুম বলে থাবা উঁচিয়ে ধরা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। হারিয়ে যাচ্ছে এই সব সহজিয়া আনন্দের মাধ্যম গুলো। পরাধীন ভারতে বৃটিশ রাজ বাংলার তাঁতকে ধ্বংস করে দিয়েছিল নিজেদের বস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে। আজ পুরুলিয়ার ছৌ, বীরভূমের বাউল বাঁকুড়ার ঝুমুর, মালদার বোলান, (মড়ার মাথার মুখোশ পরে নৃত্য) ইত্যাদির মতো লোক সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে স্বাধীন দেশ থেকে। জানি না কার স্বার্থে। অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ বিনোদনের নামে একঘেয়ে ছকে বাঁধা গল্প রঙচঙে বাহারি পাত্রে পরিবেশন করছে। এখন গান নাকি জীবনমুখী। সেই এক গীটার, এক সুর, এক ভঙ্গী, এক নৈরাশ্য, ভাঙা সম্পর্কের সেই এক ঢেউ খেলানো দুঃখ বিলাসের পাঁচালী। কোথায় যে হারিয়ে গেলো আমাদের ছোটবেলার সেই মুস্কিল আসান পীর বাবা! কোনো মুস্কিল তাই আর আসান হয় না আজকাল, বরং বেড়েই চলে দিনকে দিন।