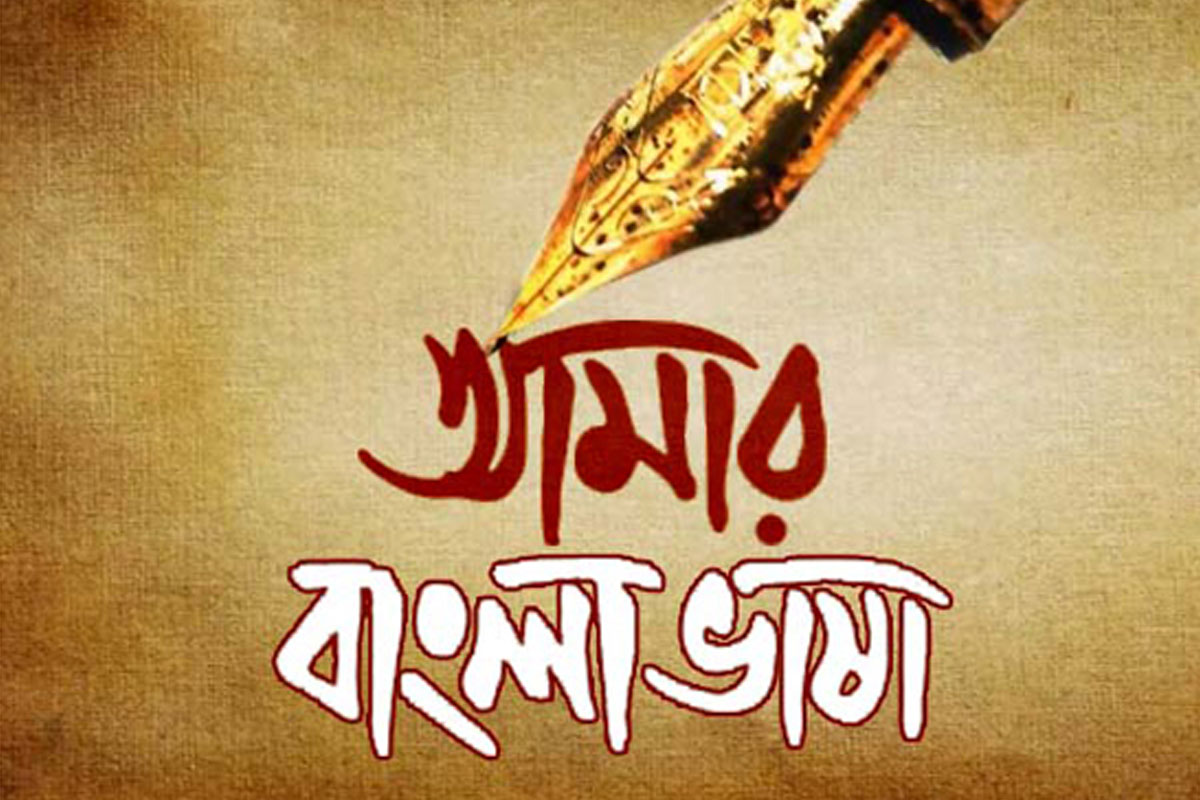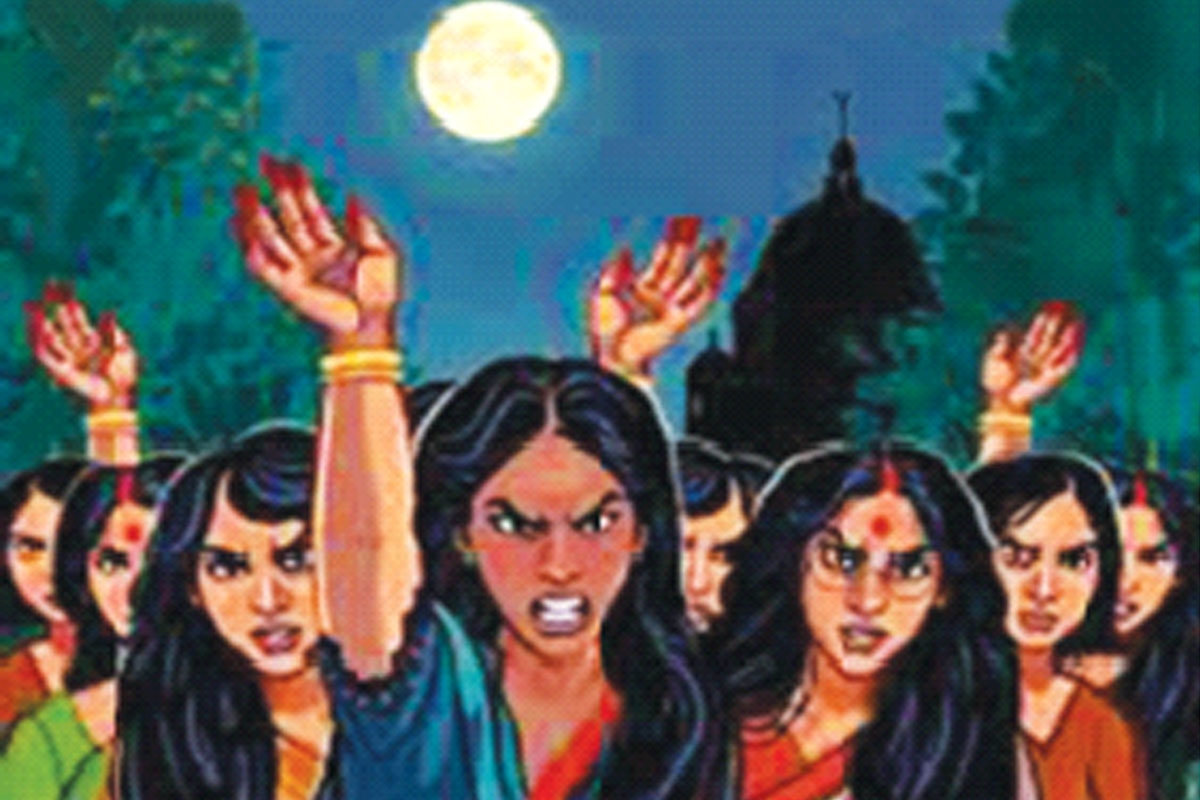আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নীরবতা পালন করি। যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ সূচক সম্মতি চোখেমুখে। বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙালি বড় উদাসীন। প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তা কখনওই গর্বের বিষয় নয়। ‘আ মরি বাংলা ভাষা’র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের উদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙালির বিস্তৃতি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে। প্রাচুর্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য। সেক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা জ্ঞান এখন ভাসা ভাসা। মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে। মাতৃভাষার গৌরববোধই তার ভাষিক চেতনায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। আসলে মা আর মাতৃত্ব যেমন এক নয়, ভাষা ও মাতৃভাষাও স্বতন্ত্র। রামপ্রসাদী গানের কথায় আছে, ‘মা হওয়া কি মুখের কথা / কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা’ কথাটি ধ্রুব সত্য। জন্ম দিলে মা হওয়ার প্রচলিত ধারণার ফাঁকটি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। মায়ের গরিমা তার মাতৃত্বে। সেই মাতৃত্ববোধ সব মায়ের মধ্যে থাকে না। সম্পর্কের আত্মিক যোগে ও তার আন্তরিক বিস্তারেই তার সৌরভ। পশুরাও মা হয়, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কেননা তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটি শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, মাতৃত্বও সেখানে অস্বীকৃত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে সেই মাতৃত্বের সম্পর্ক আজীবন থাকে। অন্যদিকে মা হলেই মাতৃত্ব থাকে না। সন্তানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ নিবিড় না হলে তার মাতৃত্ব জাগে না। সন্তানের মা হলেও সেই মায়ের মাতৃত্ব আত্মসংযোগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেখানে সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে সম্পর্কে মা হওয়া জরুরি। অনেক মা-ই সম্বন্ধে মা হলেও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে মাতৃত্বহীন মা হয়ে থাকে। আমাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে বাংলা শুধু বাংলার ভাষা নয়, বিশ্বের আপামর বাঙালির মাতৃভাষা। বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ মায়ের সম্বন্ধে নয়, মাতৃত্বের সম্পর্কে। বাঙালিত্বের পরিচয়ে তার মাতৃভাষার অসপত্ন অধিকার।
অন্যদিকে বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত। কিন্তু সে আভিজাত্য যেভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়েছে, সেভাবে বাঙালির মুখে বিকশিত হয়নি। আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারের দিকে যতটা আমরা মুখিয়ে থাকি বা থাকতে ভালোবাসি, ততটা অন্যদের ভাষার ঐশ্বর্যকে আপন করায় সক্রিয় হতে পারিনি। অনুবাদের মাধ্যমে সেসব সম্পদ স্বদেশীয় ভাষায় আজও অধরা মাধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যাকিছু হয়েছে, এপার বাংলায় তাও লক্ষ করা যায় না। এজন্য বাঙালির আপনাতে আপনি তুষ্ট প্রকৃতি নিজের ভাষার ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতাই বয়ে এনেছে, বাংলাকেই বাঙালি মাতৃভাষার পরিবর্তে ভাষা করে তুলেছে। এই মানসিকতার মূলেই রয়েছে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে আত্মিক সংযোগের তীব্র অভাব। সেখানে ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতায় তার ভাষিক চেতনায় আত্মিক যোগের অভাবে তার আভিজাত্যবোধ জেগে ওঠে না, উল্টে কাজের ভাষার চাহিদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির মায়ের যোগ অমর একুশের দৌলতে মুখর হলেও তা অন্তরে স্থায়ী হতে পারেনি। কেননা মায়ের সম্বন্ধ অনাদরে উপেক্ষায় একসময় লোকে ভুলে যায়, মনে রাখতে চায় না। অথচ মাতৃত্বের স্মৃতি আজীবন বহন করে, আপন করে রাখে আজীবন। সেই মাতৃত্বের অভাবে অমর একুশে, উনিশে মে বা ১ নভেম্বরের গৌরব আমজনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করেনি, শিক্ষিত সুধীজনের মধ্যেও তার পরিচয় আন্তরিক নয়। সেখানে মাতৃত্বের পরশে মাতৃভাষার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আন্তরিকতার বড় অভাব। ‘কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,/ বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া’র অন্ধ আনুগত্য বা ‘তোমার গরবে, গরবিনী হাম, / রূপসী তোমার রূপে’র আত্মিকতাও কোনোটাই জরুরি নয়। কেননা তার আনুগত্যে আবেগ আছে, যুক্তি নেই ; তার আত্মিকতায় একাত্মতা আছে, স্বতন্ত্র সৌরভ নেই। সেখানে আমার মাতৃভাষা আমার অস্তিত্বই শুধু নয়, সন্তানের কাছে সবার সেরা মায়ের মতো গৌরব তার। বাঙালির মাতৃভাষার চেতনায় সেই আত্মিক অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দুটিরই সক্রিয়তার অভাব এখন আরও প্রকট।
উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে বনেদি আভিজাত্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই ভাষা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষায় পরিণত হয়েছে, আবার তাতে নির্বিকার উদাসীনতাও নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাঙালির ভাষা নিয়ে কোনো রূপ অস্মিতাবোধে আভিজাত্য প্রকাশ পায় না, নিজের মাতৃভাষার মধ্যেও নিজের ভাষা খুঁজে পায় না। শ্রেষ্ঠত্ববোধে পারলে ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষাতে বাঙালিই বাংলা ভাষার দীনহীন অস্তিত্বকে জাহির করে। আসলে বাঙালিদের সঙ্গে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে। এজন্য পুরনো ধারণাতেই বাংলা ভাষার গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্যের ধারাকে আমরা অভ্যাসের বশে বয়ে চলেছি, নতুন করে আর ‘মোদের গরব, মোদের আশা / আ মরি বাংলা ভাষা’র আবেদনকে নিবিড় করতে পারি না। সেখানে বাংলা ভাষার দীনতা নয়, বাঙালির মনের হীনতাবোধই দায়ী। শ্রদ্ধাবোধের অভাব হলে অনাদর বা উপেক্ষাই শুধু স্বাভাবিক হয়ে আসে না, উদাসীনতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে, দুর্বলতাও সক্রিয় হয়। সেই বাঙালির মাতৃভাষার সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাবের মূলে তার সেই মাতৃত্ববোধের তীব্র সংকট। তার মায়ের সম্বন্ধ মাতৃত্বের সম্পর্কে পৌঁছায় না। শৈশবের মাতৃত্বকে মানুষ আজীবন মনের মধ্যে শ্রদ্ধায়, সম্মানে ও ভালবাসায় ধারণ করে চলে। সেখানে আমার মা আমারই মা-এর গৌরব আজীবন সৌরভ ছড়িয়ে যায়। সেই মা সবার থেকে ভালো কিনা বড় কথা নয়, আমার কাছে বড়’র চেতনা সদা সক্রিয়। সেই সক্রিয়তার অভাবে বাংলা আজ সম্পদশালী ভাষা হলেও বাঙালির মাতৃভাষায় গৌরাবান্বিত হয় না। মায়ের গৌরব মাতৃত্বের বিস্তারে। আবার সেই মাতৃত্বের মহত্ব প্রসব না করেও হতে পারে। সারদা দেবীর মতো সবার মা হওয়ার গৌরব শুধু সারদা মায়ের নয়, সমগ্র মাতৃকুলের। সেক্ষেত্রে একের মা অনেকের মা হতে পারে। আর তা হতে পারে মাতৃত্বের আপনত্ববোধে। বাংলা ভাষাকে যদি অবাঙালিদের মধ্যে মা বলে আপন করে নেয় বা নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তা হলে বাঙালির মাতৃভাষার আসল সৌরভ প্রকাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। একের মা হওয়ার মধ্যে মায়ের স্বার্থপরতাই অনেকের মার হয়ে ওঠায় মহত্বের আধার হয়ে ওঠে। এজন্য মায়ের মাতৃত্ব জরুরি। সবাইকে আপন সন্তানের মতো উদার অন্তর্দৃষ্টি সেক্ষেত্রে একান্ত কাম্য। বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেখানে নিজের মায়ের প্রতিই তীব্র উদাসীনতা বর্তমান, সেখানে অবাঙালিদের মধ্যে প্রত্যাশা কল্পনাতীত। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির উগ্রতা কাম্য নয়, আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ। সে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায়!