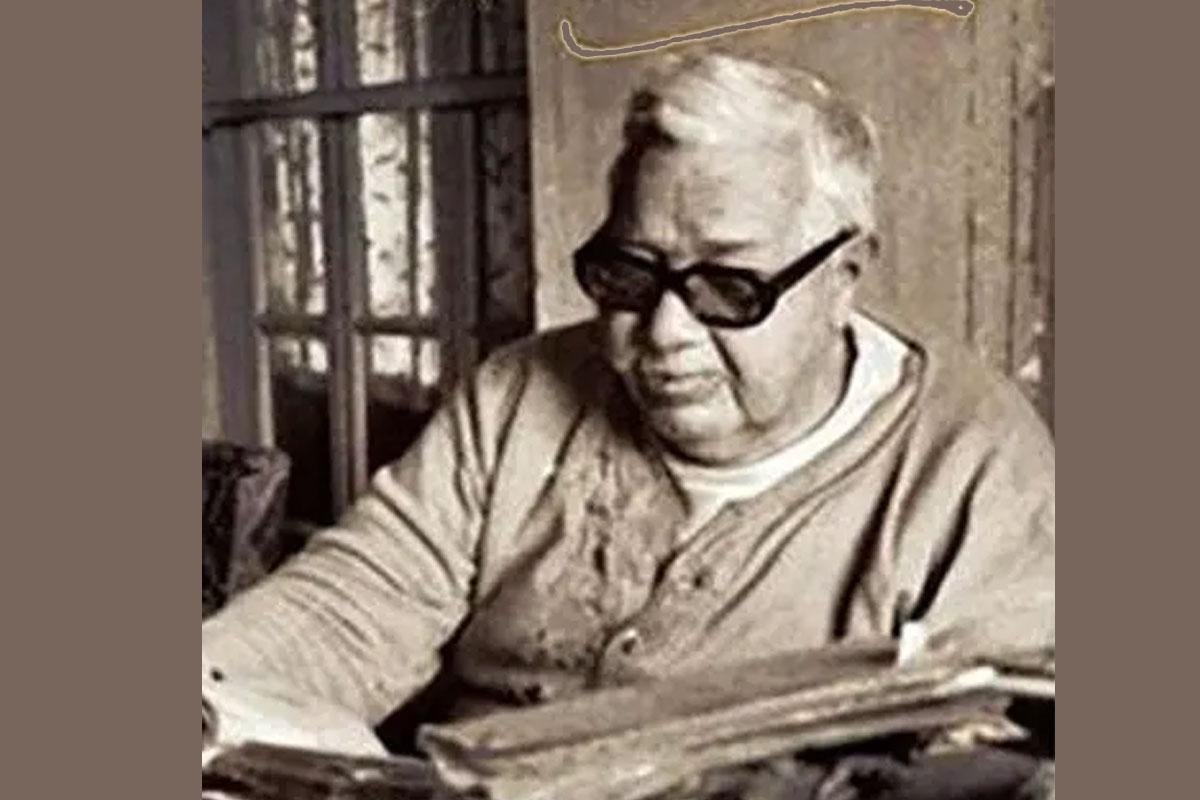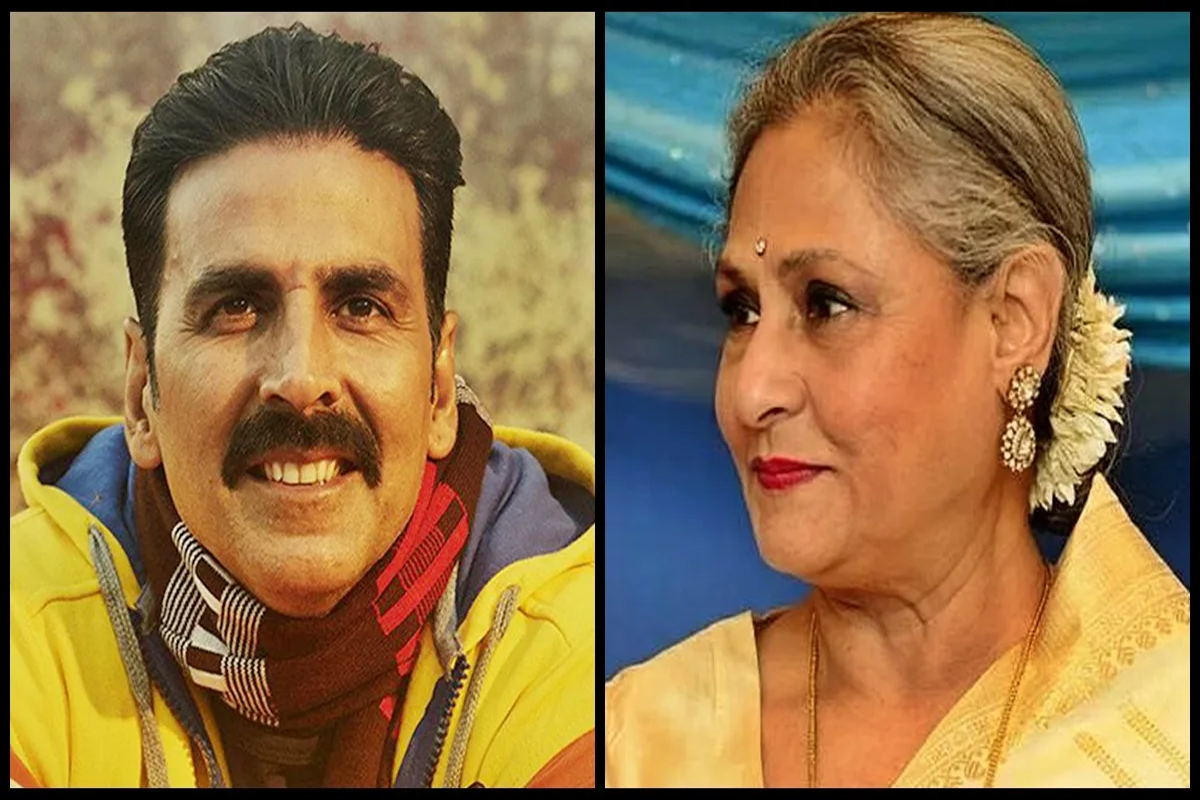শ্রীসুকুমার সেন
পূর্ব প্রকাশিতর পর
কিন্তু কিছু মৌখিক এবং লিখিত ভাষা অবশ্যই ছিল যেগুলোকে আমরা সংস্কৃতের অভিশুদ্ধ উপভাষা বা অপভাষা বলতে পারি। তাদের মধ্যে দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে: ক. মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের ভাষা বা পৌরাণিক উপভাষা, খ. ’বৌদ্ধ’-সংস্কৃত। এছাড়াও পরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার জনপ্রিয় রূপও ছিল যা সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেয়ে সমগ্র পৌরাণিক এবং লৌকিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল। এই ভাষার উপর নির্ভর করেই মহাকাব্য এবং পুরাণের মাধ্যমে আমরা এই লোক-কথার পরিচয় পাই। যাই হোক না কেন, এই মহাকাব্য এবং পুরাণের ভাষা বিভিন্ন কুশলী ও শক্তিশালী লেখক, সম্পাদক এবং লিপিকরদের হাতে আরো সমৃদ্ধ ও সুসংহত হয়ে উঠেছিল। ফলত এর মূল রূপ ধ্রুপদী সংস্কৃতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।
উত্তর ভারতের বৌদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রগুলিকে আমরা ’বৌদ্ধ’-সংস্কৃত হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এবং গ্রীসীয় এবং কুষাণযুগে ভারতবর্ষে রাজদরবারে ’বৌদ্ধ’-সংস্কৃতই রাজভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। আসলে এই ’বৌদ্ধ’-সংস্কৃত মধ্য ভারতীয় আর্যেরই বিশিষ্ট রূপ।
কালক্রমে আর্যভাষা ক্রমশ তিনটি স্তর অতিক্রম করেছিল। কালানুক্রমিক বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও যে সময় এতে ধরা হয়েছে তাকে অভ্রান্ত বলে ধরা ঠিক হবে না। যে কোনও ভাষারই কালানুক্রমিক বিবর্তন অনুধাবন করতে গেলে তার সময় মোটামুটি আনুমানিক ধরে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। তবে একথাও মানতে হবে বৈজ্ঞানিক এবং যথাযথ সময় নির্ধারণ কাম্য হলেও কখনোই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ ভাষা সর্বসময়েই পরিবর্তনশীল। যাই হোক আর্য ভাষার স্তরবিভাগ এইরকম—
ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা : খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৬০০ অব্দ।
খ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা : খ্রীস্টপূর্বাব্দ ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ।
গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা : একাদশ শতাব্দ থেকে বর্তমান কাল।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক ভাষার বৈশিষ্ট্য
ক. শব্দ ভাণ্ডার অনেকটা স্বতন্ত্র। বৈদিক ভাষার অনেকশব্দই ধ্রুপদী সংস্কৃতে রক্ষিত হয়নি, যথা— ক্রবিস্, ত্বষ্ট।
খ. স্বরাঘাত তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ স্বরাঘাতের দ্বারা শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয়। যথা অপস্ (কার্য, ক্লীব) অপস্ (কার্যক্ষম, পুংলিঙ্গ)।
গ. অসংযুক্ত দ্বি-স্বরধ্বনি পাওয়া যায়— তিতউ, প্রউগ।
ঘ. ধাতু বিশেষ্য সুপ্রচলিত, যথা—প্রজা এবং দৃক্।
ঙ. আবেস্তা ও গ্রীকের মতো ধাতুরূপে আগমের ব্যবহার ঐচ্ছিক।
চ. শব্দরূপে একাধিক বিভক্তির প্রয়োগ ছিল, যথা— নরাঃ, নরাসঃ।
ছ. নিষেধ (injunctive) ভাব সুপ্রচলিত ছিল, যথা— মা কার্ষী।
জ. তিন ধরনের (অর্থাৎ অসম্পন্ন বা imperfect, সামান বা aorist এবং সম্পন্ন বা perfect) অতীত কালের ব্যবহার।
ঞ. ধ্রুপদীর তুলনায় অদাদিগগণের ধাতুর সংখ্যাধিক্য।
ধ্রুপদী সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্য
ক. সন্ধির নিয়ম কানুন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হতে লাগল। অসংযুক্ত দ্বি-স্বরধ্বনি সম্পূর্ণভাবে বাতিল হল, যথা— বৈদিক সো অস্তি, ধ্রুপদী সোহস্তি।
খ. কেবলমাত্র বিদেশী শব্দই নয় দেশী শব্দও শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হল। বিদেশী: দ্রম্য (গ্রীক দ্রাখমে), সমিতা (গ্রীক সেমিদালিস); দেশী : উলুপ (তামিল উলবৈ)।
গ. সমার্থক শব্দবিভক্তি সম্পূর্ণ রূপে বর্জিত হল।
ঘ. নির্বন্ধভাবে বিলোপ ঘটলেও কোনো কোনো ‘মা’ এই অব্যয়ের সঙ্গে নিষেধ কোথাও কোথাও রক্ষিত ছিল।
ঙ. সমাসের বিপুল প্রয়োগ শুরু হল।
এই আলোচনা থেকে বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে ধ্রুপদী সংস্কৃতের পার্থক্য এভাবে বলা যেতে পারে:
ক. ‘এ’ এবং ‘ও’ বৈদিক ভাষায় (আবেস্তার মতো) দ্বি-স্বর ধ্বনির মর্যাদা পেলেও ধ্রুপদী সংস্কৃতে স্বরৈকধ্বনি (monophthong) হিসাবে গ্রাহ্য হল।
খ. ইন্দো-ইউরোপীয় পুরস্তালব্য চ ছ জ ঝ বৈদিকে রক্ষিত হলেও ধ্রুপদী সংস্কৃতি ঘৃষ্টধ্বনিতে পরিবর্তিত হল। (ক্রমশ)