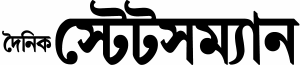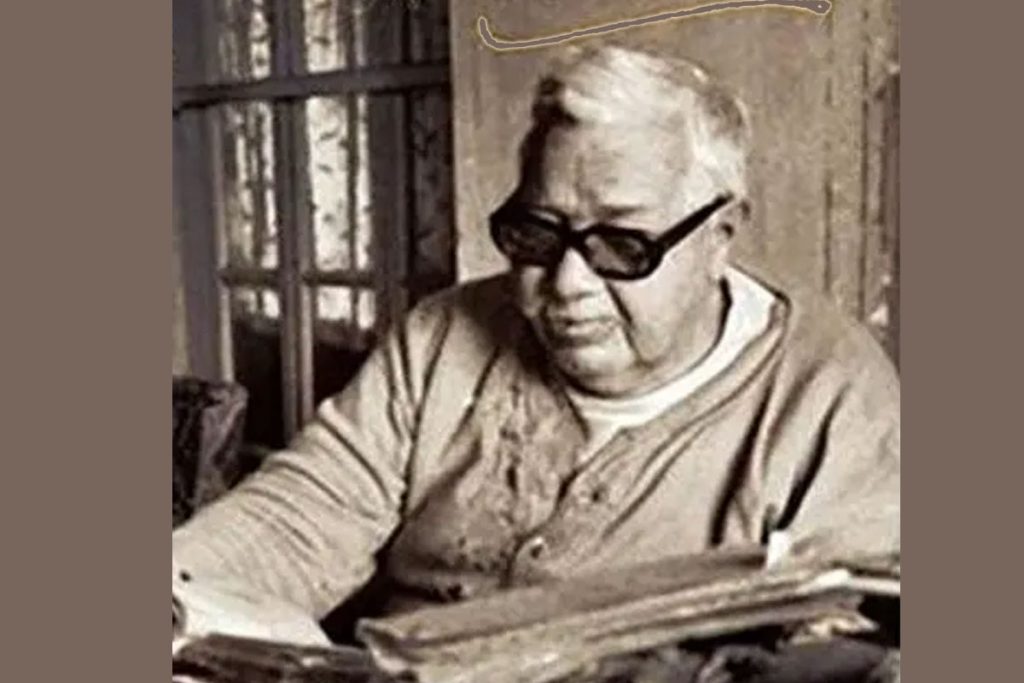শ্রী সুকুমার সেন
পূর্ব প্রকাশিতর পর
বাবার ছোট ভাই হল ‘খুড়া’ (খুড়ো), সংস্কৃস *ক্ষুদ্রক (অথবা *ক্ষুদ্রতাত তালনীয় সার্ধভাষায় ‘খুল্লতাত’) থেকে। খুড়ার সন্তান হল ‘খুড়ুতা’ (মধ্য বাংলা; সংস্কৃত * ক্ষুদ্রক পুত্র থেকে) এখন ‘খুড়তুতো’ ভাই বা বোন। খুড়ার স্ত্রী ‘খুড়ি’ (সংস্কৃত *ক্ষুদ্রিকা অথবা *ক্ষুদ্রার্ষিকা থেকে)। এমনি ‘পিসতুতো’, ‘মাসতুতো’।
‘খুড়া’, ‘খুড়ি’ শব্দের বদলে এখন বেশি চলে ‘কাকা, কাকি’। ‘কাক’ এসেছে ফারসী থেকে। সে ভাষায় মানে হল বাবার ভাই, বড়ো ভাই, অথবা বুড়ো ক্রীতদাস। কাকি তৈরি হয়েছে বাংলায় কাকা থেকে।
পুত্রের (অথবা কন্যার) পুত্র হল নাতি, সংস্কৃত নপ্তৃক (নপ্তৃ+ক) থেকে। সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ ছিল পুত্র, পৌত্র, সন্তান, বংশধর। সংস্কৃতে পরে ‘পৌত্র’ শব্দ বেশি চল হয়েছিল। পুত্রের (অথবা কন্যার) কন্যা হল ‘নাতনী’ (মধ্য বাংলা)। ‘নাতনী’ (শব্দটির একটু ভিন্ন রূপও পাওয়া যায়, ‘নাতিন’।) স্ত্রীলিঙ্গ, বাংলা শব্দটি এসেছে আনুমানিক শব্দ *নপ্তৃণী থেকে। নাতির স্ত্রী ‘নাতিবউ, নাতবউ’, নাতনির স্বামী নাতি-জামাই, নাত-জামাই।’
পৌত্রের পুত্র অর্থে পড়িনাতি শব্দটি মধ্য বাংলায় মিলেছে এ অর্থে সংস্কৃতে পাই ‘প্রণপ্তৃ’ শব্দ। অনুমান হয় বাংলা শব্দটি এসেছে, *প্রণপ্তৃক থেকে।
সংস্কৃত ‘পুত্র’ ও ‘পুত্রক’ থেকে আগত বাংলা পুত ও পুতা শব্দ এখন অপ্রচলিত। কিঞ্চিৎ চলিত আছে পো শব্দ। এটি এসেছে সংস্কৃত * ‘পোত’ শব্দ থেকে। গাছের চারা অর্থে ‘পুয়া’ বা ‘পোয়া’ শব্দ ‘পো’-র সমার্থক। ভাইয়ের ছেলে ভাইপো, বোনের ছেলে বোনপো। পুত্র ও কন্যা অর্থে কোন কোন অঞ্চলে ‘বেটা’ ও ‘বেটি’ (‘বিটি’) শব্দ চলিত আছে। ঈষৎ নিন্দার্থক অর্থে শব্দ দুটি চলিত ভাষাতেও সচল আছে। ‘বেটি’ ‘বেটা’ থেকে তৈরি স্ত্রীলিঙ্গ রূপ। ‘বেটা’ এসেছে সংস্কৃত ‘বিষ্টি’ শব্দ থেকে, মানে বেগার খাটুনি। পুত্র পিতার কাজে সাহায্য করে কিন্তু সে কোন মাইনে পায় না। তাই স্নেহ ও কৌতুক বশে কম্পিত হয়েছে বেগার শ্রমিক বলে।
এখন বাংলায় চলিত শব্দ হল ছেলে। মধ্য বাংলায় ছাবাল, ছাওয়াল, *ছবিল (সংস্কৃত) মানে ছবির মতো সুন্দর। (খুব শিশু হলে ‘কচি ছেলে’।) ‘ছেলে’র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে ‘ছা’, ‘ছানা’ (যেমন, ‘কাকের ছা’, পাখির ছানা’) শব্দের।
‘ছেলে’ সন্তান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ‘বেটা ছেলে’, ‘মেয়ে ছেলে’।
কন্যা সন্তান অর্থে এখন মেয়ে শব্দ। এ এসেছে সংস্কৃত মাতৃকা (মানে ছাট্ট মা) থেকে। কোন কোন অঞ্চলে, যেখানে কন্যা সন্তান অর্থে ‘বিটি’ (প্রচলিত, সেখানে কিন্তু ‘মায়্যা’ (*মেয়ে) বোঝায় স্ত্রীকে।
মধ্য বাংলা পর্যন্ত কন্যা সন্তান অর্থে ঝি শব্দ চলিত ছিল। এটি এসেছিল সংস্কৃত দুহিতা থেকে। এখন শব্দটি ব্যবহৃত হয় বাড়ীর দাসী বোঝাতে। শব্দটির একটু রেশ আছে ‘ঝিয়ারি’ (মধ্য বাংলা) ও ‘ঝিউরি’ শব্দে। দুটি শব্দই এসেছে সংস্কৃত আনুমানিক *দুহিতাবরী (মানে, শ্রেষ্ঠমেয়ে শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে বাড়ির কন্যা সন্তানেরা। উঢ়িষোয় ‘ঝিয়ারি’ বোঝায় বাড়ির ভাসুরের মেয়েকে। তাছাড়া, ‘ভাইঝি’, বোনঝিও চলিত আছে।
বোনের ছেলে এবং স্বামীর বোনের ছেলে ভাগনা, ভাগনে (সংস্কৃত ভাগিনেয়) থেকে। বোন এসেছে ‘ভগিনী’ থেকে। এ শব্দটির মধ্যে একটু সুপ্রাচীন ইতিহাস লুকিয়ে আছে। ‘ভগিনী’ শব্দটির মানে ঐশ্বর্যশালিনী। শব্দটি উৎপন্ন হয়েছিল সেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যেখানে পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত কন্যাসন্তান অথবা দৌহিত্র।
(ক্রমশ)