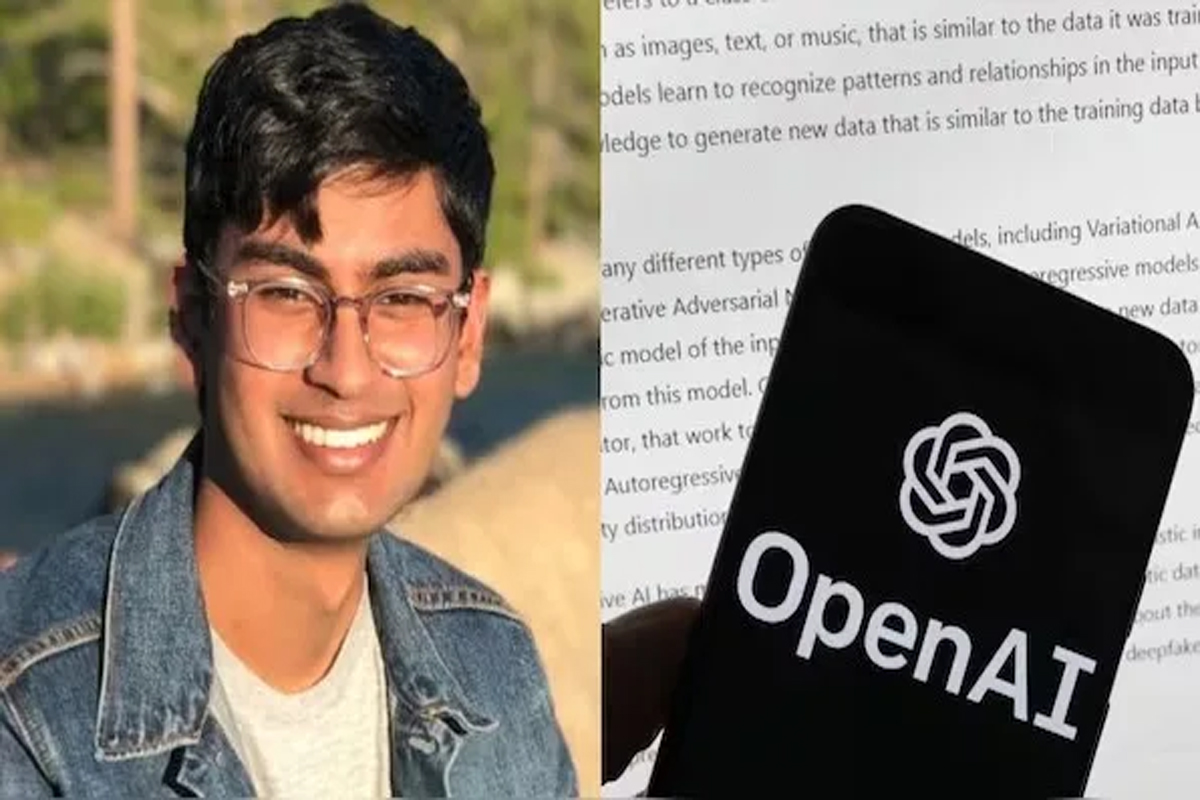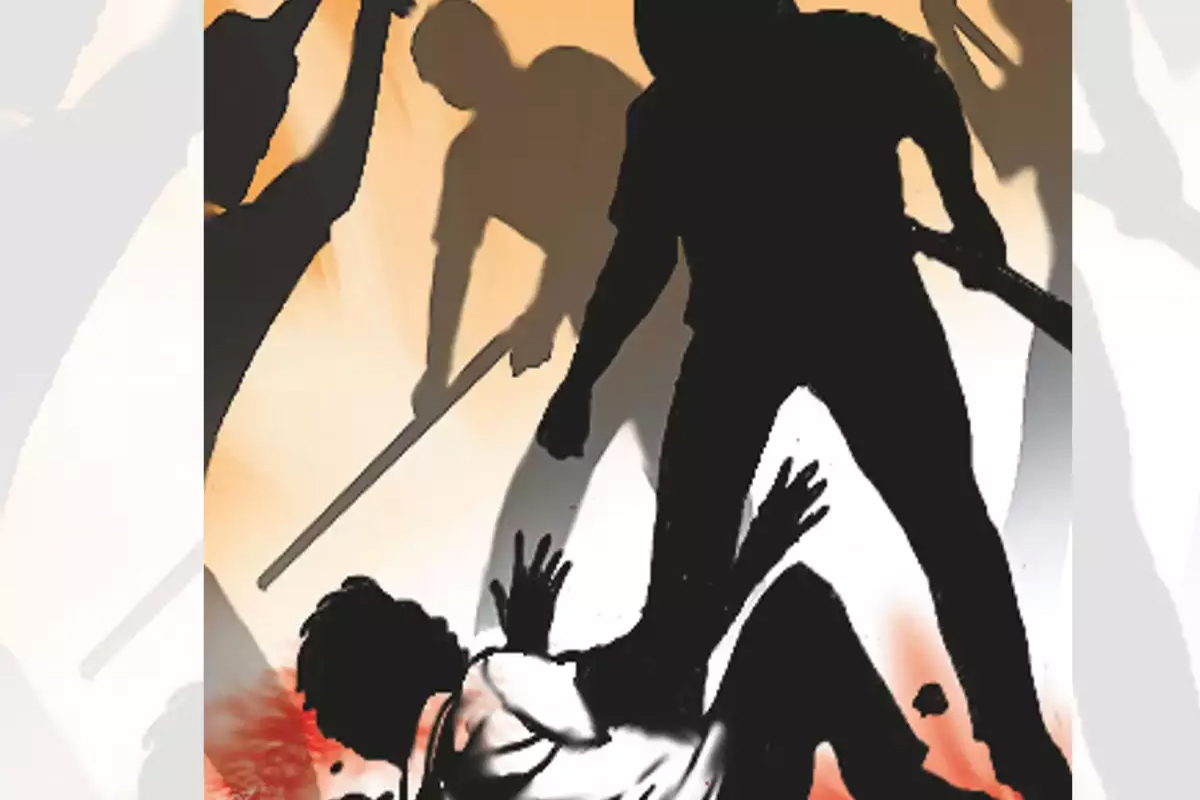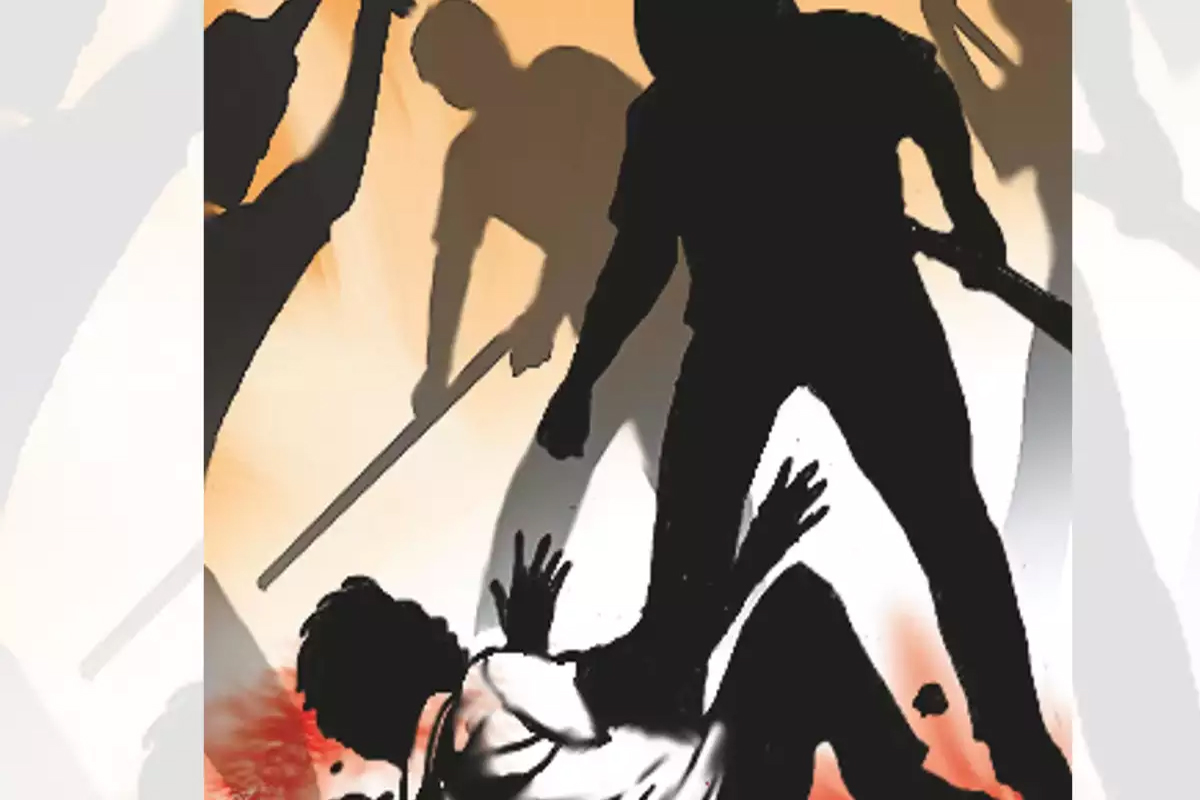সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী
দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শহিদ হলেন সিলিকোসিস অসুখে আক্রান্ত শ্রমিক মইদুল। এর আগেও একই অসুস্থতায় কমবয়সি বৌটার চোখের জল ঝরিয়ে চলে গেছেন খাদান শ্রমিক মাধব মণ্ডল। বাজি ফেলে বলা যায় যে, মইদুল বা মাধব মণ্ডল কেউ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ-এর নামও শোনেননি। স্রেফ ওরা কেন, পাথর খাদানে কাজ করা বা নির্মাণ কাজে যুক্ত ওদের মতো অন্য শ্রমিকরাতো বটেই, আমরাও অনেকে শুনিনি এনআইওএসএইচ-এর নাম, যারা ঠিক করে দেয় মুখোশের স্ট্যান্ডার্ড। সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলোর সঙ্গে করোনার দৌলতে আমরা ইদানিং কিছুটা পরিচিত। এন ৯৫, এন ৯৯, এন ১০০ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মুখোশ বা রেসপিরেটরগুলির কোনোটাই কিন্তু করোনার মোকাবিলার জন্য তৈরি হয় নি, হয়েছিল সিলিকোসিস জাতীয় অসুখ থেকে সুরক্ষা দিতে। সিলিকা হল একধনের ক্রিস্টালের মতো মিনারেল যা বালি পাথর কোয়ার্টজ-এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাথর খাদানে যাঁরা কাজ করেন, যাঁরা নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিক তাঁদের মধ্যে এই সিলিকোসিস বেশি দেখা যায়।
এই লেখাটা যখন লেখা হচ্ছে সেই মুহূর্তে কোনো এক হাসপাতালের ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে আছেন কোনো না কোনো মাধব মণ্ডল বা মইদুল। অল্প বয়স। বাইশ-চব্বিশ। মাথার কাছে অল্পবয়সি বউ বা বয়ষ্কা মা হয়তো হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। নিঃশ্বাসের কষ্ট। অক্সিজেন চলছে।
১৯৯৯ সালের এক সমীক্ষায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ দেখেছিল যে, আমাদের দেশে প্রায় তিন মিলিয়ন মানুষের হাই এক্সপোজার হয়, এদের মধ্যে ১.৭ মিলিয়ন খনি বা খাদানে কাজ করা শ্রমিক, ০.৬ মিলিয়ন কাজ করে নন-মেটালিক পণ্য উৎপাদনে যেমন কাচ ও মাইকা, ০.৭ মিলিয়ন হল মেটাল ইন্ডাস্ট্রি। এছাড়াও নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ৫.৩ মিলিয়ন হাই-রিস্ক এক্সপোজারের শিকার।
গোটা দেশেই এই সিলিকোসিস রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে আছে কমবেশি। বেশি হল গুজরাট, রাজস্থান, পন্ডিচেরি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা এবং বাঙলার পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলোর কিছু অংশে। রোগের প্রাদুর্ভাবের হার বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন রকম, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ৩.৫% থেকে স্লেট-পেনসিল শিল্পে প্রায় ৫৫% অবধি।
ইট, পাথর, সুরকি, কংক্রিটে থাকা সিলিকা গুঁড়ো গ্রাইন্ডিং, ক্রাসিং, ড্রিলিং-এর সময়ে শ্রমিকদের ফুসফুসে ঢোকে। ১০ মাইক্রন বা তার চেয়ে ছোট সাইজের এই কণাগুলি ফুসফুসের একেবারে গভীরে গিয়ে বাসা বাঁধে।
প্রথম চোটে শুরু হয় নিঃশ্বাসের কষ্ট, শুকনো কাশি, জ্বর। এরপরে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, নখের রং নীলচে। রাতে ঘুমাতে কষ্ট, বুকে ব্যথা। এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে যক্ষ্মা রোগও হয়। ক্রনিক সিলিকোসিস হলে গোটা ফুসফুসের বারোটা বেজে যায়।
সিলিকোসিস ছাড়াও অকুপেশনাল ডিজিজ বা পেশাগত অসুখ আরো আছে। অকুপেশনাল ইনজুরি, অকুপেশনাল লাং ডিসিজ বা ফুসফুসের অসুখ, অকুপেশনাল ক্যানসার, অকুপেশনাল ডার্মাটোসিস বা ত্বকের অসুখ, অকুপেশনাল ইনফেকশন, অকুপেশনাল টক্সিকোলজি, অকুপেশনাল মেন্টাল ডিসিজ বা মানসিক অসুখ ও অন্যান্য।
রোগের কারণের দিক থেকে যেভাবে ভাগ করা যায় সেগুলো হ’ল: অকুপেশনাল ইনজুরি, কেমিক্যাল ফ্যাক্টর যেমন ধুলো, গ্যাস, অ্যাসিড, অ্যালকালি, ধাতু ইত্যাদি ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর যেমন আওয়াজ, উত্তাপ, বিকিরণ ইত্যাদি বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর, বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টর, সোশ্যাল ফ্যাক্টর ইত্যাদি।
মইদুল বা মাধব মণ্ডল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হু-এর পুরোনো তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে ১০০ মিলিয়ন অকুপেশনাল ইনজুরি এবং তার থেকে ০.১ মিলিয়ন মৃত্যু হয়েছে। ভারতে প্রতি বছর ১৭ মিলিয়ন নন-ফেটাল অকুপেশনাল ইনজুরি (বিশ্বের ১৭%) আর ৪৫,০০০ ফেটাল ইনজুরি (বিশ্বের ৪৫%) হয়। গোটা বিশ্বের অকুপেশনাল ডিজিজ-এর যে ১১ মিলিয়ন কেস হয় তার মধ্যে ভারতের কেস ১.৯ মিলিয়ন (১৭%) আর বিশ্বের ০.৭ মিলিয়ন মৃত্যুর মধ্যেও ভারতের অবদান ওই ১৭%। মইদুল বা মাধব মণ্ডল বাঁচবে না। কোনো ওষুধ নেই। অক্সিজেন দিয়ে ক’দিন একটু বাঁচিয়ে রাখা মাত্র। আজ থেকে অনেক বছর আগে ১৯৫৯ সালে ২৯ ডিসেম্বর প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সেমিনারে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শিরোনাম ছিল, ‘দেয়ার ইজ প্লেনটি অফ রুম অ্যাট দ্যা বটম: অ্যান ইনভেনশন টু এন্টার আ নিউ ফিল্ড অফ ফিজিক্স।’ ওই বক্তৃতাটি ‘ন্যানোটেকনোলজি’ নামে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এক নতুন শাখার জন্ম দেয়। ছোট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণ তৈরির সাহায্যে প্রগতির পথে যাত্রার সেই শুরু। এই প্রসঙ্গে ফাইনম্যান একটি আনুষঙ্গিক ধারণারও জন্ম দেন। তাঁর ছাত্র এলবার্ট হিবস-এর সাহায্যে। নাম দেন ‘সোয়ালোইং ডক্টর’ বা ‘ডাক্তারকে গিলে খাওয়া’। না, অবশ্যই সত্যিকারের কোনো ডাক্তারকে গিলে খাওয়া নয়। হিবস কল্পনা করেছিলেন ন্যানো টেকনোলজির সাহায্যে তৈরি কোনো রোবোটিক প্রযুক্তি যার সাহায্যে কোনো সত্যিকারের ডাক্তার রুগীর দেহে ওই রোবট ঢুকিয়ে অণুবীক্ষণ স্তরে অস্ত্রোপচার সহ অন্যান্য রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে পারবে।
যদি ফাইনম্যান আর হিবস-এর স্বপ্ন পূরণ হতো, সত্যিই যদি আজ ডাক্তারকে গিলে খাওয়া যেত। কোনো এক ন্যানো রোবট পরম মমতায় মইদুলের ফুসফুসের প্রতিটি কোষ থেকে সরিয়ে দিত সেই ধূলিকণা। আবার শ্বাস নিতে পারতো ছেলেটা প্রাণ ভরে।
তাহলে কি কেবল হাতে হাত দিয়ে ইস বলবো?
না। সেটা বলার জন্য এ লেখা লিখতে বসিনি। এ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র রাস্তা হল প্রিভেনশন, অসুখ হওয়ার আগে আটকানো। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সুরক্ষাবিধি, ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত। ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি আইন, ওয়ার্কমেন কম্পেনসেসন আইন এসব থাকলেও তাদের নাগাল খুবই সীমিত এমনকি সংগঠিত ক্ষেত্রেও। আর অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যায়।
এই রোগ নিয়ে গবেষণা, শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থাকরা এসব নিয়ে ভাববে কে? রাজনীতির নেতা, পেশাদার, মধ্যবিত্ত ইন্টেলেকচুয়ালদের করোনা হতে পারে, সিলিকোসিস নয়। বাবুরা এন নাইনটি ফাইভ দিয়ে করোনা রুখবেন।
তাই মইদুল বা মাধব মণ্ডলদের ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া গতি নেই। একটা মইদুল মারা গেলে কাল শাবল হাতে খাদানে আরেকটা মাধব মণ্ডল পাওয়া যাবে, পেটের দায়ে। একটা মাধব মণ্ডল মারা গেলে আরেকটা মইদুল পাওয়া যাবে যে মন্দির ভেঙে মসজিদ বা মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরি করবে, তার সাদা মার্বেলের সিঁড়িগুলো ঘষে ঘষে চকচকে করবে। সেই সিঁড়ি ভেঙে দেশের অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ উঠবে, নামবে আরাধ্য ঈশ্বরের উপাসনায়। কেবল ওই সিঁড়ির কোনে লাল ছিটে দাগ দেখলে ওটাকে পানের পিকের দাগ বলে ভুল করবেন না কেউ। ওটা মাধব মণ্ডল অথবা মইদুলের বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা কাশির সঙ্গে মেশানো রক্তের দাগও হতে পারে। দাগ আচ্ছে হ্যায়, অথবা আচ্ছে দিনের সুনাম গাওয়ার আগে অন্তত একবার মইদুলের বুড়ি মা অথবা মাধব মণ্ডলের কমবয়সি বিধবা বৌটার কথা মনে করবেন।