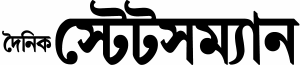শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই যে বসন্তোৎসবের প্রচলন, তা একেবারেই ঋতুর উৎসব৷ তার সঙ্গে নেই প্রথাগত হোলি বা দোলের কোনও ধর্মীয় অনুষঙ্গ৷ এই উৎসবে অসংযম বা উন্মাদনার কোনও স্থান নেই৷ ঋতুর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় ঘটনানোর উদ্দেশ্যেই এক-একটি ঋতুকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে এইসব শৈল্পিক উৎসব৷ শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবের ইতিহাস ও তার অনুধাবন সম্পর্কে লিখেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন যে বাংলা সংস্কৃতির বিশিষ্ট একটি নান্দনিক পরিসর রচনা করেছে সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই৷ আর শান্তিনিকেতনের নান্দনিকতার ইতিহাসে ‘বসন্তোৎসব’ অবশ্যই বিশিষ্টতর৷ শুধু ইতিহাস নয়, সেই উৎসবের আঁতের কথাই-বা বর্তমান কার্নিভাল-প্রিয় মানুষ কতটুকু জানতে চায়? কেউ অবিশ্যি বলতে পারেন, পৌষ-উৎসব ও মেলার ইতিহাস যতটা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, বসন্তোৎসবের তেমন কোথায়? দু-চারটে স্মৃতিকথায় যা দু-এক মুঠো তথ্য মেলে সেই সম্বল৷ এমনকি, বসন্তোৎসব ঠিক কবে থেকে শুরু হল তারও তেমন নথি নেই৷ সেই কোন ১৯০৭ সালে বালক শমীন্দ্রনাথ একটা ঋতু-উৎসব করেছিলেন, সেইটিকেই প্রথম বসন্তোৎসব ধরে নেন বেশিরভাগ মানুষ৷ আশ্রমের শাল-পিয়ালের গায়ে রঙের বাহার দেখা দিলেই আশ্রমিকদের মন কখন গুনগুনিয়ে উঠবে, কে আর তা পাঁজি-পুঁথি দেখে লিখে রাখতে যাচ্ছে? ব্যাপারখানা তো আসলে তা-ই৷ এ তো পিচকিরির রঙের গপ্পো নয়৷ প্রকৃতি সেজেছে আপন আনন্দে৷ আমরাই- বা তাহলে ঘরে বসে থাকি কী করে? ওই রঙের একটু আভা এসে আমার মর্মকেও রাঙিয়ে দিক৷ প্রকৃতির রঙের উৎসবে আমরাও যোগ দিই, রেঙে উঠি৷ এইটুকুই তো ব্যাপার৷ এখনকার সোনাঝুরি-বিলাসী আমোদসর্বস্ব বাঙালি বসন্তোৎসবের মর্মের খোঁজ কি আদৌ রাখে?
হ্যাঁ, এই কথাটা অবশ্য খুব ভুল নয় যে পৌষ-উৎসব বা মেলার মতো বসন্তোৎসবের ইতিহাস তেমন গেঁথে রাখা হয়নি৷ পৌষ-উৎসব ব্রাহ্ম-পার্বণ৷ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী’ সেই গোড়া থেকেই তার বিবরণনামা লিখে এসেছে৷ বসন্তোৎসব তো কার্যত বিশ্বভারতী পর্বের প্রকৃতি-বন্দনার উৎসব৷ চরিত্রের দিক থেকে তা একেবারে সেকুলার৷ হোলি বা দোলের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই৷ শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব হয়, বর্ষামঙ্গল হয়; তেমনই হয় ‘বসন্তোৎসব’৷ সারাদেশের দোল বা হোলি কীভাবে শান্তিনিকেতনে সর্বজনীন এই নান্দনিক উৎসবে উত্তীর্ণ হয়েছিল; কী ছিল তার নিহিত বার্তা— একটু তত্ত্বতালাশ করে দেখাই যাক না! একটু ইতিহাসের সরণি বেয়ে দেখে আসা যাক শান্তিনিকেতনের ‘বসন্তোৎসব’৷ বাঙালির নন্দিত নন্দনের এমন একটি পারিজাত মন্দারকে তো আর নিতান্ত অবহেলায় ঝরে যেতে দেওয়া যায় না! তো কী সেই ইতিকথা?
শান্তিনিকেতনের ‘বসন্তোৎসব’ নিয়ে এই এক মিথ অতিপ্রচলিত যে ১৯০৭ সালের ‘শ্রীপঞ্চমী’ তিথিতে বালক শমীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনে এর সূচনা করেছিলেন৷ কথাটা ঠিক ঠিক বললে বলতে হয়, বালক শমী ১৩১৩ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শান্তিনিকেতনে যদি সে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেও থাকেন তাহলে তা ছিল একটি ‘ঋতু-উৎসব’, ‘বসন্তোৎসব’ নয়৷ ‘রবীন্দ্রজীবনী’-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ১৭ ফেব্রুয়ারির সেই উৎসবে ‘শমীন্দ্র এবং আরো দুইজন ছাত্র বসন্ত সাজে, একজন সাজে বর্ষা; আর তিনজন হয় শরৎ৷’ ‘রবিজীবনী’-কার প্রশান্তকুমার পাল অবশ্য পাঁজি-পঁুথি ঘেঁটে জানিয়েছেন, সেবছর ‘শ্রীপঞ্চমী’ পড়েছিল ১৮ জানুয়ারি! প্রভাতকুমার সেই উৎসবের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না৷ শমীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ থেকে তিনি নাকি সেদিনের উৎসবের বিবরণ পেয়েছিলেন৷ তবে ‘শ্রীপঞ্চমী’ তিথিতে পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনে ‘বসন্তোৎসব’ উদ্যাপিত হয়েছে৷ যেমন হয়েছে ১৯২৩ সালের ২২ জানুয়ারি৷ আগেই বলেছি, প্রকৃতি সেজে উঠলেই আশ্রমিকদের মধ্যে তখন গুনগুনিয়ে উঠত ‘বসন্ত’৷ বসন্তকে আবাহন করার জন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষাও তখন তেমন আবশ্যক হয়ে ওঠেনি৷ যেমন, ১৯২৩ সালের মাঘীপূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে বসন্তের গানের আসর বসেছিল৷ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আশ্রম সম্মিলনীর অধিবেশনে আবার হয় বসন্তোৎসব৷
এখন প্রশ্ন হল, ১৯০৭ থেকে ১৯২৩ সময়পর্বের মাঝে কি তাহলে শান্তিনিকেতনে আর কোনোবার বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি? এর উত্তরে এইটুকু বলা যায়, পূর্ণমাত্রার অনুষ্ঠান হওয়ার তেমন কোনও নথি অন্তত আমাদের নজরে আসেনি৷ তবে সেই পর্বেও শান্তিনিকেতনে আবির খেলার চল ছিল৷ প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘পুরানো সেই দিনের কথা’ বইতে লিখেছেন, তিনি যে-বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে (১৯১৮-১৯) বাড়ি ফিরবেন সেই বছর বহিরাগত এক গোঁড়া ব্রাহ্ম আশ্রমে আবির খেলার এই হিঁদুয়ানিটা ভালোভাবে নিচ্ছিলেন না৷ তা নিয়ে একটি চমৎকার অ্যানেকডোট শুনিয়েছেন বিশীমশায়৷ আবির খেলা যথেষ্ট ব্রাহ্মশাস্ত্র অনুমোদিত কিনা— পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে এই প্রশ্নের সালিশি মেনেছিলেন সেই ব্রাহ্ম৷ উত্তরে সুরসিক ক্ষিতিমোহন বলেন, ব্রাহ্মধর্ম পুস্তিকাতেই যখন ‘আর্বি আবিরাবীর্ম্ম এধি’ মন্ত্র আছে তখন আর তাকে ‘ব্রাহ্ম-অশাস্ত্রীয়’ বলা যায় কী করে! অতঃপর সেই ভদ্রলোককে ট্রেনে তুলে বিদায় করে ‘উৎসবরাজ’ দিনু ঠাকুরের নেতৃত্বে অসিত হালদার, নগেন গাঙ্গুলি ‘আর আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণ খোল-করতাল সহযোগে আবির ছড়াতে ছড়াতে শাল-বীথিকার পথে আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন৷’ আর সেই সঙ্গে ‘যা ছিল কালো ধলো / তোমার রঙে রঙে রাঙা হলো৷’ —গানে সেবার ভরে উঠেছিল আশ্রম-অঙ্গন৷ দোলের দিন আবিরে-আম্রপল্লবে বসন্তের আমন্ত্রণলিপি আশ্রমিকদের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যেত সেই প্রাক্-বসন্তোৎসব পর্বের শান্তিনিকেতনে৷
সুতরাং, ১৯২০-র দশকে বিশ্বভারতী হওয়ার আগের পর্বেও দোলের দিন শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উদ্যাপন ছিল, কিন্ত্ত রীতিমতো আশ্রমিক-উৎসব সম্ভবত তখনও তা হয়ে ওঠেনি৷ তার জন্য অপেক্ষা ছিল ১৯২৩ সাল পর্যন্ত৷ তবে ১৯২৩-এর পরেও যে বসন্তোৎসবের অবিচ্ছেদ্য ও ধারাবাহিক নথি পাওয়া যায় তা নয়৷
‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’-র ৪র্থ বর্ষ মাঘ সংখ্যা সূত্রে জানা যায় ‘শ্রীপঞ্চমী’ উপলক্ষে আশ্রমে সেবার (১৯২৩) মহাসমারোহে ‘বসন্তোৎসব’ আয়োজন করা হয়েছিল৷ পত্রিকাটি লেখে, ‘এইদিন সন্ধ্যাবেলায় গুরুদেব ছাত্রীদের লইয়া কলাভবনে গান করিয়াছিলেন৷ ছাত্রীরা সকলেই বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ী পরিয়াছিল, মাথায় সকলের ফুল গোঁজা ছিল৷ পূজনীয় গুরুদেব রঙের পোষাক পরিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন৷’ এইখানে বলে রাখা ভালো, বিশ্বভারতী পর্বে ‘নারীভবন’ (১৯২০ নাগাদ); অর্থাৎ ছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে এই উৎসবের প্রবর্তনার একরকমের কালগত যোগসূত্র সহজেই চোখে পড়ে৷ নন্দিনী-বিনা নন্দন-উৎসবের কথা হয়তো তার আগে কারোর মনেই আসেনি সেভাবে!
১৯২৬ সালে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৪ চৈত্র ১৩৩২ তারিখে৷ অনুমান করা যায়, এই দিনটিতেই ছিল বসন্ত-পূর্ণিমা৷ সেবার ‘নটরাজ’-এর ‘আবাহন-গীতিকা’ (‘নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা’) নৃত্যছন্দে অভিনীত হয়েছিল৷ ১৯৩১-এর ৪ মার্চ লাইব্রেরির বারান্দায় (বর্তমান পাঠভবন অফিস) বসন্তোৎসব উপলক্ষে ‘নবীন’ নাটিকাটির অভিনয় হয়৷ সাবিত্রী গোবিন্দনের গানও ছিল সেবারের অন্যতম আকর্ষণ৷ রমা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘মরি হায় চলে যায় বসন্তের দিন’ গানটির সঙ্গে কীভাবে নাচতে হবে তার নির্দেশনা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ‘গুরুদেব’-এর কাছ থেকেই৷ ‘ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল’ গানটির সঙ্গে সেবার নেচেছিলেন অমিতা সেন৷ শান্তিদেব ঘোষও ১৯৩১ সালের ওই ‘দোলের উৎসব’-এর আলাদা উল্লেখ করেছেন একটি সাক্ষাৎকারে৷ ভ্রাতুষ্পুত্র শমীক ঘোষকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে শান্তিদেব বলেছেন, তখন ‘বসন্তোৎসব’ বলতে কিছু ছিল না৷ সবাই মিলে আবির খেলা, গান গাওয়া— এসবই করা হত৷
সন্ধ্যায় থাকত কোনও অনুষ্ঠান৷ দোলের শোভাযাত্রার সঙ্গে ১৯৩১-এ ‘নবীন’ নাটকের জন্য লেখা ‘ওরে গৃহবাসী’ গানটি অবশ্য তখনও যুক্ত হয়নি৷ খুব নির্দিষ্ট করেই তিনি বলেছেন, সকালের শোভাযাত্রার নাচটা ‘১৯৩৪ সালের আগে পর্যন্ত হতো না৷’ ১৯৩১-এ দোলের আনন্দ-আসরে শান্তিদেব আর কলাভবনের ছাত্র বনবিহারী ঘোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাউলের ভঙ্গিমায় নেচে উঠেছিলেন৷ সে নাচের সুখ্যাতি কবির কানেও পৌঁছেছিল৷ আমাদের বিবেচনায়, শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের নান্দনিক গোত্রান্তরের ক্ষেত্রে এই বছরের ওই স্বতঃস্ফূর্ত নাচের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে৷ একথা মনে হওয়ার কারণ নিহিত রয়েছে ওই সাক্ষাৎকারেই৷ শান্তিদেব বলেন: “আগের দোল-উৎসব যেটা হতো, সেটাকে গুরুদেব আর বেশি উৎসাহ দিলেন না কারণ ঐ সময় নানারকম নোংরামি হতো৷ নোংরামি মানে কী— কাদা দিয়ে দিল, ছেলেরা দুষ্টুমি করে কালি দিয়ে দিল— এরকম এলোমেলো ভাব৷ উনি [রবীন্দ্রনাথ] ভাবলেন, এটাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে দিতে হবে৷ উনি সকালে ‘বসন্তোৎসব’ ব’লে একটা বিধিবদ্ধ উৎসব করা ঠিক করলেন৷ তখন থেকে আরম্ভ হলো সকালবেলার অনুষ্ঠান— তাতে গান হবে, কিছু নাচ হবে— ছেলেমেয়েরা নাচবে, গুরুদেব আবৃত্তি করবেন৷ তখন থেকে ‘ওরে গৃহবাসী’ গানটার সঙ্গে নানারকম অর্ঘ্য নিয়ে মেয়েরা আসত৷”
এখানে সামান্য টিপ্পনী যোগ করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গূঢ় নান্দনিক প্রবর্তনা যে সেসময়ের শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা অচিরাৎ বুঝে গিয়েছিলেন তা মনে করবার কোনও হেতু নেই৷ কেননা, ১৯৩৮ সালের উৎসবের দিন বৈতালিকের গানের সময় ছাদের উপর উঠে কয়েকজনকে হৈ-হৈ করতে দেখে সেসময়ের নবাগত ছাত্র পঞ্চানন মণ্ডল ভারাক্রান্ত মনে ডায়েরিতে লিখেছিলেন, তাদের ‘অসংযত আমোদে মত্ততার আকার বহির্গত হইতেছে৷ লজ্জা দিতেছে আজ আশ্রমের এই মধুময় উৎসবকে৷’
শান্তিদেবের সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, সম্ভবত ১৯৩২ থেকেই ‘ওরে গৃহবাসী’ গাইতে গাইতে শোভাযাত্রার চল শুরু হয়েছিল৷ ১৯৩৪ সালে সেই গানের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল নাচ৷ শান্তিদেব বলছেন, সেসময় “গানের দল আগে আসত মেয়েরা পিছনে আসত, তারপর হলো যে অল্প জনা কুড়ি-পঁচিশ মেয়ে আগে আসত আর গানের দল পিছনে থাকত৷” বছর দুয়েক এরকম চলার পর ‘আমার মাথায় খেয়াল এল, মেয়েদের প্রসেশনটা নৃত্যের ভঙ্গিতে করলে কেমন হয়৷ ফোকড্যান্সে যেমন হয়৷ এই নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বললাম৷ গুরুদেব বললেন, “হ্যাঁ, ভালোই হবে৷…আমি ঠিক করলাম, বেশি কমপ্লিকেটেড নয়, মণিপুরী একটা সিম্পল স্টেপ, এগিয়ে যাওয়া…ঢঙে— এই স্টেপে নাচ করবে, এক হাতে অর্ঘ্য থাকবে, গানের দল চলবে সঙ্গে সঙ্গে৷… ব্যাস্, এই শুরু হয়ে গেল নতুন একটা দিক৷ ওরা নাচতে নাচতে এগিয়ে চলত, নন্দবাবু [নন্দলাল বসু] তালপাতা দিয়ে হাতের ডালি তৈরি ক’রে দিতেন তাতে ফুল, আবীর থাকত, কোনোটি আবার থালা, সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখা হতো, তারপর শুরু হয়ে যেত বসন্তোৎসব৷… দোল উৎসব উঠে গিয়ে এই [বসন্তোৎসব] চালু হয়ে গেল৷ এই প্রসেশনের নাচটা আমিই প্রথম ইন্ট্রোডিউস্ করলাম৷”
প্রসেশনের নাচটাকে পরে দু’জন-দু’জন করে সাজিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাটাও ছিল শান্তিদেবের৷ নাচের দলকে কাঠির নাচ, মন্দিরার নাচ, হাতের তালির নাচ— এইরকম ভাবে ভাগ করে দেওয়ার ফলে একাধারে যেমন উৎসবের বৈচিত্রসাধন হয়, তেমনি অন্যদিকে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে অংশ নেওয়ার সুযোগও করে দেওয়া যায়৷ বৈচিত্রসাধনের জন্যই তখন শোভাযাত্রার পরিক্রমা পথও বদলে যেত বছর বছর৷ আম্রকুঞ্জে গিয়ে শেষ হতো সেই শোভাযাত্রা৷
আম্রকুঞ্জে বেশ যত্ন করে নিকোনো একটা মণ্ডলী বা বেদিতে বসত গানের দল৷ আমগাছগুলোকেও ভালো করে সাজিয়ে দেওয়া হত৷ ‘বসন্তকালে গাছপালাও যে উৎসবের একটা অঙ্গ’— তা মনে রাখা হতো তখন৷ পঞ্চাশের দশকের বসন্তোৎসব প্রত্যক্ষ করেছেন এমন অনেক প্রবীণ আশ্রমিকের মুখে শুনেছি, একটা প্রকাণ্ড রেকাবি বা পরাতে চূড়া করে রাখা হত আবির৷ অনুষ্ঠান শেষে সেই আবির নিয়ে একে অপরকে মাখাতেন সবাই৷ আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত আম্রকুঞ্জেই অনুষ্ঠিত হতো শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব৷ ১৯৮১ সালে আম্রকুঞ্জের গাছে চড়ে বসা অতু্যৎসাহী দর্শকদের ভারে ভেঙে পড়ে আমের ডাল৷ তারপরই বসন্তোৎসবের আম্রকুঞ্জপালা শেষ হয়ে গৌরপ্রাঙ্গণ পর্ব শুরু হয়৷ এই বিশৃঙ্খলার কারণে ১৯৮২ সালের পয়লা মার্চ ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’-সহ বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা লেখে, আগের বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে সেবছর বসন্তোৎসব-উদ্যাপন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে৷ ১১ মার্চের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-সহ অন্যান্য সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায়, শেষপর্যন্ত অবশ্য ‘বসন্তোৎসব’ দোলের দিনই (৯ মার্চ) অনুষ্ঠিত হয়, কিন্ত্ত তার জৌলুস কিছুটা ফিকে ছিল সেবছর৷
শান্তিদেবের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ১৯৩১ বা তার আগে সকালের আনন্দ-আসরে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন না৷ ১৯৩২ থেকে শান্তিনিকেতনের দোল-উৎসব ‘বসন্তোৎসব’ হয়ে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথ সকালের অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়া শুরু করেছিলেন৷ তার চেয়েও বড়ো কথা, এইসময় থেকেই অনুষ্ঠানের প্রকরণগত দিক থেকেও এলো খুব বড়োরকম একটা পরিবর্তন৷ আমাদের চেনা বসন্তোৎসবের সূচনা এই সময় থেকেই৷
১৯৩৫ সালে বসন্তোৎসব পড়েছিল ২০ মার্চ তারিখে৷ এখনকার মতো তখনও ছিল এক-একটা রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে এক-একটা নাচ৷ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রজীবনী’-র চতুর্থ খণ্ডে সেবারের অনুষ্ঠানে নাচের দলের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে আছে ইন্দিরা নেহরুরও নাম৷ চৌদ্দটি গানের মধ্যে ‘কে দেবে চাঁদ, তোমায় দোলা’ এবং ‘তোমার বাস কোথা-যে পথিক’ গানদুটির সঙ্গে অন্যান্যদের সঙ্গে নেচেছিলেন ছাত্রী ইন্দিরা৷ আর সকালের মূল অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ‘ফাল্গুনী’ থেকে কিয়দংশ পাঠ করার পর এবছর ‘বসন্তোৎসবের মর্মকথা’ ব্যাখ্যা করেছিলেন৷
সেই সময়ের উৎসবের মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় সুজাতা মিত্রের একটি স্মৃতিচারণায়৷ তিনি লিখেছেন: “বসন্তোৎসবের জন্য উত্তরায়ণে ‘উদয়ন’ বাড়িতে গুরুদেবের নির্দেশনায় অনেক-দিন ধরে মহড়া চলত৷… মাস্টারমশাইরা সুন্দর করে আম্রকুঞ্জ সাজিয়ে দিতেন৷ মাঝখানের বেদীতে থাকত গুরুদেবের বসার আসন৷ তার পাশে ক্ষিতিমোহন সেন এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসতেন৷ কলাভবনের ছেলেরা অনেকদিন ধরে পরিশ্রম করে সারা আম্রকুঞ্জ আল্পনায় ভরিয়ে দিত৷… যে মেয়েরা নাচতে পারত, তারাই নাচে যোগ দিত৷ নাচের মেয়েদের সাজিয়ে দিতেন কলাভবনের মাস্টারমশাইরা৷ আমরা হলুদ কাপড় পরে হাতে নিতাম আবির ও ফুল৷ প্রসেশন করে পুরোনো লাইব্রেরির বারান্দার কাছে এসে নাচ শুরু করতাম, নাচতে নাচতে এগিয়ে যেতাম আম্রকুঞ্জের দিকে৷ ‘খোল্ দ্বার খোল্’ গানের সঙ্গে আম্রকুঞ্জের আল্পনাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে শেষ হত আমাদের নাচ৷”
১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ দোল পূর্ণিমার দিনেই বসন্তোৎসব হয়৷ সদ্যপ্রয়াত (২৮ ফেব্রুয়ারি) কমলা নেহরুর স্মরণে কবি সেদিন সকালে মন্দির-ভাষণে বলেন, ‘আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব৷— আমাদের আশ্রমের এই বসন্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিন রূপে গ্রহণ করছি৷’ বসন্তোৎসবের দিনটিকে প্রয়াতের স্মরণেরও দিন হিসেবে গ্রহণ করে যে বক্তৃতা করেছিলেন কবি, তার মধ্যেই নিহিত ছিল কবির চিরকালীন বসন্তভাবনার অন্তঃসার৷ রবীন্দ্রনাথের ‘বসন্ত’ উচ্ছ্বাস বা উন্মাদনার ঋতু নয়৷ তার খুব গভীরে থাকে একরকম সাবলাইম বিরহচেতনাও৷ সেই বিরহ ‘বিশ্বসাথে’, প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়ার আত্যন্তিক ব্যাকুলতা-সঞ্জাত! রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-ভাবনার একটি ভাব অপসারী ধরনের৷ তার মানে, বিশ্বজগতের দিকে যেন ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে মিলতে চাইছে মানুষ৷ বসন্তের অনেক গানের সুরে সেই ব্যাকুলতার প্রকাশ৷ আবার এও মনে রাখতে হয়, ‘নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে’ গানটি ‘গীতবিতান’-এ প্রকৃতি পর্যায়ের অন্তর্গত হলেও তার বাণী ও সুরের মধ্যে আছে গভীর একটি ধ্যানমূর্তি৷ গানটি একসময় ‘ব্রহ্মসংগীত’ হিসেবেই গীত হত৷ রবীন্দ্রনাথের ‘বসন্ত’ শুধু উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনার ঋতু নয়— তা কবে আর বুঝব আমরা? যাকগে সে মনখারাপের কাহন৷ আমরা ইতিহাস খুঁড়ে একটু যদি সেসময়ের দখিনা বাতাসের স্পর্শ পাই তো সেই ঢের!
পূর্বোক্ত পঞ্চানন মণ্ডলের ডায়েরি থেকে জানা যায় ১৯৩৭ সালে মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে বসন্তোৎসব হয়েছিল আশ্রমে৷ সেবার সন্ধ্যার অনুষ্ঠান হয় গৌরপ্রাঙ্গণে৷ সেবছর ২৬ মার্চ দোলপূর্ণিমার দিনও আবার হয় উৎসব৷ তখনও প্রভাতী বৈতালিকের গান ছিল ‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে৷’৷ পঞ্চানন মণ্ডল লিখছেন: “তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া… স্নান সমাপনান্তে বাসন্তী রঙের উত্তরীয় গায়ে জড়াইয়া উৎসব প্রাঙ্গণে গিয়া যোগ দিলাম৷ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভবন হইতে আশ্রমিকদের নৃত্য ও সঙ্গীত সহযোগে শোভাযাত্রা আসিল মঙ্গলঘট লইয়া আম্রকুঞ্জ পর্যন্ত৷ রবীন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন বটবৃক্ষমূলের ঘণ্টাতলায়৷ শেষে আসিলেন আম্রকুঞ্জে যেইখানে প্রজাপতি আঁকা প্রাঙ্গণে বেদী সজ্জিত উঁহার জন্য৷ উনি ‘বনবাণী’ ও ‘সঞ্চয়িতা’ হইতে কয়েকটি বাছাই কবিতা পাঠ করিলেন৷… কয়েকটি সময়োচিত সঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হইল৷ ছোট মেয়েরা আবীরে গুরুদেবের পা রাঙা করিয়া দিয়াছে৷ দোলপূর্ণিমার অবারিত হোলিখেলায় আজ আশ্রমের বাদ গেল না কেহই— এমনকি কুনো আমি পর্যন্ত৷ সন্ধ্যায় আলোকমালা সজ্জিত আম্রকুঞ্জে গুরুদেবের উপস্থিতিতে গুজরাটি গরবা ও অন্যান্য দেশের আরও কয়েকটি নৃত্য হইল৷ রবীন্দ্রনাথের বসন্ত সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটিল৷”
কাঠি সহযোগে ডান্ডিয়া কিংবা রাস-গরবা নাচের সঙ্গে মণিপুরী নাচের সামান্য ‘ফিউশন’ হয়তো ঘটেছিল শান্তিনিকেতনের শোভাযাত্রার নাচের, কিন্ত্ত পরিণামত তা হয়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র একটি ধারা৷
এখানে জানিয়ে রাখি, তিরিশের দশক থেকে বসন্তোৎসব উপলক্ষে কবিকে বিশেষ ভাষণ দিতেও দেখা গেছে৷ কবির প্রয়াণের পরও বসন্তোৎসবে ভাষণের এই ধারা অব্যাহত থাকে কিছুকাল৷ তখন উৎসবে আচার্যের ভূমিকা পালন করতেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন৷ প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে এও জানা যায়, ক্ষিতিমোহন এই নান্দনিক উৎসবের সঙ্গে উপযুক্ত মাঙ্গলিক মন্ত্রও যোগ করেছিলেন৷ প্রণতি মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘তাঁর [ক্ষিতিমোহন] প্রবন্ধগুলি মনে পড়ে, যেখানে তিনি দোল উৎসবের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করেছেন৷ কতবার উৎসবের দিনেও বলেছেন সেসব কথা৷… আম্রকুঞ্জের বেদিতে বসে ঋতুরাজ বসন্তকে অর্ঘ্য দিয়েছেন বৈদিক মন্ত্রে, রবীন্দ্র-রচনায়৷’ এইরকমই একবছর কোনও এক জাতীয় বা সামাজিক আপৎকালে বসন্তোৎসব করা সমীচীন কি না এই নিয়ে যখন আশ্রম দ্বিধাগ্রস্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে ক্ষিতিমোহনই বলেন, কবি নেহাত আমোদ-প্রমোদের জন্য বসন্তোৎসবের সূচনা করেননি শান্তিনিকেতনে৷ ‘এই উৎসব যা মিথ্যা ও কুৎসিত তার উপরে সত্য ও সুন্দরের জয়ের প্রতীক৷’
‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র ইউ.পি. প্রেরিত ১৯৪০ সালের উৎসবের প্রতিবেদনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য রয়েছে৷ সেবছর বসন্তোৎসব (২৭ মার্চ) প্রসঙ্গে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, এ বৎসর ‘শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন বিভাগ ও তাহাদের পৃথক পৃথক পল্লী কেন্দ্রে পৃথক পৃথক দিনে এই বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়৷’ এই
১৯৪০-এই কবি শেষবার সক্রিয়ভাবে বসন্তোৎসবে যোগ দেন৷ ১৯৪১-এ অসুস্থতার মধ্যেও যাতে নিখুঁতভাবে উৎসব সম্পন্ন হয় তার জন্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষকে কবি দায়িত্ব দেন৷ এই শেষ বসন্তোৎসব উপলক্ষেই কবি লেখেন ‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থের ৪ সংখ্যক কবিতাটি৷ ‘আর বার ফিরে এল উৎসবের দিন৷/—এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ৷’
উৎসবের দিন এখনও বারবার ফিরে ফিরে আসে৷ ট্রেনভর্তি গাড়িভর্তি হোটেলভর্তি দর্শকের চাপে তাড়া খাওয়া হরিণীর মতো একুশ শতকের প্রথম দশকে ‘বসন্তোৎসব’ আশ্রমমাঠে গিয়ে আশ্রয় খোঁজে৷ ব্যাধের মতো উদ্যত মানুষ যেন দৌড়চ্ছে তার পিছে পিছে৷ আর এসব দেখে মনে হয়, ‘বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ৷’ বাঙালি কি আদৌ বুঝতে পেরেছে কবির বসন্তোৎসবের মর্মকথা?
লেখক বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের অধ্যাপক