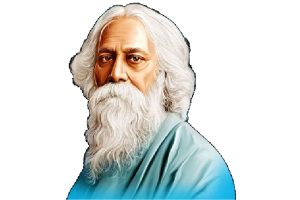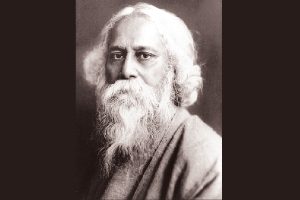স্বপনকুমার মণ্ডল
মাত্র ষোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ অভিনব বৈষ্ণব পদাবলী লেখায় ব্রতী হয়েছিলেন । তারও বছর দুয়েক আগে থেকেই তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের সোপানে তাঁর মধ্যে বহুমুখী বিস্তার যেমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, তেমনই স্বকীয় পথের সন্ধানে তাঁর অতীতকে অতিক্রমের প্রয়াসও জারি ছিল। সেখানে যেমন শ্রেষ্ঠত্ববোধে অনেকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে, তেমনই তাতে তাঁর উন্নাসিকতাও বেরিয়ে পড়ে কৃতীদের তুলনা বা প্রতিতুলনার অবকাশে। সেক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির বহুমুখী নিবিড় আয়োজনের পাশাপাশি তাঁর মননের বহুধাবিস্তৃত মূল্যায়ন একইভাবে স্বকীয় অস্তিত্বকে প্রকাশ করে চলেছিল। তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত মাসিক ‘ভারতী’ পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ১২৮৪-র শ্রাবণ/ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত লেখার মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান। তাতে কবিতার পাশাপাশি তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘ভারতী’র প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি বেরিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি প্রকাশের বছর তিনেক আগে (১৮৭৩) তাঁর প্রয়াণ ঘটে। স্বাভাবিক ভাবেই খ্যাতির প্রতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশের মধ্যেও কবির স্বকীয় প্রতিভার পরিচয়ও সংগুপ্ত থাকেনি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই বিরূপ সমালোচনার নেপথ্যে তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধার কথা বছরপাঁচেক পরে (১৮৮২) বললেও তার মধ্যে তাঁর তীব্র অস্মিতাবোধের উগ্রতাকে অস্বীকার করা যায় না। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিভাজাত ঈর্ষা নানাভাবেই উৎকর্ষবোধে উঠে এসেছে। সেখানে প্রশংসার ছলেও তাঁর স্বকীয় অস্তিত্ব নানাভাবেই মুখর। মহাকবি কালিদাসের কথা প্রসঙ্গেও তাঁর নিজের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। ‘ক্ষণিকা’র (১৯৯৩) ‘সেকাল’ কবিতার শেষ স্তবকের সূচনায় অকপটে কবি জানিয়েছেন : ‘আপাতত এই আনন্দে/ গর্বে বেড়াই নেচে—/ কালিদাস তো নামেই আছেন,/ আমি আছি বেঁচে। ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যেই তাঁর অস্মিতাবোধের পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে।
অন্যদিকে সেবছর (১২৮৪) ‘ভারতী’র আশ্বিন সংখ্যাতেই তাঁর ‘ভানুসিংহের কবিতা’ শুরু হয় ‘শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা’। দ্বিতীয় কবিতা বেরোয় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় । সেই কবিতাটি লেখার আনন্দ রবীন্দ্রনাথ আজীবন বহন করেছেন। এও যেন তাঁর ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’-এর মতো সৃষ্টির আনন্দ বয়ে এনেছিল। ‘জীবনস্মৃতি’-তে (১৯১২) সেকথা অকপটে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : ‘‘একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটি শ্লেট লইয়া লিখিলাম ‘গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে’। লিখিয়া ভারী খুশি হইলাম।’’ সেই খুশিতে সেবছর মোট সাতটির সঙ্গে পরে আরও ছয়টি এবং ‘ছবি ও গান’-এর অন্তর্ভুক্ত আর দুটি মিলে পনেরোটির সঙ্গে আর নতুন করে লেখা ছয়টি মিলে ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ ১২৯১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিতে নতুন মাত্রা লাভ করে। কাব্যটি পরে আরও সংযোজন-বিয়োজন করা হয়। অন্যদিকে তার আগে তাঁর বিশ বছরের মধ্যে যেসব কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে যে কবিপরিণতির পরিচয় সমুন্নত ছিল না, তা রবীন্দ্রনাথের পুনর্মুদ্রণের অনীহাবোধেই স্পষ্ট মনে হয়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বরমাল্য পাওয়া ‘সন্ধ্যাসংগীত’ কাব্যটিকেও বাদ দিতে চেয়েছিলেন কবি। সেক্ষেত্রে তাঁর ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ যে তাঁর কাব্যধারায় প্রথম উৎকৃষ্ট ফসল, সেকথাও স্বয়ং কবির অভিপ্রায়েই প্রতীয়মান। ১৯৪০-এও কাব্যটির নতুন সংস্করণের ভূমিকা লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপ্রত্যয়কে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-আবিষ্কারে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ বিশেষভাবে স্মরণীয়। চোদ্দো বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে একাত্ম হতে শুরু করেন। সেই সময় ‘সাধারণী’ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় সরকার, সারদাচরণ মিত্র ও বরদাকান্ত মিত্রের সম্পাদনায় ১২৭১-এর অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে ‘প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ’ নামে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখের পদাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলী টীকা-সহ প্রকাশিত হয়। সেখানে বিদ্যাপতির অচেনা-অজানা ভাষায় লেখা পদগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে তীব্র আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে পাওয়া বিদ্যাপতির পদগুলি তাঁর রীতিমতো গবেষণা ও সাধনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’তে ‘ভানুসিংহের কবিতা’য় সেকথা অকপটে জানিয়েছেন। সেই ‘প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে’ তাঁর কাছে ‘লোভের সামগ্রী’ হয়ে উঠেছিল।
গুরুজনদের পাঠের অভাববোধে সেগুলো অনায়াসেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জোগাড় করা সহজ হয়েছিল, কিন্তু আত্মস্থ করা সহজ ছিল না। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অসাধারণত্ব নিবিড়তা লাভ করে। তাঁর কথায় (প্রশান্তকুমার পালের ‘রবিজীবনী’র প্রথম খণ্ডে ‘জীবনস্মৃতি’র পাণ্ডুলিপির পাঠে): ‘বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ করিয়া দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।’ সেই সব প্রস্তুতির পটভূমিকায় খাতাটির কথা সুদীর্ঘকাল পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে ১৯৪০-এর ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’র ভূমিকায় পুনরায় স্মরণ করেছেন । শুধু তাই নয়, আরও জানিয়েছেন : ‘পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মনে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।’ সে মতেই রবীন্দ্রনাথের সততা ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠাই নয়, প্রতিভাদীপ্ত অস্মিতাবোধও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ‘ভানুসিংহের কবিতা’র কবিতার মধ্যে যে তাঁর কবিখ্যাতির সচেষ্ট প্রয়াস ছিল, সে কথাও তার অব্যবহিত অনুচ্ছেদের সূচনায় ‘পদাবলীতে জালিয়াতি’র কথা পুনরায় তুলে ধরাতেই প্রতীয়মান।
সাফল্যবোধের উৎকর্ষে ঋণস্বীকারের কথা প্রকাশমুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভানুসিংহ ঠাকুরের কবিতার উৎকর্ষবোধে তার রচনা প্রসঙ্গে অনেকের ঋণের কথা অকপটে বলেছেন। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিতে মনে হয় যেন তাঁদের সংযোগেই তাঁর এই বিরল কৃতিত্বের প্রকাশ সহজসাধ্য হয়েছিল। আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিনয়ের অভিনয় ছিল না। বরং সত্যপ্রকাশে তাঁর স্পষ্টবাক্মূর্তি আপনাতেই শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। সেখানে বৈষ্ণব পদাবলীতে তাঁর স্বকীয় ভূমিকার মধ্যে জালিয়াতির ছায়া কীভাবে বিস্তার হয়েছিল, তা নিয়ে তাঁর দ্বিধাহীন প্রকাশের মধ্যেই আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের কাব্যালোচনার সুহৃদ তথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে ইংল্যান্ডের বালককবি টমাস চ্যাটার্টনের (১৭৫২-৭০) প্রাচীন কবির মতো নকল কবির বিপুল খ্যাতির কথা শুনেছিলেন। সেই চ্যাটার্টনের কবিখ্যাতির মোহে পড়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁর পথ অনুসরণ করেছিলেন। ‘জীবনস্মৃতি’-তেও জানিয়েছেন : ‘চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।’ অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষোলো বছর বয়সেই বালককবির ‘জালিয়াতি’র শরিক হওয়ার কথা রসিকতা করে বলেছেন, তাও অচিরে তিনিই ফাঁস করে দেন। সেখানে তাঁর ‘জালিয়াতি’র মধ্যেই নকলের আভিজাত্য নেই, আসলের অসাধারণত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। মাঝখান থেকে বাংলার পণ্ডিতমহলের ফাঁক ও ফাঁকি নিয়ে তাঁর রসিকতায় চূড়ান্ত ব্যঙ্গবিদ্রুপও আন্তরিক হয়ে ওঠে । প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ বালককবি চ্যাটার্টনের পঞ্চদশ শতকের প্রাচীন কবি টমাস রাউলির (Thomas Rowley) কবিতার মতো নকল করে কবিখ্যাতি লাভে সচেষ্ট হননি। বালককবির মতো তাঁর কবিতার প্রতি পাঠকবিমুখতা বা কবিখ্যাতির অভাববোধ তাঁর ছিল না। সেদিক থেকে বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চা প্রকাশের আলো খুঁজে পায়, অচিরেই একাধিক সাময়িক পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যচর্চা বিস্তার লাভ করে। সেদিক থেকে চ্যাটার্টনের হীনমন্যতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুর কোনো প্রাচীন কবি নন। সেটি তাঁরই ছদ্মনাম। শুধু তাই নয়, তিনিই যে ভানুসিংহ সেকথাও রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বালককবির ছায়া নেই, তবে রসিকতা আছে।
আসলে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে তাঁর কবিসত্তার উৎকর্ষকে পরখ করতে চেয়েছিলেন। সেখানে বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলির মতো বাংলা ও মৈথিলীর কৃত্রিমতাজাত মিশ্রভাষার রহস্যময় প্রকৃতির প্রতি তীব্র অনুরাগে তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় নতুন করে কবিতা রচনার মধ্যে যেমন তার পাঠযোগ্যতায় প্রাচীনত্বের সৌরভ জরুরি, তেমনই তার সাফল্যে কবির কৃতিত্ব প্রতীয়মান। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমের বাস্তবায়নের ভিতেই দ্বিতীয়-র আবির্ভাব নির্ভর করায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভানুসিংহের প্রাচীনত্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অচিরেই সফলতা লাভ করেন। সত্য স্বীকারে ছলনার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ছলনার মাধ্যমে সত্যে পৌছানোর মধ্যে সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের পরিচয় বর্তমান। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভানুসিংহের প্রাচীনত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বীয় কবিত্বের পরিচয়কে পরখ করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর দুর্বলতা নয়, বরং অনেকবেশি সবলতার পরিচয়। প্রথমে ভানুসিংহের প্রাচীনত্বের আধারে তাঁর কবিতার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তারের আয়োজন চলে। লাইব্রেরিতে খুঁজে খুঁজে বহু পুরনো জীর্ণ পুঁথি থেকে প্রাচীন কবি ভানুসিংহের কবিতা ‘কাপি করিয়া’ আনার কথা বলে প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে আগ্রহী বন্ধুকে দেখিয়ে বিশ্বাস করানোর প্রয়াসী হয়েছিলেন কিশোর কবি। এতে সেই বন্ধুর ভানুসিংহকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের চেয়েও বড় কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কাছে ধরা দেন। তাতে অবশ্য প্রশংসা শংসায় এসে ঠেকে। বন্ধুটির ‘নিতান্ত মন্দ হয়নি’ নামমাত্র মূল্যায়ন স্বাভাবিক হয়ে আসে। অন্যদিকে ‘ভারতী’তে প্রকাশকালেই জার্মানীর প্রবাসী ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোয়াপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের গীতিকাব্যের তুলনা করে যে চটি বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে ভানুসিংহকে ‘প্রাচীন পদকর্তারূপে’ ‘প্রচুর সম্মান দিয়েছিলেন’ যা ‘কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে সহজে জোটে না’ বলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ‘জীবনস্মৃতি’তে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ‘এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।’
আসলে রবীন্দ্রনাথ যে ভানুসিংহের কবিতা লিখে ভানুসিংহের কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন, সেকথা শুধু প্রকাশের উৎকর্ষেই উচ্ছ্বাসিত হয়ে ফলাও করে বলেননি, তার মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের অভিনব আয়োজনের সার্থকতাও ছিল। যা বালককবি চ্যাটার্টন প্রাচীন কবির আড়ালে থেকেই কবিখ্যাতি নিঃস্ব করে ফেলেছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় কবিপ্রতিভায় প্রাচীন কবিকে আধুনিকতায় নবজন্ম দিয়েছেন। সেখানে তাঁর সচেতন সাধনা ও সৃষ্টির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী যিনি চ্যাটার্টনের কথা রবীন্দ্রনাথকে অল্পবিস্তর জানিয়েছিলেন, সেই বালককবিকে নিয়েও তাঁর গবেষণা অচিরেই ‘ভারতী’তে (আষাঢ় ১২৮৬) ‘চ্যাটার্টন— বালককবি’ নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে পণ্ডিতমহলের মূল্যায়নে ফাঁক ও ফাঁকি থেকে অনুমানের অসারতা নিয়ে ভানুসিংহের পরিচয় নিয়ে যাতে রহস্য আরও ঘনীভূত না হয়, এজন্য রবীন্দ্রনাথ ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ প্রকাশের সমকালেই ‘নবজীবন’ (শ্রাবণ ১২৯১) পত্রিকায় সব্যঙ্গে ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী’ লিখেছেন। এটি আবার তাঁর প্রথম ব্যঙ্গরচনাও। অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কথাতে ভর করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভানুসিংহের কবিতায় আত্মনিয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন, একথাও যথার্থ নয়। কৈশোরেই তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তীব্র অনুরাগ লক্ষণীয়। সেখানে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার প্রতি দুর্বার আকর্ষণের মূলে শুধু ভাষাগত দুর্বোধ্যতা রহস্যময়তাকেই দায়ী করলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ যদিও সেদিকেই আমাদের দৃষ্টিকে সক্রিয় করে তুলেছেন। অথচ তা হলে সেই চর্চা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারত না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’র ভূমিকার (১৯৪০) শেষে স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা।’ সেক্ষেত্রে কবিখ্যাতি পাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের প্রতি একাত্মতাবোধকে নিবিড় করে তুলেছেন।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’র প্রথম সংস্করণের (১৮৮৪) আখ্যাপত্রে কবি নিজেকেই ‘প্রকাশক’ হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেছেন। সবদিকেই ভানুসিংহের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সযত্নে লালিত উদ্যোগের মধ্যে তাঁর নিছক প্রাচীন কবির কবিখ্যাতির লক্ষ্য যে ছিল না, অচিরেই তার পরিচয় মেলে।
আসলে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিই তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ ও তীব্র আকর্ষণ তাঁর তন্বিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের মধ্যেই প্রতীয়মান। সেখানে বয়সোচিত জ্ঞানের অভাবে নয়, তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বকে সঙ্গী করেই রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের বিস্তার ঘটেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্রজীবনকথা’য় রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি মুগ্ধতার কথা বলেও তাতে তাঁর ‘কাব্যরস-উপভোগ’-এর বাইরে ‘বৈষ্ণবতত্ত্ব বোঝবার বয়স ও আগ্রহ তখনো হয়নি’ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই ক্রমশ সেই বৈষ্ণবতত্বে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন বলেই প্রভাতকুমারই তার অব্যবহিত পরের বাক্যেই বলেছেন, ‘তাঁর অসংখ্য কবিতায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও ভাষা এমনভাবে মিশে আছে যে, লোকে ভুল করে ভাবতেও পারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে বুঝি বৈষ্ণব ছিলেন।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভানুসিংহের ‘শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, ‘বার বার সখি, বারণ করনু,/ না যাও মথুরাধাম’ বা ‘মরণ রে/ তুঁহু মম শ্যামসমান’ প্রভৃতি পদে সেই ভাবের বিস্তার রবীন্দ্রনাথকেও বৈষ্ণব কবি মনে হয়। শুধু তাই নয়, পদগুলির মধ্যে সুরের ব্যঞ্জনায় গানের অস্তিত্বে অভিনব আবেদন বয়ে আনার প্রতি সুকুমার সেন সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’-এ (চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স) তিনি আরও জানিয়েছেন, ‘এই গানগুলির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে পরিচিত হইয়াছিলেন।’ অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলী গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তো রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করতে পেরেছিলেন। ‘জীবনস্মৃতি’-তেও তাঁর সত্যান্বেষণী মনের কথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন তিনি, ‘গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।’ সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে বিদ্যাপতি বা তাঁর ব্রজবুলি ভাষার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য পদকর্তাদের পদেও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ভানুসিংহের ভাষায় বিদ্যাপতি বা ব্রজবুলি প্রকট হয়ে উঠলেও ভাবে চণ্ডীদাসের প্রভাবও সেখানে বর্তমান। ‘মরণ রে / তুঁহু মম শ্যামসমান’ রাধাবিরহের জনপ্রিয় পদটিতে চণ্ডীদাসের ছায়া সুস্পষ্ট।
অন্যদিকে শুধু ভানুসিংহের কবিতাতেই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যেও তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা বেরিয়ে এসেছে। ‘আলোচনা’র (১৮৮৫) ‘বৈষ্ণব কবির গান’, ‘সমালোচনা’র (১৮৮৮) ‘চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’, ‘বসন্তরায়’ প্রভৃতি প্রবন্ধে তার পরিচয় বর্তমান। ‘বৈষ্ণব কবিতার গান’-এ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের আধারে স্বর্গের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন। সেখানে জ্ঞানদাসের গানের উদ্ধৃতিতে তা মূর্ত করে তুলেছেন । আবার ‘ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিত্বের পার্থক্যই শুধু স্পষ্ট করে তোলেননি, দ্বিতীয়জনের চেয়েও প্রথমজনের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে বিশদে আলোচনা করেছেন। ‘বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি’র মূল্যায়ন বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় পথনির্দেশ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ‘বসন্তরায়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে বসন্তরায়ের ব্রজবুলি ভাষা ও তাঁর কবিত্বের সুখ্যাতি করেছেন। প্রবন্ধের বইদুটিকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে অগ্রাহ্য করলেও বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় সেগুলি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মননে বৈষ্ণব পদাবলী সুদীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল। সময়ান্তরে তিনি তাতে মনোযোগীও হয়েছেন। ‘আধুনিক সাহিত্য’(১৯০৭)-এর ‘বিদ্যাপতির রাধিকা’র মধ্যে তার পরিচয় মেলে। সেটি ‘সাধনা’ পত্রিকায় ১২৯৮-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যেও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধার তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান। শুধু তাই নয়, সেখানে বিদ্যাপতির রাধার চিরনবীন প্রেমের ভূমিকার পরে চণ্ডীদাসের চিরপুরাতন প্রেমের কথা আন্তরিক ভাবে ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতির অপূর্ণতার আধারেই চণ্ডীদাসের প্রেমের অপার মহিমা বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের অসীম ব্যঞ্জনায় বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ভানুসিংহের পদাবলী বা প্রবন্ধাদিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই ক্ষান্ত হননি, কবিতাতেও সক্রিয় হয়েছেন। বৈষ্ণবতত্বকথাকে তাঁর মতো এমন সহজ করে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেননি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনসাধনের কথা কত ভাবেই না ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে প্রেমের বিস্তারে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন সহজেই অবৈষ্ণবদের মনেও সৌরভ ছড়িয়ে দেয় ।
‘সোনার তরী’ (১৮৯৪) কাব্যের ‘বৈষ্ণবকবিতা’য় সেই প্রেমের কথাই প্রথমে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান’ বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কবি। সেখানে রাধার প্রেমের একাত্মতায় কবিদের বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন প্রেমের কথাই স্মরণ করেছেন। কবির ভাষায় : ‘সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/ কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/ কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান/ বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,/ রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?’ সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই দেবতা ও প্রিয় একাকার হয়ে ওঠে । কবির ভাষায় : ‘দেবতারে যাহা দিতে পারি, দেই তাই/ প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/ তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!/ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।’ রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর কবিত্বের প্রতি তীব্র অনুরাগী হয়েই শুধু ভানুসিংহ হয়ে ওঠেননি, তার সঙ্গে বৈষ্ণবতত্বের যোগও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ছিল। গাছের উপরের ফুলফলের দৃষ্টি থেকে মাটির মূলের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আপনাতেই প্রসারিত হয়েছিল। এজন্য অবৈষ্ণব হয়েও তিনি যেভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের মধ্যে আত্মগোপন থেকে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমশ তাঁর আত্মস্থ প্রকৃতিকে সাহিত্যের নানা শাখাপ্রাশাখায় সবুজ করে তুলেছেন, তা তাঁর দিগন্তবিস্তারী সৃষ্টিশীলতারই পরিচয়বাহী। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলীকে আধুনিক পরিসরে তিনি শুধু পুনর্জন্মই দেননি, তার বনেদিয়ানাকেও নতুন করে প্রাণিত করেছেন। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে, যা নীরবে নিভৃতে আমাদের পথ দেখিয়ে চলে অবিরত, বিস্ময় জাগিয়ে রাখে নিরন্তর।