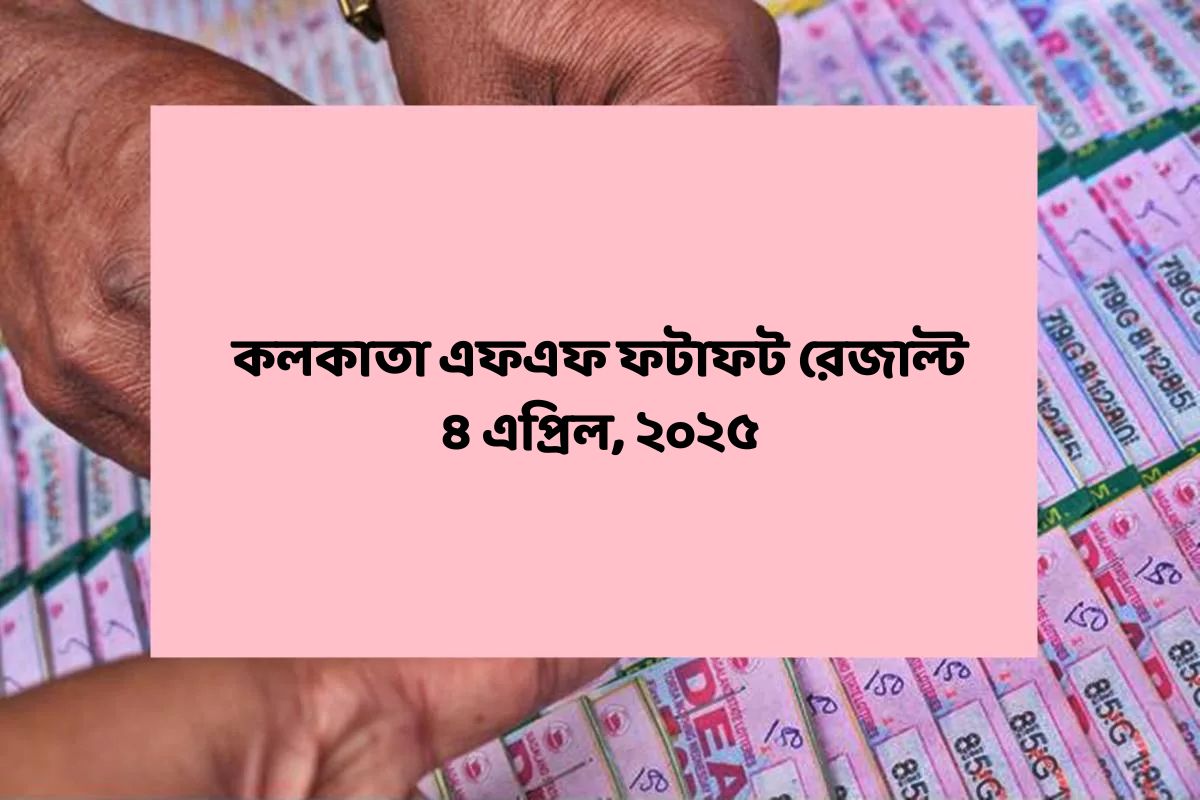আধুনিক সময়কালের ভারতীয় হিসেবে অনুসরণযোগ্য মানুষ ও আইডিয়ার সন্ধানে আমরা সাধারণত দেশের তথাকথিত মূল ভূখণ্ডের বাইরে, বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতে, যাবার কথা ভাবি না। অথচ ইতিহাস খনন করে দেখলে ওই অঞ্চলে একাধিক স্মরণীয় কীর্তির মানুষের দেখা মিলবে। অসমের প্রত্যন্ত গ্রামে গত শতাব্দীর একেবারে শুরুতে এমন একজন নারী জন্মেছিলেন, যাঁর জীবন ও কর্ম তাঁকে অবিসংবাদিত নেত্রীতে পরিণত করেছিল। আরও অনেকের মতোই তাঁর নাম হয়তো তেমন পরিচিত নয় সাধারণ বঙ্গভাষী মানুষের মধ্যে, তবে তাতে তাঁর গুরুত্ব কোনওমতে ক্ষুণ্ণ হয় না। নাম তাঁর চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী।
চন্দ্রপ্রভা সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর তথ্যের একটি হল, তাঁর জন্ম (১৯০১) ও মৃত্যু (১৯৭২) উভয়ই ঘটেছিল একই তারিখে— ১৬ মার্চ। তবে এটিকে নেহাতই একটি আপতিক ঘটনা বলে ধরে নিলেও, অবশিষ্ট বিস্ময়গুলি সৃষ্টির পেছনে এই সাহসী নারীর অনেক লড়াই, কষ্টস্বীকার ও ত্যাগের কাহিনি রয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে স্বাধীনতা-সংগ্রামী, নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী, সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যসেবী। একশো বছর আগে একটি পশ্চাদপদ অঞ্চল থেকে উঠে এসে তিনি যে-সমস্ত সংস্কারের সূচনা করে গিয়েছিলেন, স্পষ্টতই তার সবগুলি এখনও সম্পূর্ণ করা যায়নি। তাঁর কাজ ও কাহিনি, অতএব, আজও সমান প্রাসঙ্গিক।
জন্মেছিলেন অসমের কামরূপ জেলার অখ্যাত গ্রাম দৈশিঙ্গরিতে, পিতা গ্রামের মোড়ল রাতিরাম মজুমদার। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল চন্দ্রপ্রিয়া। যে-কালে আসামে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল প্রায় নগন্য, সে-সময়ে রাতিরাম ও তাঁর স্ত্রী গঙ্গাপ্রিয়া পুত্রদের পাশাপাশি কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। গ্রামে কোনও বিদ্যালয় না থাকায় দুই বোন— চন্দ্রপ্রভা ও রামেশ্বরী— তিহুর কাছে মাসির বাড়ি ভালুকি গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার পড়া শেষ করে ফিরে এলে রাতিরাম কন্যাদের নিকটবর্তী কাঁঠালগুড়ি গ্রামস্থিত বালকদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন, কারণ গোটা অঞ্চলে কোথাও মেয়েদের জন্য কোনও মিডল স্কুল ছিল না।
প্রথমত মেয়ে হয়ে জন্মে পড়াশুনা করা, দ্বিতীয়ত ছেলেদের বিদ্যালয়ে পড়তে যাবার জন্য নিয়মিত উপহাস ও সমালোচনা শুনতে হত দুই ভগিনীকে। তার ওপর অত্যন্ত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে কাদা-মাটি-জল-জোঁকের ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে এতদূর যাবার শারীরিক গ্লানি ছিল। এই সব মিলিয়ে একসময় পড়াশোনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন দুজনে। কারও কারও মতে এইসময় চন্দ্রপ্রিয়াকে উলুয়া গ্রামের এক বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ওই ব্যক্তির সঙ্গে সংসার করতে অস্বীকার করে পিতার গৃহে ফিরে আসেন তিনি। আবার কারও মতে তিনি এই বিবাহ করতে কোনওমতে রাজি হননি। এটা ছিল চন্দ্রর প্রথম প্রতিবাদী পদক্ষেপ, যা তাঁর পিতাও মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্বে দেখা গিয়েছিল যে, চূড়ান্ত কঠিন সময়েও, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পিতা চন্দ্রর হাত ছাড়েননি। এই সমর্থনটুকু মানুষের জীবনে অত্যন্ত জরুরি, যার অভাবে অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে থাকে। পরে যখন প্রয়োজনের তাগিদে সাইকেলে চড়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছেন চন্দ্র, তখনও তাঁর সমালোচনা কম হয়নি নারী হয়ে সাইকেল চালানোর জন্য। তবে তাতে চন্দ্রপ্রভার মতো বিদ্রোহী আত্মাকে দমন করা যায়নি।
মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব ওই বয়সেই সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন চন্দ্র, নিকটবর্তী গ্রাম অকয়াতে তিনি তাই ছোটো বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় খুলে বসেন, নিজেই সেখানে বিনা-বেতনের শিক্ষক হন। সেটা ১৯১৩ সাল, শিক্ষিকার বয়স মাত্র বারো-তেরো। ক্রমে বিদ্যালয়টি বরপেটা লোক্যাল বোর্ডের অধীনে চলে আসে এবং শিক্ষিকার জন্য ছয় টাকা বেতন ধার্য হয়। চন্দ্রর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর, নিজস্ব উপার্জনের প্রথম পর্ব ছিল এই ঘটনা। এই শিক্ষকতা চলাকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শক নীলমণি বরুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর আনুকূল্য লাভ চন্দ্রর জীবনের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়। তাঁরই পরামর্শে ও সুপারিশের জোরে চন্দ্রপ্রিয়া ও রামেশ্বরী নগাঁও মিশন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হন ১৯১৫ সালে; প্রয়োজনীয় স্কলারশিপের ব্যবস্থাও তিনি করে দেন। এই বিদ্যালয়টি আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হত, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যারা যুগপৎ শিক্ষাদান ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ করে চলছিল। সেখানে দুই ভগিনীর নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় চন্দ্রপ্রভা ও রজনীপ্রভা দাস, আরও পরে চন্দ্রর পদবী হয়ে দাঁড়াবে শইকীয়ানী। এই রজনীপ্রভাই পরে আধুনিক অর্থে অসমের প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবে পরিচিত হবেন, এবং চন্দ্রপ্রভার পরিচিতি আরও ব্যাপক আকার নেবে ক্রমে। তবে রজনীপ্রভার বিবাহ-পরবর্তী জীবন জটিল হয়ে পড়ে, তিনি দীর্ঘদিন বাঁচেননি।
দুই বছর নগাঁওয়ের স্কুলে পড়তে হয়েছিল তাঁদের, সেখানেই জনসমক্ষে চন্দ্রপ্রভার প্রতিবাদী সত্তার স্ফূরণ দেখতে পাওয়া যায় প্রথম বারের মতো। কতই বা বয়স তাঁর তখন, মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছর! খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে হিন্দু ছাত্রীদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল চন্দ্রপ্রভার গলায়। ওখানে বাইবেল ক্লাসের জন্য সদ্য নির্মিত একটি ঘরে সাধারণত হিন্দু মেয়েদের থাকতে দেওয়া হত। ওই ঘরটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে যাবার পর নতুন একটি হিন্দু মেয়ে যখন এল, তাকে বলা হল গুদামঘরে গিয়ে থাকতে। ঘরটি ছিল ছোটো, অন্ধকার এবং অপরিচ্ছন্ন; একেবারেই বাসের যোগ্য ছিল না। মেয়েটির হয়ে এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানান চন্দ্রপ্রভা। তার উত্তরে মিস লং নাম্নী শিক্ষিকা বলেছিলেন, ‘তোমরা ভারতীয়রা তো এর থেকেও ছোটো এবং আরও বিচ্ছিরি কুটির আর কুঁড়েঘরে থাকো!’
বিদেশি মিশনারি কর্তৃক এই অপমান এবং ভেদভাব চন্দ্রপ্রভা মেনে নেননি। তিনি গর্জে উঠেছিলেন, ‘আমরা কেউ এমন জঘন্য ঘরে বাস করি না, আর আমাদের কেউই ওই ঘরে থাকবে না।’ চন্দ্রর নেতৃত্বে সমস্ত মেয়ে ওই ঘরটিতে থাকতে অস্বীকার করল। শেষে জয় হল ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের। স্কুলজীবনের এই সাফল্য লড়াকু নেত্রী হিসাবে চন্দ্রপ্রভার ভবিষ্যৎ পথরেখার সূচনাবিন্দু ছিল বলা যেতে পারে। তিনি পরে লিখেছেন— মিশন স্কুলে পড়তে আসা খ্রিস্টান মেয়েদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি বিনামূল্যে দেওয়া হত বিদ্যালয় থেকে; কিন্তু হিন্দু মেয়েদের কাছ থেকে সে-সবের জন্য অর্থ নেওয়া হত। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেও চন্দ্রপ্রভাকে প্রতিবাদ করতে হয়েছিল।
ঔপনিবেশিক অসমে সামাজিক ও ধর্মীয় অপর, এবং নারী ও নিম্নতর জাতির মানুষের প্রতি বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য এবং বঞ্চনার ঘটনা ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এইসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠনে তাঁকেই এগিয়ে আসতে হয়েছিল। অনেকেই হয়তো বৈষম্যের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সোচ্চার হবার সাহস সবার থাকে না। চন্দ্রপ্রভার সেই মনোবল ছিল, যা তাঁকে অগ্রপথিকের স্থান দেয়।
চন্দ্রর প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৭ সালে নগাঁও মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর নর্মাল স্কুল ট্রেনিং শেষ করার পর তাঁকে তেজপুর মিডল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করা হয়, সেটা ১৯১৮। তেজপুরে থাকাকালীন তাঁর নারীবাদী ও দেশপ্রেমিক চেতনা পরিপক্ব হতে থাকে, একই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল এটি। তেজপুরে থাকাকালীন অমিয়কুমার দাস, চন্দ্রনাথ শর্মা, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে চন্দ্রপ্রভার বিকাশ হতে থাকে। জ্যোতিপ্রসাদের অনুরোধে তিনি অসম ছাত্র সম্মিলনের মেয়েদের শারীরিক কসরৎ শেখাতে থাকেন। অমিয়কুমার দাসের কথায় তিনি ওই সম্মিলনের চতুর্থ বাৎসরিক সভায় আফিমের মতো ক্ষতিকর নেশা নিষিদ্ধ করার দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দেন। এইরকম প্রকাশ্য জনসভায় একটি সতেরো বছরের মেয়ের ওই তীব্র বক্তৃতাটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকল ঔপনিবেশিক অসমের ইতিহাসে, এর আগে কোনও মহিলা জনসমক্ষে বক্তব্য রাখেননি। ওই সম্মিলনের সভাপতি হিসেবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেয়েদের শিক্ষালাভের বিষয়ে যে-বক্তব্য রেখেছিলেন, সেটি চন্দ্রকে বেশ প্রভাবিত করেছিল।
১৯১৯ সালে অসম সাহিত্য সভার অধিবেশনে আরেকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন চন্দ্রপ্রভা। তাতে তিনি দেশসেবা ও দেশের কল্যাণের জন্য ত্যাগস্বীকার করার জন্য জনতাকে আহ্বান জানান। ওই একই বছর তিনি কিরণময়ী আগরওয়ালার সঙ্গে মিলে তেজপুর মহিলা সমিতি গঠন করেন। সেই সমিতি অসমে প্রথমবারের মতো মহিলাদের পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করে। এমন নয় যে অসমে চন্দ্রপ্রভারাই প্রথম মহিলা সমিতি ধারণার উদ্ভব ঘটান। এর আগেই ১৯১৫ সালে হেমপ্রভা দাসের নেতৃত্বে ডিব্রুগড়ে মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু সেখানে শহরস্থ উঁচু শ্রেণির ভদ্রমহিলারা শিক্ষাসংস্কৃতি ও গান-বাজনা ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। সেটিকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া ও সামাজিক সংস্কারের কাজে ব্যবহার করার তেমন কোনও প্রচেষ্টা ছিল না।
এরপর চন্দ্রপ্রভার জীবনে দুটি মোড়-ঘোরানো ঘটনা ঘটল। একটি ছিল ১৯২১ সালে মোহনদাস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা। গান্ধী প্রথমবারের মতো অসমে এসে তেজপুর ভ্রমণ করেন এবং পোকিতে আগরওয়ালদের আবাসে আতিথ্য নেন। সেখানেই উদীয়মান ও সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর সঙ্গে গান্ধীর একান্ত আলাপচারিতা হয়। গান্ধী তাঁকে নারীদের সংগঠিত করা ও তাঁদের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার পথনির্দেশ করেন। চন্দ্রপ্রভার অনুরোধে গান্ধী পরের দিন শহরের বেঙ্গলি থিয়েটারে তেজপুর মহিলা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন, বিদেশি পণ্য বর্জনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এইভাবে ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠেন চন্দ্রপ্রভা।
এই অধ্যায়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ জটিল ঘটনা ছিল চন্দ্রপ্রভার প্রেমজীবন। ১৯২১ সালেই তরুণ অসমিয়া লেখক দণ্ডীনাথ কলিতার সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার প্রেম ও পরিণয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু পরে সামাজিক চাপের মুখে দণ্ডীনাথ নিচু জাতের এক নারীকে বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান দিতে অসম্মতি জানান। ইতিমধ্যে চন্দ্রর গর্ভে দণ্ডীনাথের সন্তান এসেছে, সেটিকে নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না তিনি। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে যান। এই কঠিন সময়ে চন্দ্রর পিতামাতা তাঁকে কাছে টেনে নেন, ১৯২২-এ পিতৃগৃহে নির্বিঘ্নে পুত্রসন্তান অতুলের জন্ম হয়। একক মা হিসেবে চন্দ্রর ব্যক্তিগত সংগ্রাম শুরু হয়। ক্রমে সেই অতুল শুধু একজন মানুষ হয়েই ওঠেননি, একাধিক জায়গায় শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন ও তাঁদের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। পরে, ১৯৭২ সালে স্বাধীন ভারতের অসম রাজ্যের একজন বিধায়ক হিসেবেও নির্বাচিত হন অতুল।
ফিরে আসি চন্দ্রর জীবনকথায়। ১৯২৫ সালে নগাঁও শহরে অসম সাহিত্য সভার অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলই। তখনকার প্রথা অনুযায়ী সভায় মেয়েদের বসার স্থান ছিল একটি বাঁশ-নির্মিত ঘেরার আড়ালে। সভায় নিজের বক্তব্য বলতে উঠে চন্দ্রপ্রভা এই বৈষম্যমূলক পর্দাপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর আহ্বানে মেয়েরা পর্দা ভেঙে সামনে বেরিয়ে আসেন, সকলের সমক্ষে তারা আসন গ্রহণ করেন। পিতৃতন্ত্রের অজস্র বিধিনিষেধের মধ্যে আরও একটির বিরুদ্ধে চন্দ্রপ্রভার প্রতীকী জয় হল, যদিও আরও অনেক কাজ তখনও বাকি।
চন্দ্রপ্রভা শহরের সমস্ত মহিলাকে এবং সাহিত্য সভার প্রতিনিধিদের ডাক দেন পরের দিন ওখানে সমবেত হবার জন্য, উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যভিত্তিক একটি মহিলা সংগঠন তৈরি করা। এক হাজার নারী সেদিন জমায়েত হয়েছিলেন সেখানে, কিন্তু কিছু গোঁড়া পুরুষের প্রবল বিরোধিতায় সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও মহিলারা বেরিয়ে এসে একটি খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে সংগঠন তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। পরের বছর সাহিত্য সভার ধুবুরি অধিবেশনে অসম মহিলা সমিতি গঠিত হয়, চন্দ্রপ্রভা নিজে হন তার সচিব। পরে সমিতির নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল অসম প্রাদেশিক মহিলা সমিতি।
তাঁর সক্রিয়তায় সমিতি নারীদের পক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। তার মধ্যে ছিল নারীদের শিক্ষার অধিকার, বিধবার পুনর্বিবাহ, শৈশব-বিবাহ রদ, পর্দাপ্রথার বিলোপ এবং অস্পৃশ্যতার উন্মূলন। ভারতের অন্য অনেক জায়গার মতোই অসমে নিম্নতর বর্ণের মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বঞ্চনা একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে ছিল। উচ্চবর্ণের নিষেধ থাকাতে ধর্মমন্দিরেও তারা প্রবেশ ও পূজাপাঠ করতে পারত না। মূলত চন্দ্রপ্রভার প্রবল চেষ্টার ফলে গুয়াহাটির কাছে হাজোতে অবস্থিত হয়গ্রীব মাধব মন্দির সমস্ত বর্ণের মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়। নিজের রচিত কবিতায় তিনি লিখেছিলেন:
খোলো হে খোলো মন্দিরদ্বার
এ-মন্দির ঈশ্বরের,
ঈশ্বরে পূজা করে যে-মানুষ
এ-মন্দির সে-মানুষের।
(কাব্যগ্রন্থ ‘মোর কবিতা’)
আগেই বলা হয়েছে— নারীবাদী কার্যক্রম ছাড়াও, গান্ধীর প্রেরণায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে চন্দ্রপ্রভা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাকালীন তিনি প্রথমবার গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী, জাতীয়তাবাদী ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার চাকরি করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯২৮ সালে গুয়াহাটির পাণ্ডুতে জাতীয় কংগ্রেসের ৪১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুনরায় গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার সাক্ষাৎ ঘটে। নেত্রী হিসাবে ক্রমশ তাঁর পরিচিতি ও উচ্চতা বেড়ে উঠেছিল। গুয়াহাটির কার্জন হলে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আয়োজিত ২৮ অক্টোবরের সভায় অসম প্রাদেশিক মহিলা সমিতির হয়ে তিনিই ভাগ নেন ও বক্তব্য রাখেন। এরপর ১৯৩১ সালের মার্চে করাচিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনেও তাঁকে ওই সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়।
স্বাধীনতাকামী, বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান কখনোই শান্তি ও স্বস্তির জীবন দেয় না। সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী হলে অনেক শারীরিক-মানসিক কষ্ট সইতে হয়। পরাধীন ভারতে, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে, চন্দ্রপ্রভাকে তিনবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং সাতবার ১৪৪ ধারা জারি করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। স্বাধীন ভারতে ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি বজালী নির্বাচনক্ষেত্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। অসাধু জোতদার, কন্ট্রাক্টর, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তিনি আগে থেকেই সোচ্চার ছিলেন। তাছাড়াও তাঁর সৎ, অকপট উচ্চারণ; এমনকী তাঁর একক মাতৃত্ব ও তজ্জনিত অবস্থান তাঁকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল বলে ধরা হয়। নিজে হেরে গেলেও রাজনৈতিক বলয়ে বেশি করে নারীদের অংশগ্রহণের পক্ষে তিনি ক্রমাগত সওয়াল করে গেছেন। তাঁর জোরালো দাবি ও নেহরুকে প্রেরিত চিঠিপত্রের কারণেই ১৯৫১ সালে অসম থেকে পুষ্পলতা দাসকে রাজ্যসভার সদস্য করে নেওয়া হয়।
চন্দ্রপ্রভা জানতেন শুধু সভা-সমিতি-আন্দোলন করলেই হবে না, নারীবাদী চেতনার প্রসার ও নারীদের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য কলমও ধরতে হবে। বাস্তবিক অর্থেই লিখিত শব্দের ক্ষমতা ও আয়ু অনেক বেশি, অনেক সময়ই তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করেও মানুষকে ভাবায়। যে-সময়ে আসামে সাক্ষর ও শিক্ষিত নারীর সংখ্যা একেবারেই কম, তখন লেখালিখি বলতে মেয়েরা মূলত কবিতাই লিখত। চন্দ্রপ্রভা সাংগঠনিক রিপোর্ট ও কবিতার ধাপ পেরিয়ে দৃপ্ত পায়ে ঢুকে গেলেন প্রবন্ধ, ছোটগল্প, আখ্যান, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনির জগতে। একইসঙ্গে ‘অভিযান’ ও ‘অভিযাত্রী’ নামে দুটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন তিনি, এককভাবে বা অন্যদের সঙ্গে মিলে। তাঁর প্রথম ছোটগল্প ‘দেবী’ প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে ‘বহ্নি’ নামক পত্রিকায়, লেখিকা হিসেবে নাম ছিল কুমারী চন্দ্রপ্রভা দাস। এই ‘দাস’ পদবী ব্যবহারের জন্য তাঁকে গল্পটির লেখিকা বলে বহুদিন চিহ্নিত করা যায়নি। গল্পটিতে একটি বালিকা বিধবার জীবনযন্ত্রণা ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার লড়াই চিত্রিত হয়েছে।
আরও পরিণত বয়সে লেখা ‘দৈবজ্ঞর দুহিতা’ (১৯৪৭) আখ্যানে চন্দ্রপ্রভা পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তো তুলেছেনই, পাশাপাশি এ-ও দেখাচ্ছেন কীভাবে মেয়েরাই পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসাবে ভূমিকা নিয়ে থাকে। নারীর ব্যক্তিগত মুক্তির লড়াই এখানে শেষমেশ দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই দুটি লেখাতেই নারীর ইচ্ছা ও কামনার অধিকারকে বৈধতা দিয়েছেন লেখিকা।
চন্দ্রপ্রভা-সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া; এর আগেকার পুরুষ লেখকদের লেখায় চিত্রিত নরম, ভঙ্গুর, রোম্যান্টিক নারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে-কারণে পুরুষ-রুচি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাহিত্য ও প্রকাশনার জগতে তাঁর তেমন কদর হয়নি। তাঁর ‘পিতৃভিটা’ (১৯৩৭) উপন্যাসে চন্দ্র নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর নায়িকা নিজের যুক্তিসঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যে-সমস্ত কুপ্রথা মূলত ব্রাহ্মণবাদ ও পিতৃতন্ত্রের দ্বারা তৈরি। তিনি ‘শেষ আশ্রয়’ ও ‘অপরাজিতা’ নামে আরও দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যেগুলি প্রকাশের মুখ দেখেনি। তার মধ্যে একটির পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না। এ-সব ছাড়াও চন্দ্রপ্রভার উল্লেখযোগ্য লেখার সংখ্যা কম নয়।
দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশের নারীদের অবস্থা নিয়েও অবহিত ছিলেন চন্দ্রপ্রভা। শিবসাগর থেকে প্রকাশিত মহিলাদের মাসিক পত্রিকা ‘ঘর জেউতি’-তে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে দুটির উল্লেখ করা যায়: ‘উন্নতি পথত রুশ নারী’ এবং ‘বৈদেশিক পণ্ডিতসকলর মতামত’। প্রথমটিতে বিপ্লব পরবর্তী সময়ের সোভিয়েত রাশিয়ার নারীদের উন্নত অবস্থার বিবরণ দেন; নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেন। মেয়েদের শিক্ষা, সাক্ষরতা, সংগঠন; তাদের নিজস্ব পত্রপত্রিকা এবং সমস্ত কাজে যোগদানের বিষয়টি তুলে ধরেন। সেখানে গর্ভিনীদের জন্য যথাযথ চিকিৎসা, শিশুদের যত্ন নেবার জন্য ক্রেশ, মেয়েদের হাসপাতাল, শিশুদের হাসপাতাল ইত্যাদি কী কী সুযোগসুবিধা তারা পেয়ে থাকে আর এই দেশে অসমিয়া নারীদের বাস্তব অবস্থাটি কী— তা তুলনা করে দেখান।
দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি পশ্চিমী বিদ্বান, পণ্ডিত ও কবিরা নারীদের কী চোখে দেখেন তার উল্লেখ করেন। লর্ড বায়রন, সার্ল, টমাস মুর, জেমস নর্দিংটন থেকে শুরু করে মিলটন, ওয়াশিংটন আরভিং, গোল্ডস্মিথ প্রমুখ ব্যক্তিরা নারীকে কোন উচ্চ পাদপীঠে স্থান দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করে দেখান। দুর্ভাগা এই প্রাচীন দেশ এবং ওই অর্বাচীন সময়, যখন এক নারীকে বিদেশি লেখকদের বয়ান টেনে এনে সমাজে নারীদের গুরুত্ব প্রমাণ করতে হয়! চন্দ্রপ্রভার লেখা ও কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি জানতেন সাধারণত পুরুষরা মেয়েদের সমস্যাগুলির গুরুত্ব বোঝে না, সেগুলিকে ছোটো করে দেখে। সে-কারণেই মেয়েদের সংঘবদ্ধ হওয়া, দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে নামা অত্যন্ত জরুরি।
১৯৭২ সালে ভারত সরকার চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ, কর্কটরোগে শয্যাশায়ী। নিজের জন্মদিন ষোলই মার্চ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফলে চব্বিশে মার্চ দিল্লিতে নিজের হাতে পুরস্কার গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাস্তব জীবন ও জগৎ ভারি অদ্ভুত। এ-হেন অভিযাত্রী ও অগ্রণী নারীর কথাও মানুষ প্রায় ভুলতে বসেছিল। দু’জন লেখিকার জন্য তাঁর নাম পুনরায় বৃহত্তর বৃত্তে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে। একজন তাঁর স্নেহপাত্রী পুষ্পলতা দাস। পুষ্পলতা রচিত ‘অগ্নিস্নাতা চন্দ্রপ্রভা’ (১৯৯৮) বইটি চন্দ্রপ্রভার জীবন ও সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে। দ্বিতীয়জন সাহিত্যিক নিরুপমা বরগোহাঞি। চন্দ্রপ্রভার জীবন ও কর্মের উপর ভিত্তি করে তিনি একটি বৃহৎ উপন্যাস লেখেন, নাম দেন সেই ‘অভিযাত্রী’ (১৯৯৫)। উপন্যাসটি ১৯৯৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। তারপর ২০০২ সালে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ চন্দ্রপ্রভার সম্মানে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।
একশো বছর আগে চন্দ্রপ্রভা অতি প্রয়োজনীয় যে-সংস্কারগুলির সূত্রপাত করে গেছেন, সেই পথ ধরে আজ অনেক নারী এগিয়ে এসেছে। সারা দেশে মেয়েদের চলার পথ কিছুটা হলেও সুগম হয়েছে। তবে কাজ কিন্তু শেষ হয়নি। এখনও অনেক অসাম্য, অনেক কুসংস্কার, অনেক বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে মেয়েরা এবং মেয়েদের দ্বারা অন্য মেয়েরা, অন্য শ্রেণীর মেয়েরা। চন্দ্রপ্রভার পুণ্য জন্মদিনে এই কথাটাই সব নারীপুরুষকে স্মরণ করিয়ে দেবার।
গণবিস্মরণ মানুষকে অনেক মহান আইডিয়া ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চন্দ্রপ্রভাকে স্মরণ করে লেখা এই নিবন্ধটি আপাতত শেষ করব ওঁর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে: ‘আমাদের উদ্দেশ্য নয় সভা-সমিতি করে স্ত্রীলোকদের ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে পুরুষের মতো করে তোলা। আমাদের মধ্যে যাতে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, শিক্ষার বিস্তার হয়; স্ত্রীজাতি যাতে আবার মাতৃমূর্তিতে, গরীয়সী রূপে আবির্ভূত হতে পারে; আমাদের বিধবাদের দুঃখের নিরসন হয় ও নিরাশ্রয় শিশুদের জন্য একটি সুউপায় হতে পারে; এই সবকিছুর জন্য আমাদের নিজেদেরই মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে হবে। মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে, সোজা হয়ে না দাঁড়ালে এসবের প্রতিকার অসম্ভব।’
গোয়ালপাড়া অধিবেশন, অসম মহিলা সমিতির সম্পাদিকার রিপোর্ট, ‘ঘর-জেউতি’ ১৮৪৯ শকাব্দ (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ)।