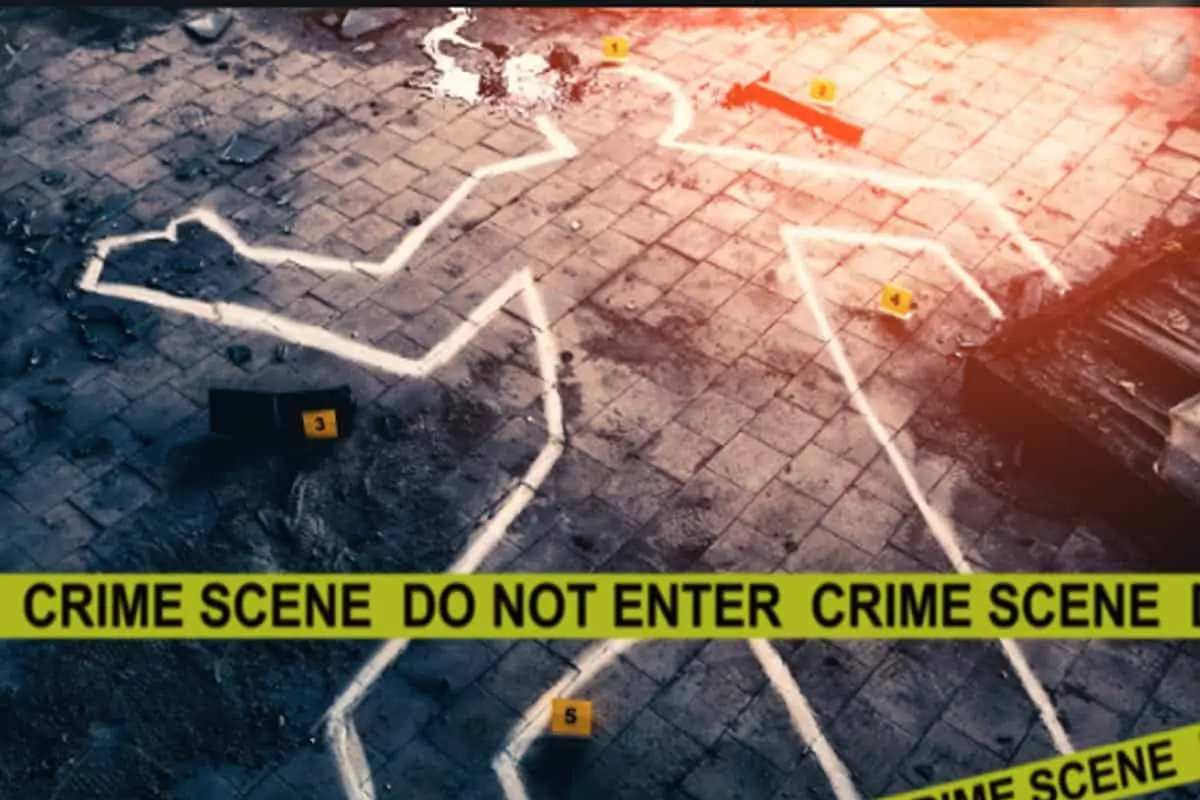গৌতম অধিকারী
১৮৫৭ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি। তাদের তত্ত্বাবধানে শিয়ালদা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১০ মাইল রেলপথ তৈরির কাজ শুরু হয় ওই ১৮৫৭-তেই। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের গোলোযোগে কাজটি কিছুদিন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। পরে কাজ শুরু হয় এবং ১৮৬২-র ১৯ সেপ্টেম্বর এই লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ট্রেন চালু হয় কলকাতা থেকে রানাঘাট স্টেশন পর্যন্ত। বগুলা নামের এক অখ্যাত জনপদকে বেস স্টেশন (Base Station) তৈরি করে প্রথমে পোড়াদহ এবং পরে জগতি স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের জন্য সমস্ত পরিকাঠামো তৈরির কাজটিও একসঙ্গে শুরু হয়েছিল। ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ রানাঘাট থেকে জগতি পর্যন্ত প্রথম রেলযাত্রা শুরু হলেও নিয়মিত যাতায়াতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত।
বেস স্টেশন হিসেবে বগুলা রেললাইন তৈরির জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এখান থেকেই রেলপথ নির্মাণের সমস্ত কিছু সরবরাহ করা হতো। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে রেলপথটি চালু হবার সময়ে রানাঘাট থেকে জগতি পর্যন্ত পথে স্টেশন ছিল বগুলা, দর্শনা, পোড়াদহ, চুয়াডাঙ্গা ও জগতি (কুষ্টিয়া)। দেশভাগের পরে সেই পুরনো রেলওয়ে স্টেশনগুলোর মধ্যে একমাত্র বগুলাই রয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মধ্যে। যদিও জনপদ হিসেবে বগুলার ইতিহাসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয় না। কেননা, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের প্রকাশনা অমিয় বসু সম্পাদিত ‘বাংলায় ভ্রমণ’ নামের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিতে আড়ংঘাটা, মাজদিয়ার কথা থাকলেও বগুলা সম্পর্কে কোনো কথা নেই। কিন্তু ছোট্ট গ্রামীণ জনপদ বগুলার সে অর্থে কোনো কৌলিন্য না থাকলেও ধীরে ধীরে একটা পরিসর সে খুঁজে নিতে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থেই। নদিয়া-যশোরে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও খানিকটা শিক্ষা প্রসারের কাজ তদারকি করবার জন্য এখানে খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটি ১৮৩৮ সাল নাগাদ গড়ে তুলেছিল একটি ডাকবাংলো। মিশনারি ছাড়াও জেলা সদর কৃষ্ণনগর যাবার পথে এখানে বিশ্রাম বা রাত্রিবাস করতেন রাজপুরুষেরা। দেশিয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই ডাকবাংলোকে বিশ্রামকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিতেন, এমন কথা লোকমুখে শোনা যায়। এটি ছাড়া এই জনপদের অন্য কোনো আকর্ষণ ছিল বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। এই ছোট্ট জনপদটিতে স্টেশন গড়ে ওঠে মূলত জেলা সদর কৃষ্ণনগরের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার জন্য। এমনকি একসময় স্টেশনটি মানুষের মুখে মুখে কৃষ্ণনগর-বগুলা নামেও পরিচিত ছিল। কৃষ্ণনগরের দূরত্ব বগুলা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার। যদিও রেলওয়ের নথিতে বগুলা (Boogula) নামেই তার পরিচয় লিপিবদ্ধ ও স্বীকৃত।
১৮৬২-তে রেলওয়ে স্টেশনটি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বগুলার স্থানিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে ঠিকই, কিন্তু রাতারাতি এমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি যে বগুলা কোনো স্বতন্ত্রচিহ্নিত জনপদ হয়ে উঠতে পারে। তবুও এখানে ছিল নীলচাষের অবাধ আয়োজন। খালবোয়ালিয়া কানসার্নের তত্ত্বাবধানে থাকা ভাজনঘাট কুঠিবাড়ির অধীন বগুলাতে তৈরি হয় নীলকুঠি। তবুও নীল বাজারজাতকরণের চেষ্টার সঙ্গে রেলওয়ে স্টেশন প্রতিষ্ঠার একটি কষ্টকল্পিত সম্পর্ক গড়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও সেটাকে মান্যতা দেওয়া কঠিন। কারণ, ১৮৬২ বা ১৮৬৪ সালে নীলচাষের রমরমা তলানিতে এসে গিয়েছে। কিন্তু ১৯৩৮-এ প্রতিষ্ঠিত কেরু এ্যান্ড কোম্পানির চিনিকল দর্শনাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বগুলার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। চূর্ণী নদীর দুপাড় দিয়ে প্রসারিত বেলে-দোআঁশ মাটিতে প্রচুর আখচাষ হতো। চিনিকলে এই আখ সরবরাহ করবার বিষয়ে বগুলার একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। কেরু কোম্পানি বগুলা বাজারে নিজেদের উদ্যোগে আখ জমা, মাপা ও ট্রেনে করে দর্শনাতে পাঠানোর জন্য কেন্দ্র গড়ে তোলে। বর্তমানে যা হাটচালি বা ছোটোবাজার নামে পরিচিত এবং এসব আখ জমা রাখার জন্য বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে বেশ কয়েকটি গুদামঘর গড়ে ওঠে। এছাড়া তিনটে বড়ো বড়ো বিল্ডিং রয়েছে যেগুলোর অবস্থান এখনকার বেনফিশ মার্কেটের (কিছুদিন আগে খোয়ার মাঠ) উত্তরদিকে বাড়িঘরের আড়ালে। একটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। এগুলো ছিল গার্ডরুম। অপর গোডাউন বা গুদামঘরটি ছিল ১নং প্ল্যাটফর্মের পশ্চিমদিকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কোয়ার্টার ও প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি অংশে।
বর্তমানে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মটি বারো বগির ইএমইউ কোচ দাঁড়াবার জন্য খানিকটা এলাকা বাড়িয়ে অবস্থিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এটা এতটা বড়ো ছিল না বলাই বাহুল্য। তবে রানাঘাটের পরে যে স্টেশনগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বগুলা রেলওয়ে স্টেশন ও সংলগ্ন রেলওয়ে কোম্পানির জায়গা অনেকটাই বেশি। আপাতত বগুলা স্টেশনপাড়া দক্ষিণ অংশের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতরের তৈরি কলোনি পুরোটাই রেলওয়ের সম্পত্তি। নতুন গড়ে ওঠা বেনফিশ মার্কেটের নাম ছিল খোয়ার মাঠ এবং ডাকবাংলো ঘেঁষে বিরাট জলাশয়ের পুরনো নাম ‘রেলপুকুর’ প্রমাণ করে দুটোই রেলওয়ের সম্পত্তি। মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রয়োজনীয় ইটের যোগান পাওয়ার জন্য মাটি কাটার ফলে রেলপুকুর তৈরি হয়েছে। আর সেই ইট থেকে গাঁথুনির কাজে খোয়া ভাঙার কাজ হয়েছিল যে মাঠে, তার নাম হয়েছিল ‘খোয়ার মাঠ’। এমনকি স্টেশনের পাশে অবস্থিত কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রসারিত বর্তমান স্টেশন রোডের বামদিকে পোস্ট অফিস রোড পর্যন্ত ও ডানদিকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত গোটা এলাকাটাই রেলের। প্রকৃত অর্থে শিয়ালদা-গেদে রেলওয়ে সেকশনে রানাঘাট জংশনের পরে কোনো স্টেশনে রেলওয়ের এতটা সম্পত্তি ছিল না। তথ্য বলে বগুলা রেলওয়ে স্টেশনকে কেন্দ্র করে কোম্পানির জমির পরিমাণ ৫৫ একর। এ থেকে বোঝা যায় ছোট্ট জনপদ হলেও জেলার যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেদিন রেলওয়ে কোম্পানি বগুলার স্থানিক গুরুত্ব অনেকটাই অনুধাবন করে এত জমি কিনেছিল।
শুধুমাত্র আখ বা ইক্ষু নয়, এতদঞ্চলে পাটচাষেরও একটা বিস্তৃত পরিসর ছিল এক সময়ে। রেললাইন তৈরি হবার আগে নদীপথে পাট নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একদিকে ইছামতী, গোরাগাঙনি— অন্যদিকে চূর্ণী ও ডিঙিটানা যোগে পাটের বড়ো বড়ো নৌকা গিয়ে ভাগীরথী-গঙ্গায় মিশত এবং হুগলি নদীর দু’পাড়ে গড়ে ওঠা পাটকলগুলিতে সাপ্লাই হত। বগুলা রেলওয়ে স্টেশন তৈরি হবার পর নদীপথগুলোর গুরুত্ব সেভাবে কমেনি, বরং ছোটো ছোটো নদী ও বিল-বাওড়ের পথ ধরে পাটবোঝাই নৌকা এসে ভিড়ত রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী একদিকে গোরাগাঙনির বিভিন্ন ঘাটে, অন্যদিকে আন্ধার বিল ও লক্ষ্মী বিলের কিনারে। ফলতঃ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সঙ্গে চাষীদের কিছুটা উপকার যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হতে শুরু করে, এতে সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও জনপদের জনসংখ্যার বিন্যাসে তখন পর্যন্ত তেমন কোনো গুরুতর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।
১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি বগুলা জনপদের জনসংখ্যার ভারসাম্যে বিপুল পরিবর্তন এনে দেয়। অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী উদ্বাস্তু পরিবারগুলো, যাঁরা নির্বিবাদে বিভক্ত বঙ্গের পূর্বাংশ থেকে এলেন, তাঁরা অনেকেই জমিজমা কিনে বসতি স্থাপন করেছেন বিস্তৃত কৃষিজমিগুলোতে। বিভক্ত নদিয়ার পূর্বাংশের কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ৪৭-এর পরপরই সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে এদেশে স্থায়ী হয়েছেন অনেকে। এই বিনিময় প্রথার মাধ্যমে আসা উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগের বসবাস বগুলা পুরাতন পাড়া এলাকায়। এলাকার আদি অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের জমি খানিকটা কিনে কিংবা জবরদখল করে বসবাসের ঘটনাও কম ঘটেনি। অনেক মুসলমান পরিবার দেশভাগের প্রভাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের মতো উদ্বাস্তু হয়ে চলে গেছে পাকিস্তানে। তাঁদের ওয়ারিশহীন জমি দখল করে বসেছে হিন্দু উদ্বাস্তুদের একাংশ। আবার নিরূপায় অনেক মানুষ প্রধানত রেলওয়ের ফাঁকা জায়গায় বসতি শুরু করে। বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের পাশে রেলওয়ে কোম্পানির বিশাল সম্পত্তির অধিকাংশই যে আজ দখলদারদের হাতে, এই সত্যটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। পরিবর্তন যেটুকু ঘটেছে সেটা এই যে ১৯৯৩ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতর একটা বিস্তৃত এলাকা রেলওয়ের কাছ থেকে লিজ নিয়ে পাট্টা প্রদান করেছে। আর রেলওয়ের খোয়ার মাঠে পরিবেশগত ভারসাম্যের সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেনফিশ মার্কেট। বাজার-সংলগ্ন রেলওয়ের জায়গায় গড়ে উঠেছে দোকান। ফলত একদা বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের বৃহৎ এলাকা সংকুচিত হতে হতে শুধু প্লাটফর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেমন সীমাবদ্ধ হতে হতে হারিয়ে গেছে বৃহত্তর হাঁসখালি অঞ্চল তথা চূর্ণী-জনপদের ইতিহাসটাও।
চূর্ণী-জনপদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় বগুলা রেলওয়ে স্টেশন একদা জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে নানান দলিল দস্তাবেজে; বিশেষ করে শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্মৃতিচিত্রে। সেসব প্রমাণ কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও বা পরোক্ষ। সাধারণভাবে বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাসের একটি জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসের মাস্টারমশাই যদুনাথ মুখুজ্জের বাড়ি বেড়াবেড়ি গ্রামে, যেখানে তিনি যাতায়াত করতেন বগুলা স্টেশন হয়েই। সাহিত্যের এই বিষয়গুলোর জন্য স্বতন্ত্র অবকাশ রেখে আমরা বরং তথ্যের কাছে যেতে পারি। বঙ্কিম-যুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গদ্যকার নদিয়ার ভূমিপুত্র মীর মোশারফ হোসেনের স্মৃতিচিত্রে বর্ণিত বগুলা-হাঁসখালির প্রত্যক্ষ বর্ণনা প্রথমে দেখে নিতে পারি।
মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবিভক্ত নদিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক গদ্যকার মোশারফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘আমার জীবনী’ গ্রন্থের একটা বড়োসড়ো অধ্যায়ে বগুলা-হাঁসখালির স্মৃতিকথা রয়েছে, যা সমসাময়িক বগুলা ও হাঁসখালিসহ বৃহত্তর চূর্ণী-জনপদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মীর পিতার নির্দেশে কৃষ্ণনগর আসেন এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি লিখেছেন— ‘পিতৃদেবের আদেশ— কৃষ্ণনগর যাইয়া কলেজে পড়। আমি সমুদায় ঠিক করিয়া দিতেছি।’ এক বছর পরে তিনি কৃষ্ণনগর থেকে পিতার বন্ধু নাদির হোসেনের কলকাতার চেতলার বাড়িতে যান। সেখান থেকে ফিরে আবার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং সেখান থেকে লাহিনীপাড়ায়। পরবর্তীতে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন।
তাঁর লেখাটি নিছক বর্ণনা নয়, কার্যকারণ ও পরিপ্রেক্ষিতসহ রসসাহিত্যিকের কলম। মীর লিখেছেন, ‘কৃষ্ণনগর চলিলাম। কৃষ্ণনগর কোথায় আমাদের দেশে কেউ জানিত না। কুষ্টিয়া মহকুমা স্থাপিত হইলে, কিছুদিন পাবনার অধীনে থাকিয়া পরে নদীয়া জিলার অধীন হয়। পাবনার নিকটে থাকিতে নদীয়ার সামিল হওয়ার কারণ? —লোকের সুবিধা। বর্ষাকালে পদ্মানদীর পার হওয়া জীবন সংশয়। দক্ষিণ পার নদীয়ার সামিল হইয়া বিশেষ উপকার হইয়াছে। বগুলা স্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর নদীয়া জজ কাছারী এগার মাইল ব্যবধান। এ এগার মাইল পথেও ঘোড়াগাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। কুষ্টিয়া অঞ্চল হইতে কৃষ্ণনগর যাওয়া-আসার কোন প্রকার অসুবিধা নাই।’
এই বর্ণনা বুঝিয়ে দেয় কৃষ্ণনগর যাতায়াতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বগুলা রেলওয়ে স্টেশন। এবং তুলনামূলকভাবে পুরনো অন্যান্য স্টেশন মাঝদিয়া, বানপুর বা আড়ংঘাটা থেকে বগুলাপথে যাতায়াত অনেক সুবিধার ছিল এবং সে সময় বগুলা যে একটি জমজমাট রেলওয়ে স্টেশন ছিল তার প্রমাণ রয়েছে মীরের রচনায়— ‘বগুলা স্টেশনে গাড়ী লাগিল। টিকিট দিয়া স্টেশনের বাহিরে যাইতেই ঘোড়ার গাড়ীর সইস কোচওয়ান হাঙ্গামা করিয়া সকল সকল যাত্রীকেই ধরপাকড় আরম্ভ করিল। গাঁঠুরি ব্যাগ ইত্যাদি ধরিয়া টানাটানি একপ্রকার জবরানে ধরিয়া আপন গাড়ীতে তুলিল। কুলি, মজুর, সইস কোচম্যান মুখে বাঙ্গালা শুনিয়া আমি ত অবাক। যে এই সকল লোক এত ভাল কথা বলে, আমাদিগকে যে কথা সন্ধান তালাস খুঁজিয়া মুখে আনিয়া বলিতে হয়, এরা স্বভাবতই অনর্গল বলিয়া যাইতেছে।’
মীর ১৮৬৪ সালে কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন বগুলা রেলওয়ে স্টেশনে নেমে, অর্থাৎ শিয়ালদা থেকে জগতি পর্যন্ত প্রথম রেল চলাচলের বছরেই। তখন যে রেলওয়ে স্টেশন জুড়ে ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান থেকে শুরু করে সহিস, রেলস্টেশনের কুলি-মজুর সবাই অবাঙালি ছিল এবং বাঙালিরা এসব কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত না, তার একটা প্রমাণও তাঁর বর্ণনা থেকে উঠে এসেছে।
এমন একটা স্মৃতিচিত্র বগুলা রেলওয়ে স্টেশনকে ঘিরে রয়েছে প্রমথ চৌধুরীর অপ্রকাশিত ‘আত্মকথা’য়। ১৮৭৩ সাল নাগাদ চাকুরির বদলিসূত্রে তাঁর পিতা ও তিনি কৃষ্ণনগর আসেন। পাঁচ বছর বয়সের যেটুকু স্মৃতি মনে রাখতে পেরেছিলেন, তা লিখেছেন আত্মকথায় ২ অক্টোবর ১৯৪০-এ— ‘এখন বাল্যকালে ফিরে যাওয়া যাক। কৃষ্ণনগর এসে আমি হঠাৎ জেগে উঠলুম— অর্থাৎ আমি চেতনা পদার্থ হলুম। বোধহয় ঠিকে গাড়ির একদিন একরাত ঝাঁকুনিতে! যশোর থেকে বনগাঁ, বনগাঁ থেকে চাকদহ, বগুলা থেকে ন-মাইল দূরে কৃষ্ণনগরে একটা পুঁটলির মতো গাড়িতে করে আসতে হয়।’ ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। রেলওয়ের সুবিধা নিতেই বগুলা হয়ে কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন। এ কথাগুলোর সমর্থন রয়েছে প্রমথ চৌধুরীর বড়দি প্রসন্নময়ী দেবীর স্মৃতিগ্রন্থ ‘পূর্ব্বকথা’তেও।
বগুলা রেলওয়ে স্টেশন হয়ে কৃষ্ণনগর যাবার পরোক্ষ একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বেঙ্গল থিয়েটারের কৃষ্ণনগরে অভিনয়োপলক্ষে আগমন-সংক্রান্ত বর্ণনায়, নটি বিনোদিনীর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘আমার কথা’তেও। অনেকেই দাবি করেন, দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক কৃষ্ণনগরে অভিনয় হয়েছিল। একটা সম্ভাবনার কথা লেখা হয়েছিল ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত একটি সংবাদে— ‘… নীলদর্পণ… একবার কৃষ্ণনগরে অভিনীত হইলে ভালো হয়।’ (১২ ডিসেম্বর, ১৮৭২)। কিন্তু সত্যি সত্যিই অভিনয়টা হয়েছিল কি না, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ অবলম্বনে বেঙ্গল থিয়েটারের ‘মেঘনাদবধ’ কৃষ্ণনগরে অভিনীত হয়। এই নাটকে প্রমীলা চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে বিনোদনী ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘একবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ঘোড়ায় চড়িয়া অভিনয় করিতে পড়িয়া আঘাত লাগিয়াছিল।… প্রমীলার পার্ট ঘোটকের উপর বসিয়া অভিনয় করিতে হইত। সেখানে মাটির প্লাটফর্ম প্রস্তুত হইয়াছিল, যেমন আমি স্টেজ হইতে বাহিরে আসিব, অমনি মাটির ধাপ ভাঙ্গিয়া ঘোড়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।’ ৬ মার্চ ১৮৭৫ কলকাতায় প্রথম নাটকটির অভিনয় হয়। অনুমান করা হয়েছে কৃষ্ণনগরে এই অভিনয় হয় ১৮৭৫-এর এপ্রিল মাস নাগাদ। বিনোদিনী লিখেছেন, ‘আমাদের কোম্পানী কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে অভিনয় করবার জন্য আহুত হয়েছে। আমরা সব দল বেঁধে যে যার মোট-ঘাট নিয়ে শিয়ালদহে গাড়ীতে গিয়ে উঠেছি।’ কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যাওয়ার রেলপথ যেহেতু তখনও তৈরি হয়নি, সেহেতু বগুলা রেলওয়ে স্টেশনে নেমেই বেঙ্গল থিয়েটারের দলবল কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন— এতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৭৫-এ রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর রেলপথ চালু হয়নি।
প্রকৃত প্রস্তাবে জেলাসদর এবং সেকালের অন্যতম শহর কৃষ্ণনগরের সঙ্গে কলকাতার বুদ্ধিজীবী, দেশসেবক, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটা নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১৯০৫-এর ১ সেপ্টেম্বরের আগে বগুলা রেলওয়ে স্টেশন হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণনগরে যাতায়াতের মাধ্যম। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এসেছিলেন ১৮৪৭ সালে। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের পান্ডুলিপি সংগ্রহ করতে এসেছিলেন মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করবার জন্য। এরপর নানান প্রয়োজনে এসেছেন তিনি। শেষ এসেছেন তিনি ১৮৭৮ সালে। নদিয়া গবেষক মোহিত রায়ের সিদ্ধান্ত, ‘আমরা নিশ্চিত যে, বিদ্যাসাগর ১৮৭৮ সালে বগুলা পর্যন্ত ট্রেনে এসে চূর্ণি নদী পার হয়ে পাল্কীতে চড়ে কৃষ্ণনগরে এসেছেন।’ এছাড়া বগুলা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট খোঁজখবর রাখতেন, তার প্রমাণ রয়েছে ‘রত্নপরীক্ষা’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে। বগুলার পার্শ্ববর্তী গ্রাম মুড়াগাছার ঘোষ পরিবারের তিনকড়ি ঘোষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন রিজার্ভ করে বগুলা স্টেশন পর্যন্ত পণ্ডিতদের সমাদরে নিয়ে আসেন ঘোষ পরিবার। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয় ‘সাধারণী’ পত্রিকায়। বিদ্যাসাগর সেই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ব্যবহার করে সংস্কৃত কলেজের তিন পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ও প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্নের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে কামান দেগেছিলেন এই লেখাটিতে।
দীনবন্ধু মিত্র রচিত ‘নীলদর্পণ’ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন মধুসূদন, কথাটা সকলে ইদানিং মেনে নিয়েছেন। সেটা না হলেও দীনবন্ধু ও মধুসূদনের সখ্য সুবিদিত। অপরিসীম শ্রদ্ধার এই সম্পর্কের একখণ্ড উঠে আসে হাঁসখালির চূর্ণী নদী পার হওয়ার ঘটনায়। নগেন্দ্রনাথ সোম ‘মধুস্মৃতি’তে লিখেছেন, ‘‘একবার মধুসূদন ও দীনবন্ধু একত্রে কৃষ্ণনগর হইতে প্রত্যাগমনকালে অতি প্রত্যুষে হাঁসখালিতে নদী পার হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তখনও রজনীর শেষ অন্ধকার বিগত হয় নাই। মাঝি নৌকার ভিতর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দীনবন্ধু নৌকার নিকটে গিয়া তাঁহার পরিহাস-রসিক সুরে ডাকিয়া বলিলেন, ‘ও বাবা মাঝি! একবার ওঠ্, উঠে আমাদের গাঙ পার করে দিয়ে, আবার ঘুমুস।’ দীনবন্ধুর ডাকে মাঝির নিদ্রা ভাঙিল না। তখন মধুসূদন বলিলেন, ‘ওরূপ মিহিসুরে ডাকিলে কি আর মাঝির সাড়া পাবে?’ তিনি তৎক্ষণাৎ সাহেবী ঢংয়ে ‘Oh! You!’ প্রভৃতি কথায় ডাকিবামাত্র মাঝি ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া, তাঁহাদিগকে নদী পার করিয়া দিল।’’ স্মৃতিটা হাঁসখালির হলেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বগুলা রেলওয়ে স্টেশন। কারণ, হাঁসখালি হয়ে কলকাতা যেতে হলে বগুলা স্টেশন ছাড়া ট্রেনে ওঠার আর কোনো স্টেশন কাছাকাছি ছিল না। যে স্টেশনে নিয়মিত পদধূলি পড়ত নদিয়ার চৌবেড়িয়ার ভূমিপুত্র দীনবন্ধুর। আর কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর যাতায়াতের পথে স্বয়ং মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আসতেন মাঝেমধ্যেই।
স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নায়কদের যাতায়াতের পথ যে বগুলা রেলওয়ে স্টেশন ছিল, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহই নেই। কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ‘মনমোহন দাদা’ প্রবাদপ্রতিম মনমোহন ঘোষ অনেকবার বগুলা রেলওয়ে স্টেশন হয়ে কলকাতা গিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বগুলা ডাকবাংলোতে তাঁর অবস্থান ও জনসভা করার কথা লোকশ্রুতিতে মিলেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বগুলা রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনের কোয়ার্টারে থাকতেন বুকিং ক্লার্ক শৈলেন্দ্রনাথ বসু। খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের মানুষ। ঘটনাটা ১৯০৯ সালের। মাঝেমধ্যেই এই কোয়ার্টারে এসে থাকতেন শৈলেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারুচন্দ্র এবং শিয়ালদা থেকে কুষ্টিয়া ফেরার পথে নামতেন বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— বাঘা যতীন। শৈলেন বসুর কোয়ার্টারেই কথা হতো চারুচন্দ্র বসুর সঙ্গে। স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী ধারা তখন বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইংরেজের ওপর। ধরা পড়ছেন অনেক বিপ্লবী। সরকারি জাঁদরেল উকিল আশু বিশ্বাস নানান আটঘাট বেঁধে আদালতে লড়ছেন বিপ্লবীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে। অতএব সিদ্ধান্ত আশুকে সরিয়ে দাও পৃথিবী থেকে। এগিয়ে এলেন একজন, তিনি চারুচন্দ্র। বয়স মাত্র কুড়ি বছর। সদ্যবিবাহিত চারুর ডানহাত নুলো, শক্তিহীন। অগ্নিপুরুষ বাঘা যতীন কী ভেবেছিলেন জানার উপায় নেই। তবে রোগা টিংটিঙে প্রতিবন্ধী ছেলেটির উপর ভরসা করেছিলেন হয়তো এই ভেবে— সাহসের চেয়ে বড়ো নির্ভরতা আর নেই। এই বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের কোয়ার্টারে বসেই কি বাঘাযতীন সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন? দায়িত্ব দেওয়া হল চারুচন্দ্রকে। নুলো ডানহাতে বেঁধে নিলেন ওয়েবলি মার্ক পিস্তল। ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে থাকলেন জনকোলাহলমুখর সুবারবান আদালতের প্রবেশপথে। ডানহাত বাগিয়ে সোজা আশুর বুক তাক করে বামহাতে টানলেন ট্রিগার। বিকট শব্দে আদালত কেঁপে উঠল। মানুষ শুধু তাকিয়ে দেখল এক দেশদ্রোহীর রক্তাক্ত মৃতদেহ লুটিয়ে আছে মাটিতে।
চেষ্টা করেছিলেন চারু, পালিয়ে যেতে— পারেননি। পালানোর চেষ্টা নিজের জন্য নয়, তাঁর ভয় ছিল বৃটিশ পুলিশের অত্যাচারে সহযোদ্ধাদের নামধাম যদি বলে ফেলেন। আশঙ্কা সত্যি হলো। হাজতবাস থেকে জেলখানায় অত্যাচার নামল নির্মমভাবে। কিন্তু না, একটা গোপন ডেরা কিংবা একজন বিপ্লবীরও নাম বলেননি চারু। শুরু হলো বিচার, ওই আলিপুর আদালতে। প্রথম দিনের পরে নতুন সেশন ঘোষণা করলেন বিচারপতি এফ আর রো। হেসে উঠলেন আসামি চারুচন্দ্র, বললেন ‘আবার সেশন-টেশন কী! ফাঁসি দেওয়া হোক আমাকে। এটা পূর্বনির্ধারিত ছিল যে আশু আমার হাতে মরবে এবং আমার ফাঁসি হবে।’ ১৯০৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রায় দিল আদালত, সাজা ফাঁসি। ১৯০৯-এর ১৯ মার্চ ফাঁসি কার্যকর হলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চতুর্থ বাঙালি শহিদ। ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পর যশোর (পরবর্তীতে খুলনা) জেলার শোভনা গ্রামের কুড়ি বছরের যুবক চারুচন্দ্র বসু। বগুলা রেলওয়ে স্টেশন জুড়ে গেল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে। যদিও সেই ইতিহাস আজ আর কেউ মনে রাখেনি।
যেমন মনে রাখেনি এতদঞ্চলের শিক্ষাপ্রসারের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান, বগুলা মিডল ইংলিশ জুনিয়র হাইস্কুল— ১৯২৮ সালে গড়ে উঠেছিল বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে। এই সময়ের আগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল এখানে, কিন্তু সেটা ঠিক কোথায়, আজ আর নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। ১৯২৫ সাল থেকে বগুলা হাইস্কুলের প্রাথমিক রূপটি গড়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের তখনকার স্টেশনমাস্টার রামপদ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গী হিসেবে পান মেডিকেল অফিসার কালীপদ চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী স্টেশনমাস্টার শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে। স্থানীয় সম্পদশালী মানুষ সিরাজুল ইসলাম মুন্সী ও আব্দুল হামিদ মুন্সীর সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ মানুষকে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে ধান সংগ্রহ, পাট সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে চলে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা। তাঁদের উদ্যোগ এবং স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ১৯২৮-এর ১ জানুয়ারি তারিখে সেদিনের ‘বগুলা মিডল ইংলিশ জুনিয়র হাইস্কুল’, আজকের বগুলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতি ছিলেন বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার রামপদ মুখোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন মেডিকেল অফিসার কালীপদ চট্টোপাধ্যায়। দক্ষ সংগঠক ও কৃতবিদ্য মানুষ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ খুলনা থেকে আসেন প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে।
দেশভাগের আগেই ১৯৪৬ সালে সম্পূর্ণভাবে হাইস্কুল অর্থাৎ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে এলেন চূর্ণীতীরবর্তী শোনঘাটা গ্রামের মানুষ প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক ভোলানাথ নাথ। আবার বগুলা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই স্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে শুরু হয় এতদাঞ্চলের প্রথম দুর্গোৎসব। খুব নির্দিষ্ট করে বলার সুযোগ থাকছে যে, বগুলা রেলওয়ে স্টেশন শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস নয়, বরং তার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে একটি পিছিয়ে পড়া জনপদের সামগ্রিক হয়ে ওঠার ইতিহাস। এখন সেই ইতিহাসের উপরে কোথাও কি পড়তে শুরু করেছে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসী থাবা?