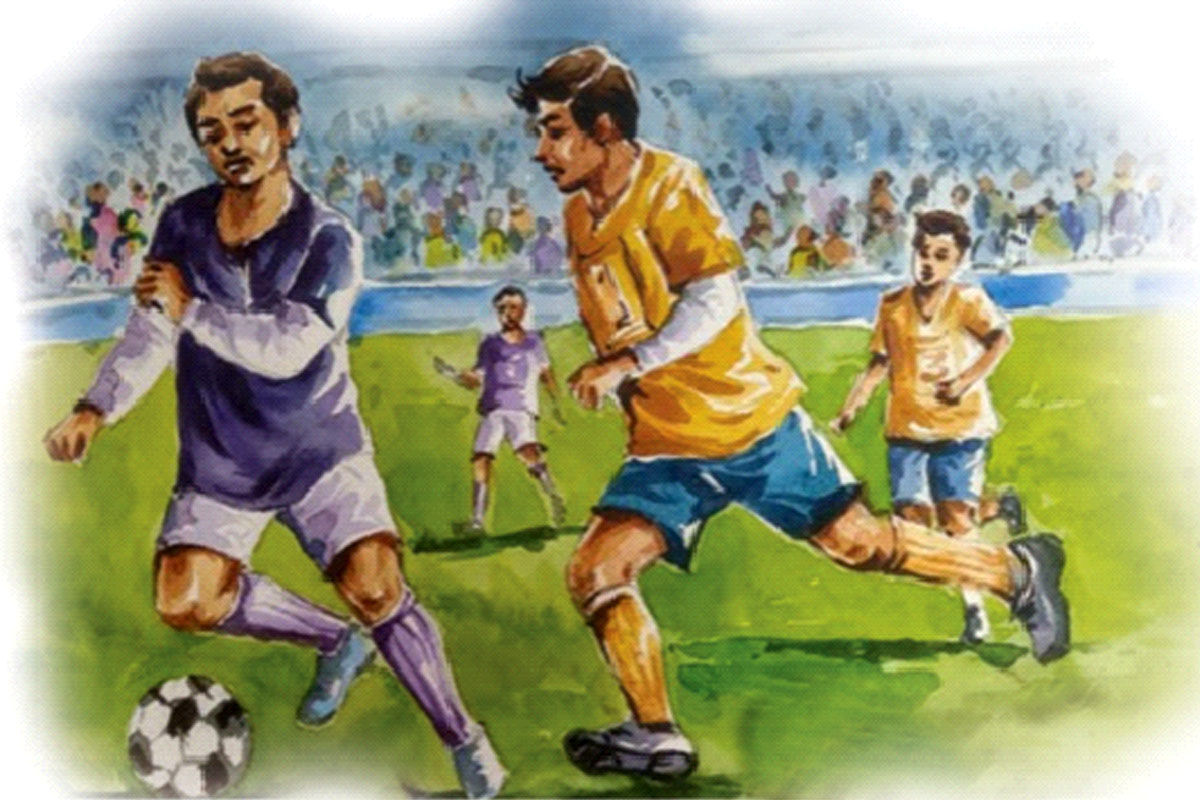গৌতম অধিকারী
১৯৬৮-র জুন মাসের এক বর্ষণসিক্ত দুইপ্রহরবেলা। তারিখটা ২৬। কৃষ্ণনগর জংশন স্টেশনে নেমে দুটো রিকশায় শান্তিপুর-নবদ্বীপ ছোটো রেললাইনের কৃষ্ণনগর রোড স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলছেন চারজন— খালেদ চৌধুরী, রণজিৎ সিংহ, ঈশিতা সিংহ এবং এঁদের তুলনায় বয়সে তরুণ সৌম্য চক্রবর্তী। এঁরা তখন কলকাতা ফোক গবেষণা কেন্দ্রের হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কথা বলছেন বিস্মৃত শিল্পীদের সঙ্গে; এবং সুযোগ হলে রেকর্ড করে নিয়ে আসছেন শিল্পীর হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীতের কিছু কিছু নমুনা। এই অনুসন্ধানপর্বে তাঁরা খুঁজে চলছিলেন অনন্তবালা বৈষ্ণবীকে।
প্রাথমিকভাবে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন মারা গেছেন অনন্তবালা। খানিকটা নিরাশা গ্রাস করল। পরে জানা গেল বেঁচে আছেন অনন্তবালা, বড়ো অনাদরে-অবহেলায়; কৃষ্ণনগর শহরের উপকণ্ঠে রোড স্টেশনসংলগ্ন এক উদ্বাস্তু পল্লিতে। অনেকটা ঝক্কি পেরিয়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন বৈষ্ণবীর ঝুপড়ির সামনে। ভেতরে বসে কাঁথা সেলাই করছেন এক বৃদ্ধা। তারপর অচেনা আগন্তুকদের দেখে তিনি বাইরে এলেন। মনে হল তাঁর বয়েস
৭০-এর কাছাকাছি। রোগা ছিপছিপে গড়ন। গলায় তুলসির মালা। ওঁদের একজন রণজিৎ সিংহ লিখেছেন, “আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম আর উদ্দেশ্যের কথা বললাম। বৃদ্ধার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি, চোখে সন্দেহ। জানালেন তিনিই অনন্তবালা বৈষ্ণবী। আমাদের এতদিনের চেষ্টা সার্থক হল। অনন্তবালাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা আর কৃতার্থতার বোধে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। পরক্ষণেই বুঝলাম ভুল করেছি। বৈষ্ণবরা কাউকে পা ছুঁতে দেন না। অনন্তবালাও সঙ্গে সঙ্গে আমার পা ছুঁতে চাইলেন। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।”
১৯৬৮ সালের এই কাঁটা দেওয়া পুনরাবিষ্কারের গল্প সম্ভবত বহুদিন পরে প্রথম আমরা পেলাম ১৯৮৩ সালে, ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার একটি সংখ্যায়। লিখেছেন রণজিৎ সিংহ। বলা যায় এই লেখাটির সূত্র ধরেই কিঞ্চিৎ অনন্তবালাকে নতুন করে চেনার পথটা সুগম হলো। আর জানা গেল তাঁর অনন্তবালা নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হরসুন্দরী নামের একজন নারীর হয়ে ওঠার লড়াই, সাফল্য ও জীবনের ব্যর্থতার কথাও বটে।
সেই লড়াইয়ের কাহিনি স্বয়ং শিল্পী ১৯৬৯-এর ২৬ জুন রণজিৎ সিংহ, খালেদ চৌধুরীর কাছে নিজে যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলো গুছিয়ে লিখেছেন রণজিৎ সিংহ এভাবে— “প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সম্পর্কে যা জানতে পারি তা এই— অনন্তবালা বৈষ্ণবীর জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দে। তাঁর দেশ বরিশাল। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন। সে বছর মেগাফোন কোম্পানি তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড করে। প্রথম গান ‘প্রাণ কান্দে ভাইরে সদায় মাইয়া বলে’। লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রথম যিনি রেকর্ড করবার জন্য মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন তিনি হলেন ছমীর [ছমীরুদ্দিন?]। ছমীর ছিলেন কোম্পানির বড়সায়েব [জে এন ঘোষ]-এর মোটরগাড়ির চালক এবং তিনি ঢাকার লোক। অনন্তবালার সঙ্গীত শিক্ষার গুরু পরেশ দেব। (মাটির সুরের খোঁজে / অনন্তবালা / প্রতিক্ষণ, ১৯৮৫) সত্যের অনেকটা কাছাকাছি এই বর্ণনা। কিন্তু এখানেও হরসুন্দরী নেই।
হরসুন্দরীকে আমরা জানলাম ১৯৮৯-তে, একটি ছোট্ট কাগজ ‘পণ’-এ প্রকাশিত অধ্যাপক মণি মণ্ডলের লেখা ‘সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী— অনন্তবালা বৈষ্ণবী’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধধর্মী রচনার মাধ্যমে। সেই সূত্র বলছে, হরসুন্দরীর জন্ম হয়েছিল বাংলা ১৩১০ সালের ১৪ ফাল্গুন। ইংরেজি হিসেবে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ। অবিভক্ত বরিশাল জেলার ছয়ঘরিয়া (মতান্তরে ছয়ঘইরগা) গ্রামে। বর্তমানে যে গ্রামের নাম পূর্ব সাঁচিয়া। বাবার নাম তারিণীচন্দ্র গাইন। গাইন পরিবারের আর একটি বাড়ি ছিল তুরুকখালি গ্রামে, যার এখনকার পরিচয় পূর্ব সাঁচিয়া (বর্তমান পিরোজপুর জেলা)।
বিল-বাওড়ের দেশ বরিশাল। তুরুকখালি একেবারেই ছিল বিলাঞ্চল। বর্ষাকালে সেখানে বসবাস কষ্টকর ছিল বলেই হয়তো ছয়ঘইরগা বা ছয়ঘরিয়াতে দ্বিতীয় বাড়িটি তৈরি করতে হয়েছিল গাইন পরিবারকে। পাশ দিয়ে বয়ে-চলেছে ছোট্ট নদী বেলুয়া। এই দুই গ্রামেই কেটেছে হরসুন্দরী অনন্তবালার শৈশব-কৈশোর-যৌবন। দেশভাগের আগে পর্যন্ত। যদিও কৃষ্ণনগরে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রণজিৎ সিংহ জানাচ্ছেন অনন্তবালার জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দে। আর তিনি কলকাতা আসেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। এবং সেই বৎসর অনন্তবালার প্রথম রেকর্ড বের হয়। বাংলা ১৩৩৮ সাল অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩১। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘বেতার জগত’ পত্রিকায় মেগাফোনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, যার হেডিং ছিল ‘ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত রেকর্ডের বিজয়মাল্য’। এই বিজ্ঞাপনে অন্যান্যদের সঙ্গে অনন্তবালার রেকর্ডের যে গানটির বিজ্ঞাপন ছিল, যে রেকর্ডটির নম্বর JNG 483। আমাদের তথ্য বলছে রেকর্ডটিতে দুটো গান ছিল–‘আমার প্রাণ কান্দে ভাইরে সদাই মাইয়া বলে’ এবং ‘প্রাণসখীরে আমার’। বিজ্ঞাপন ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হলেও রেকর্ডটি বাজারে আসে ১৯৩৮ সালে। স্বাভাবিকভাবেই অনন্তবালার বাংলা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩১-এ তাঁর কলকাতায় আসা। এবং অন্তত পাঁচটি বছর জুড়ে তাঁর হয়ে ওঠার লড়াই।
নদীকেন্দ্রিক বঙ্গজীবনে শৈশব-কৈশোরের এই কাহিনি প্রকৃতির আনন্দনিকেতনে বেড়ে উঠছিলেন অনন্তবালা। গানকে পেয়েছিলেন পারিবারিক উত্তরাধিকারে। হরসুন্দরী বা অনন্তবালার পারিবারিক পদবির কথা। পারিবারিক উপাধি ‘গাইন’। আর ভাটি-বাংলাদেশের প্রচলিত প্রবাদ হলো ‘বাজাতে বাজাতে বাইন, / গাইতে গাইতে গাইন।’ অনুমান করতে পারা যায় ‘গাইন’ পদবি এই পরিবারের অর্জন করা। অর্জনের ইতিহাস অজানা হলেও পরিবারটি যে সর্বার্থেই পদবিটির যোগ্য, এতে সন্দেহ নেই। হরসুন্দরীর ঠাকুরদাদা গাইতে পারতেন। হরসুন্দরীর বাবাও পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, কীর্তন, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গান সুন্দর গাইতেন। দু’চার গ্রামের মধ্যে কীর্তন, হরিরলুঠ, মহোৎসব হলে ডাক পড়ত তারিণী গাইনের। সঙ্গে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন। তারিণীবাবুর তিন ছেলে— যোগেশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র এবং গণেশচন্দ্রের মধ্যে উমেশ ও গণেশ সুগায়ক। এঁদের নিজেদের কীর্তনের দল ছিল। রামায়ণ গানের দলও এঁরা করেছেন। ফলে খুব অল্প বয়সেই হরসুন্দরী বাবার সঙ্গে কীর্তন-মহোৎসবে যেতেন। গান গাইতেন গুপিযন্ত্র বাজিয়ে। এমনকি বরিশালের নিজস্ব লোকগানের পালা ‘রয়ানী’ (রোদনী>রয়ানী), যা আসলে ‘মনসামঙ্গলে’র রচয়িতা বিজয় গুপ্তের কাহিনির গীতিপালা, সেই দলেও গান গেয়েছেন হরসুন্দরী। সেকালের নিয়মানুযায়ী মাত্র সাত বছর বয়সে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে সেকালের নিয়মানুযায়ী কিছু টাকা পণের বিনিময়ে বিয়ে হয়ে গেল হরসুন্দরীর। পাত্রীর গায়ের রঙ কালো পণ জুটল না বেশি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে দুর্ভোগের জীবনকে জুটিয়ে নিলেন হরসুন্দরী। বিবাহিত জীবনের পরিসর এতটাই কম যে, অনন্তবালা স্বামীর কথা ভালো করে মনেও করতে পারেননি। জীবনের দুর্ভোগ তখন তাঁকে বুঝি বা টানছিল অন্য কোনো জীবনের পথে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে এলেন হরসুন্দরীর অতীত, হয়ে উঠলেন অনন্তবালা, অনন্তবালা বৈষ্ণবী।
কলকাতার উপকণ্ঠে প্রথম এসে উঠলেন গঙ্গার ওপাড়ে হাওড়ার শালকিয়াতে ৭৪, হালদার পুকুর লেন-এ হরিদাস বৈরাগীর আখড়ায়। বেঁচে
থাকার উপায় একমাত্র গান গেয়ে মাধুকরী বা ভিক্ষাবৃত্তি। এমনই এক দিনে পথের ধারে তাঁর গান শুনতে শুনতে একটি ছেলে আশ্চর্যজনক প্রস্তাব দেয়, “বায়না করে দিলে গাইবেন গান?” খানিকটা স্তম্ভিত অনন্তবালা নিজেকে সামলে নিয়ে রাজী হয়ে যান প্রস্তাবে। তারপর সেই ছেলেটি, যার নাম কোনোদিন ভোলেননি অনন্তবালা, সেই ইসমাইলের হাত ধরে শালিমার কোম্পানি আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান গাইলেন অনন্তবালা। প্রতিযোগিতামূলক আয়োজনে গুরু-শিষ্য পরম্পরার গান। জাহাজের সারেঙ অথচ গানপাগল মঙ্গল ফকিরের বিপরীতে শিষ্যধারায় গাইলেন অনন্তবালা। তাঁর নিজের কথায় “সে বছরে মেগাফোন কোম্পানি তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড করে। প্রথম গান ‘প্রাণ কান্দে ভাইরে সদাই মাইয়া বলে’। লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রথম যিনি মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন তিনি হলেন ছমীর [ছমিরুদ্দিন?] ছমীর ছিলেন কোম্পানির বড়সায়েব [জে এন ঘোষ]-এর মোটরগাড়ির চালক এবং তিনি ঢাকার লোক।” (মাটির সুরের খোঁজে, অনন্তবালা, প্রতিক্ষণ)
শুরু হলো অনন্তবালার পর্ব। ১৯৩৮-এ বের হয় অনন্তবালার প্রথম গান, রেকর্ড নম্বর— J.N.G. 483। গানটি ছিল
“আমার প্রাণ কান্দে ভাইরে, সদাই মাইয়া বলে
হ’ল মাইয়াতে উৎপত্তি জগত
মাইয়া আমার হৃদিদলে।।
মাইয়ার গুণের কী দেই সীমা
দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলা—
করেন সেই কালা
যেদিন গিরি ধারণ করলেন কৃষ্ণ—
সেদিন শক্তিরূপে সঞ্চারিলে।।”
গানটি তিনি গেয়েছিলেন পরেশ দেবের তত্ত্বাবধানে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রথামাফিক অনন্তবালার গানের গুরু কেউ ছিল না। গান শিখেছিলেন প্রাথমিকভাবে বরিশালের জ্ঞান দত্তের কাছে। মেগাফোন কোম্পানিতে সেই জায়গা নিলেন পরেশ দেব। এমনকি স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরে তাঁর তত্ত্বাবধানেও গানের রেকর্ড করেছেন অনন্তবালা।
হিজ মাস্টার্স ভয়েসের বাণিজ্যিক আয়োজনের বিপরীতে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমান্তরাল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ রেখেছিল জীতেন ঘোষ মেগাফোন কোম্পানি। ১৯১০ সালে গড়ে মেগাফোনের গুরুত্ব ও অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক, এমন কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। আনকোরা শিল্পীদের সন্ধান চালিয়ে তাঁরা একের পর এক রেকর্ড বাজারে এনেছেন। অচেনা অনন্তবালাকে সেই মেগাফোনের কাছেই নিয়ে এসেছিলেন। দক্ষ জহুরী জীতেন ঘোষ হাতে কাঁচা সোনা তখন অলঙ্কার হয়ে উঠতে শুরু করে, এবং এটাকে ছিল স্বাভাবিক। পল্লীগীতির রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে অনন্তবালার অভিষেক যখন হচ্ছে, সেইসময় এইচএমভি-সূত্রে একটি মাত্র পল্লীগীতি রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা পরবর্তী সময়ে বহুখ্যাত আব্বাসউদ্দিন গেয়েছেন— “আমার হাড় কালা হইল রে দুরন্ত পরবাসে।” ঠিক সেই সময়ে মেগাফোনে ভাটিবাংলার ভাটিয়ালী গানের পসরা জমিয়ে বসলেন অনন্তবালা। যদিও এটা সত্য যে তখন তিনি শুধু ভাটিয়ালী গান গেয়েছিলেন, এমন নয়। গেয়েছিলেন পল্লীবাংলার সবধরনের গান। আসলে তখন পূর্ববাংলার পল্লীগীতিগুলোকেই ভাটিয়ালী বলে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা ছিল শহুরে সমাজে। তাই শুধু ভাটিয়ালী নয়, পূর্ববাংলার লোকসংগীতের একটি সামগ্রিক ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অনন্তবালা।
মেগাফোন কোম্পানিতে অনন্তবালা রেকর্ড করেছিলেন অন্তত দেড়শো গান। অনেকেই বলেন সংখ্যাটা দুশোর বেশি। রণজিৎ সিংহের সঙ্গে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী শিল্পীর নিজের দাবি রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা একশো চল্লিশ। বর্তমান নিবন্ধকার এ-পর্যন্ত যেগুলোর সন্ধান পেয়েছেন, তার সংখ্যা একশো উনিশটি, এর মধ্যে একশো আঠারোটি গান অর্থাৎ উনষাটটি রেকর্ডের JNG নম্বর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে চোদ্দোটি রেকর্ডে রয়েছে আঠাশটি গান, যেগুলো পল্লীগীতি হিসেবে প্রকাশিত। এই পল্লীগীতিগুলোর মধ্যে মানব-মানবীর প্রেমানুভবের প্রকাশ রয়েছে ‘তুমি বিনে আর মনের দুঃখ’, ‘আমার বুকের আগুন’, ‘কোথায় রইলে আমার প্রাণ’ প্রভৃতি কয়েকটি গান। কিন্তু অধিকাংশ গানেই বৈষ্ণবীয় প্রেমানুভব মানবিক প্রেমের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। যেমন উল্লেখ করা যায়— ‘বৃন্দে, বল তোরা আমায়’, ‘সখি, শ্যামবিচ্ছেদে’, ‘কৃষ্ণ প্রেমানলে’ প্রভৃতি গানের কথা। মনে রাখা দরকার সেকালের অনেক গায়ক-গায়িকা স্বধর্মে বৈষ্ণব না হয়েও গানের রেকর্ডিংয়ে অজানা কারণে ‘বৈষ্ণব’ বা ‘বৈষ্ণবী’ উপাধি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ধর্মীয়ভাবেই অনন্তবালার জীবন লালিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় উত্তরাধিকারে। বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত তাঁর কাছে ছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। বিমান মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “অনন্তবালা ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণবী। সাজ-পোশাকে বৈষ্ণবীদের দু’রকম পোশাকই পরতেন। ধবধবে সাদা থান ধুতি, নয়তো গেরুয়া রঙের জামা-ধুতি। মাথায় সবসময় ঘোমটা টানা, কপালে তিলকফোঁটা।” (বিমানে বিমানে আলোকের গানে, বিমান মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার)। শুধু পোশাকে-আশাকে নয়, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বৈষ্ণবের আচার তিনি রক্ষা করছেন, এমন সাক্ষ্যও দুর্লভ নয়। রণজিৎ সিংহ তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার কথায় লিখেছেন, “আমাদের দেখে তিনি বাইরে এলেন। মনে হল তাঁর বয়েস ৭০-এর কাছাকাছি। রোগা ছিপছিপে গড়ন। গলায় তুলসির মালা।… অনন্তবালাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা আর কৃতার্থতার বোধে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। পরক্ষণেই বুঝলাম ভুল করেছি। বৈষ্ণবরা কাউকে পা ছুঁতে দেন না। অনন্তবালাও সঙ্গে সঙ্গে আমার পা ছুঁতে চাইলেন। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।” এই জীবনদর্শন তাঁর চিরসঙ্গী বলেই পল্লীগীতি গাইতে গিয়ে ‘ওরে নিমাই, কোন দোষেতে গেলিরে ছেড়ে’-র মতো গানে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন চিরায়ত মাতৃহৃদয়ের হাহাকার।
ভাটিবাংলার ভাটিয়ালী গান পারিবারিক ও স্থানিক উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন অনন্তবালা। ‘একদিন দেখেছি যারে’ কিংবা ‘মনের পিপাসায় যত কাঁদব’ স্বাভাবিক ভাটিয়ালী হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু ভাটিয়ালী সুরে তাঁর যে দুটো গান একদা গোটা বাংলাদেশকে আলোড়িত করেছিল, তার একটি ‘নিমাই দাঁড়ারে, দেখিব তোমারে রে’ অপরটি ‘যশোদে, মা তোর কৃষ্ণধনরে দে মা গোষ্ঠে নিয়ে যাই।’ ভাটিয়ালী সুরে এখানেও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ। আর ভাষার উচ্চারণে ভাটিবাংলার মাটির গন্ধ লেগে আছে। পূর্ব-গোষ্ঠের সখ্যরসের গানটি কোনো শ্রোতা নিবিড়ভাবে গানটি শুনলে অনন্তবালার আঞ্চলিক উচ্চারণগুলোর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করতে পারবেন। অনন্তবালা গাইছেন ‘সব রাখালে গিছে চলে’-এখানে ‘গিছে’ উচ্চারণটি কিংবা ‘হায় মণিগণের দ্বারে দ্বারে’-তে ‘মুণি’ নয় ‘মণি’ উচ্চারণ ভাটিবাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে মাটিলগ্ন। কিংবা পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ-রীতি মেনে ‘কে’ নয় ‘রে’ বিভক্তির ব্যবহার- ‘সে ফল আমরা না খাই কানাইরে খাওয়াই’। তার বিভিন্ন গানেই এই প্রবণতা ছড়িয়ে রয়েছে। ‘গ্রাম্যগীতি’ কিংবা ‘গ্রাম্যসঙ্গীত’ উল্লেখ করে সবচেয়ে বেশি গান অনন্তবালা গেয়েছেন। গ্রামীণ জীবনে মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ-মিলন, আনন্দ-বেদনা এসবের উপজীব্য। এমনকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুষঙ্গে রচিত গানেও তো মানবিক প্রণয়ের বেদনা বাঙালি উপেক্ষা করতে পারেনি কখনও। অনন্তবালা গেয়েছেন “কালা আমায় পাগল কইরাছে রে ঘরে রই কেমনে?” আবার এই গ্রামগীতির মধ্যে একধরনের দার্শনিক উপলব্ধির গানও গাওয়ানো হয়েছে তাঁকে দিয়ে এবং সসম্মানে তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। এমন একটি গান—
‘ঘরে বাইরে সুহৃদ না থাকিলে রে
ও তার মনের দুঃখ হয় না নিবারণ।
ও তার না জোটে পিরিত,
ঘটে সকল বিপরীত,
মাঝে চলে বিচ্ছেদ দুঃশাসন।।’
কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে অনন্তবালার গাওয়া ইসলামী গানের রেকর্ড-প্রসঙ্গ। বাংলাভাষায় ইসলামী গানের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের মনের মধ্যে দুজন মানুষের নাম প্রায় অনিবার্যভাবে ভেসে ওঠে— আব্বাসউদ্দিন ও নজরুল ইসলাম। ইসলামী গানের এই জগতে তৃতীয় স্মরণীয় নামটি অবশ্যই অনন্তবালা বৈষ্ণবী। মহিলা শিল্পী হিসেবে তিনিই প্রথম ইসলামী গানের রেকর্ড করেন ১৯৩৮-এই, প্রথম গানটির শুরু ছিল এরকম— ‘হল রে দোজাহান উজালা’। এর পর একে একে গেয়েছেন ‘মুর্শিদ প্রেমের পাকা রঙে’, ‘আহারে খোদার বান্দা’ প্রভৃতি প্রায় চব্বিশটি গান। মুসলিম সমাজ যখন গান শুনলেই কানে তুলো লাগানোর মতো আচরণ করছে, তখন একজন হিন্দু-বৈষ্ণবীর স্বনামে (অনেক হিন্দু শিল্পী মুসলমান নামে ইসলামী গান গাইতেন) গাওয়া ইসলামী গান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে, এটা বিস্ময়কর বটেই। এসব গানের মধ্যে জনপ্রিয়তায় সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল ‘ধনি প্রেম করতে পারবি কি তোরা’ (JNG 5053)। জানা যায় দুদিনে পাঁচশো রেকর্ড বিক্রি হয়ে যায়। গানের কথাগুলো ছিল এরকম—
“ধনি, প্রেম করতে কি পারবি তোরা
আমার নূরনবী জগতের পতি, প্রেমেতে সে হল্ করা।
প্রেমের তত্ত্ব জেনে নবী ধরে আনে চৌদ্দ বিবি
টের পায় না মুনশী মৌলবী জনরা।।
গানটি নিয়ে বিতর্ক হয়। গানটিতে ‘চৌদ্দ বিবি’ শব্দের ব্যবহার ঠিক নয়। ওখানে ‘এগারো বিবি’ শব্দবন্ধ চলতে পারে— এরকম একটা দাবি তিনি উত্থাপন করালেন কুষ্টিয়ার একজন মাওলানা। সেই অনুযায়ী নতুন রেকর্ড তৈরির কথা ভাবা হলেও কুষ্টিয়া আদালতে মাওলানা সাহেব অভিযোগ করেন। অভিযোগ ছিল দুটো ‘চৌদ্দ বিবি’ যথার্থ প্রয়োগ নয় এবং এটা ইসলাম-বিরোধী। দাবি ছিল হিন্দুর মেয়ে ইসলামী গান গাইতে পারবে না। এক বছর মামলা চলে, কোম্পানি হেরে যায়, পুলিশ রেকর্ডগুলো ভেঙে দিয়ে যায়। মানসিকভাবে জীতেন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার যেমন তেমনই অনন্তবালাও ভেঙে পড়েন। শোনা যায়, অনন্তবালা পনেরোদিন বিছানা থেকে ওঠেননি। এই কারণে আর দুজন মানুষ আঘাত পেয়েছিলেন, তাঁদের একজন মঙ্গল ফকির, গানের রচয়িতা ও অনন্তবালার পিতৃপ্রতিম। আর একজন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। একাধিকবার অনন্তবালার কাছে তিনি ক্ষোভ ও অনুতাপের কথা জানিয়েছেন। তবে এই ঘটনার পেছনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটা একজন কবি ও মেগাফোনের মালিকের অহংবোধের লড়াই।
অনন্তবালা গানের শিল্পী ছিলেন, গানের কথা বা বাণীর লেখিকা ছিলেন না, এমনটাই প্রচলিত ধারণা। তিনি গান গেয়েছেন মঙ্গল ফকির, ভবানী দাস, ঈশান দাস, প্রমুখের কথা বা বাণীতে। এসব গানের একটা বড়ো অংশ সুর করেছেন ও তাঁকে শিখিয়েছেন পরেশ দেব। গেয়েছেন ভবানী দাসের সুরেও। স্বয়ং নজরুল ইসলামের কথা, সুর ও তাঁর তত্ত্বাবধানে অনন্তবালা অন্তত দুটি গান গেয়েছিলেন জানা গেছে। এগুলোর একটি হলো—
“খোদার রহম চাহ যদি নবীজীরে ধর।
নবীজীরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়।”
১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে গানটির প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তবে কিন্তু কিছু গান যে তিনি নিজেও লিখেছিলেন, এমন তথ্যের একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে রণজিৎ সিংহের একটি রচনায়। ১৯৬৯-এর ২৬ জুন খালেদ চৌধুরী, অধ্যাপক সৌম্য চক্রবর্তী আর রণজিৎ সিংহ কৃষ্ণনগরে দেখা করেছিলেন অনন্তবালার সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে রণজিৎ সিংহ লিখেছেন, “অনন্তবালা গানও রচনা করেছেন। তাঁর রেকর্ডের কিছু কিছু গানে ‘অনন্ত তাই ভেবে বলে’ বা ‘অনন্ত ভেবে বলে’ ভণিতা শোনা যায়।” (মাটির সুরের খোঁজে, অনন্তবালা, প্রতিক্ষণ)।
সাধারণ লেখাপড়ার সামান্য সুযোগ যে তিনি গ্রামের বাড়িতে পেলেও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আব্বাসউদ্দিন বা শচীন দেববর্মণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ অনন্তবালা পাননি। তাছাড়া ওঁদের মতো আর্থিক সঙ্গতির সুযোগ ছিল না অনন্তবালার জীবনে। শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর আর্থিক দীনতা কেটেছিল, এটা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু বেহিসেবি খরচ, দান-ধ্যানে সে অর্থ সঞ্চয় করবার মানসিকতা তাঁর কতটা ছিল, এ প্রসঙ্গে সংশয় জাগে।
এতদসত্ত্বেও বাংলা লোকসংগীতের জগতে অনন্তবালা ছিলেন আপন মহিমায় উজ্জ্বল। কমলা ঝরিয়ার মতো শিল্পী ‘অনন্তদি’-র কথায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সাক্ষাৎকারে আঙুরবালা বলেছিলেন, অনন্তবালা বৈষ্ণবীর ভাটিয়ালী-পল্লগীতি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত। রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন অনন্তবালার গুণমুগ্ধ শ্রোতা, যিনি বিমান মুখোপাধ্যায়কে অনন্তবালার গান বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, একথা জানিয়েছেন স্বয়ং বিমানবাবু। সেই অনন্তবালা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন মূলত দেশভাগ-জনিত কারণেই। দেশভাগের আগে বরিশালের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু ছিল তা একবারে চুকেবুকে গেল। অনন্তবালা প্রথমে ঠাঁই নিলেন নদিয়ার বেতাই নামক স্থানে একটি উদ্বাস্তু কলোনিতে। তারপর কৃষ্ণনগর রোড স্টেশনের কাছে গড়ে তুললেন ছোট্ট আবাস, তৈরি করেছিলেন তাঁর আরাধ্য রাধামাধবের মন্দির। পূর্ববাংলার বিপুল শ্রোতার কাছে তাঁর গান পৌঁছনোর পথ বন্ধ। ফলে রেকর্ডের গানে ভাটিয়ালীতে তখন ভাঁটার টান। বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে গানকেই অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন তিনি। আকাশবাণীর (All India Redio) একটানা সাত বছরের শিল্পী গিয়েছিলেন গান গাইতে আকাশবাণীতে আর একবার। কিন্তু নতুন করে অডিশন দেবার কথা বলতেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে। ভেতরে হয়তো গুমরে কাঁদছিল অভিমান, কার কাছে দেবেন তিনি ভাটিয়ালীর পরীক্ষা?
কিন্তু ১৯৬৯-এর সময়কালের বারো-তেরো বছর আগে থেকেই ‘কোম্পানি আর কোনো টাকা-পয়সা দেয় না। দশ-বারোখানা রেকর্ডের স্বত্বও আছে তাঁর, রয়্যালিটি পাওয়ার কথা। তাও আর পান না।’ এই বাস্তবতাকে ভবিতব্য করে কিছু ভক্ত-অনুরাগীদের সাহায্যে অনন্তবালা বেঁচেছিলেন বাংলা ১৩৮৫-র আষাঢ় মাস পর্যন্ত। ইংরেজি ১৯৮৮ সালে তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু কত তারিখে সেই নির্দিষ্ট দিনের সন্ধানটাও অজানা রয়ে গেছে। সময়ের সংকট শিল্পীকেই শুধু গ্রাস করেনি, গ্রাস করেছে শিল্পকেও। আমাদের মনে পড়ে যায় বিজন ভট্টাচার্যের ‘রাণীপালঙ্ক’ উপন্যাসের যুগীবর সূত্রধরকে। দেশভাগের আগে যে মানুষটি শিল্পীর অহমিকা নিয়ে রাণীপালঙ্ক তৈরি করত, দেশভাগের পরে সেই যুগীবরের শিল্পীসত্তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তুচ্ছ খাট বা খাটিয়া তৈরিতে। শুধু শিল্পী নয়, দেশভাগ শিল্পকেও করেছে উদ্বাস্তু। অনন্তবালার অনন্ত যাত্রাপথের বিষাদছায়ায় কি উদ্বাস্তু শিল্পটিও আমাদের একবিংশের বন্ধ্যাদশার কাছে পরাজিত হয়নি?