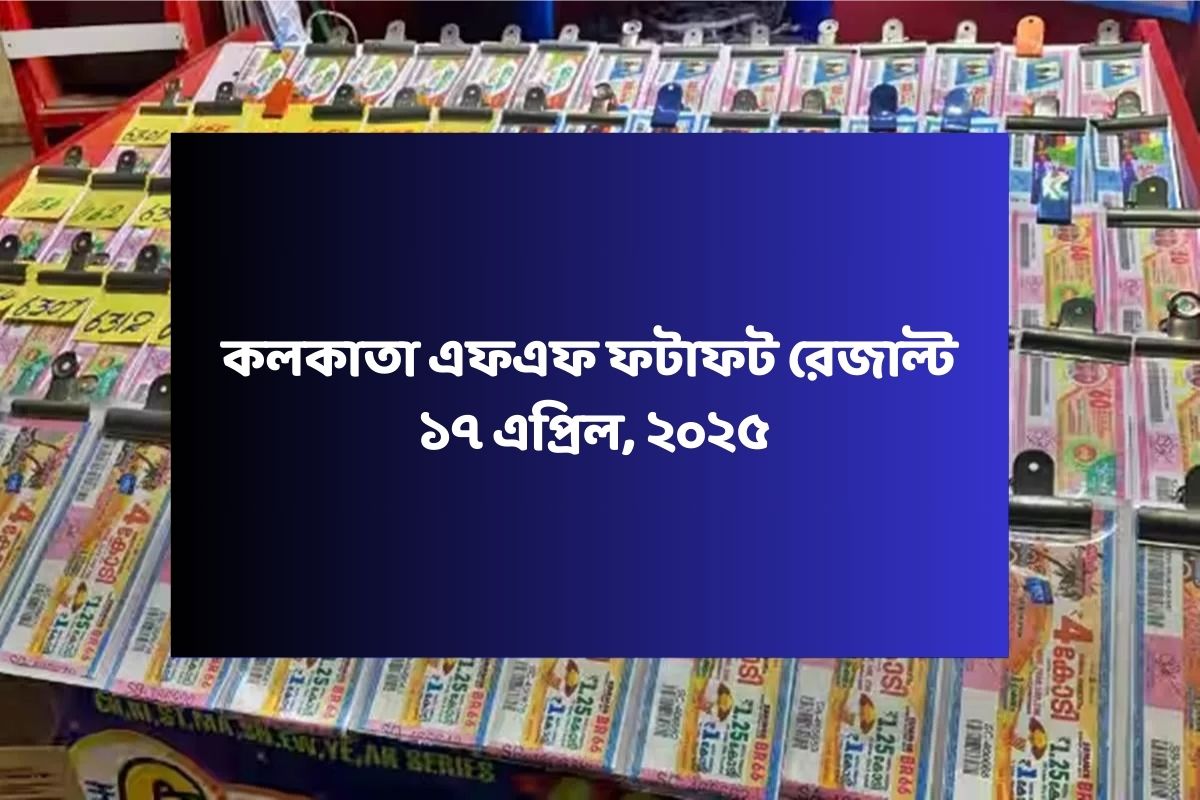সজল দে
এক তুমুল ঝড়জলের রাতে তাঁর জন্ম, ঢাকা শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে বাঁশাই নদীর তীরবর্তী গ্রাম শেওড়াতলিতে। দিনটা ছিল ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর। প্রকৃতির প্রতিকূল প্রতিবেশে ক্ষুব্ধ মেঘগর্জনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হন তিনি, সে-কারণে দিদিমা নাম রাখেন মেঘনাদ। নবজাতকের এই নাম পরিণত বয়সে সার্থক প্রমাণিত হয়েছিল। অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা, অসহিষ্ণু, ঋজু ও অনমনীয় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন মেঘনাদ, অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি সবেগে ধাবমান হওয়া ছিল তাঁর চরিত্রের অঙ্গ। পরবর্তী জীবনে কারও কারও সঙ্গে মেঘনাদের বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর আচরণ ও ভাষণ।
তথাকথিত উচ্চবংশের সন্তান ছিলেন না, পিতা জগন্নাথ সাহার একটি মুদির দোকান ছিল স্থানীয় বলাইদি বাজারে। পরিবারের নিত্যসঙ্গী ছিল দারিদ্র। সব পুত্রের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি জগন্নাথ, তার প্রয়োজনও বোধ করেননি; কিন্তু মেঘনাদের ক্ষেত্রে অন্যথা হয়েছিল। অত্যন্ত মেধাবী হবার কারণে, শিক্ষার্জনের প্রতি অদম্য আগ্রহে, মা ও দাদা জয়নাথের সমর্থন এবং সহায়তায় মেঘনাদ সাফল্যের সঙ্গে গ্রামের বিদ্যালয়শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বৃত্তি পেয়ে বারো বছর বয়সে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন তিনি। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে সময়টা ছিল অগ্নিগর্ভ, সদ্য প্রথম বঙ্গভঙ্গ ঘটেছে এবং তার প্রতিবাদে ফুঁসছে মানুষ। এই সময় গভর্নর স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার স্কুল পরিদর্শনে এলে তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ ওঠে। অনেক ছাত্রকে শাস্তির মুখে পড়তে হয়, মেঘনাদ ও তাঁর সহপাঠী নিখিলরঞ্জনকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। যদিও মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত মেঘনাদের শিক্ষার অগ্রগতি তাতে আটকানো যায়নি, বেসরকারি বিদ্যালয় কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল তাঁকে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডেকে নেয়।
বিদ্যালয় স্তর থেকেই গণিত ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়, তার পরে ইতিহাস। সাহিত্যের মধ্যে মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করেও লড়াই করার স্পৃহা তাঁকে সবসময়ই উদ্বুদ্ধ করত। ছোটোবেলা থেকেই যে-জাতবৈরিতার ও অবহেলার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন উচ্চবর্ণের অনেক মানুষের কাছে, তা সারাজীবনের মতো তাঁর ওপর ছাপ রেখে গিয়েছিল।
এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য) পূর্ববঙ্গের মধ্যে প্রথম হয়ে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন আইএসসি পড়ার জন্য, সেটা ছিল ১৯০৯ সাল। একজন ভিয়েনা-ফেরত অধ্যাপকের কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জার্মান ভাষার তালিম নেওয়া শুরু করেন। আইএসসি পরীক্ষায় সব মিলিয়ে মেঘনাদ তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও গণিত ও রসায়নবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। তারপর ঢাকা ছেড়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে আসেন তিনি। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরের শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন মেঘনাদ, সেখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মতো উজ্জ্বল কয়েকটি নাম। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও নীলরতন ধর ছিলেন তাঁর থেকে সিনিয়র এবং সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন প্রিয় জুনিয়র ছাত্র। আর শিক্ষক হিসাবে মেঘনাদ পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো বিজ্ঞানসাধকদের। কলকাতায় তিনি ইডেন হস্টেলে থাকতেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে ওই ছাত্রাবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। জাতপাতজনিত অবহেলা ও বৈষম্য তাঁকে সেখানেও সইতে হচ্ছিল। বন্ধুদের সহায়তায় বিকল্প একটি যৌথ বাসার বন্দোবস্ত হয়। এই সময়েই তিনি বিপ্লবী পুলিন দাস ও বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন এবং অনুশীলন সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পুলিনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন আগে থেকেই, তবে এখন সক্রিয় বিপ্লবী হিসেবে নতুন করে তাঁর ঘনিষ্ঠ হলেন। বিজ্ঞানকে মেঘনাদ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু একইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য তাঁর ভাবনা ও ভূমিকা কম ছিল না।
১৯১৩ সালে দামোদর উপত্যকায় এক বিধ্বংসী বন্যা হয়। বন্যার্তদের ত্রাণ ও সেবা দিতে প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে যান তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের নিয়ে, সেই দলে ছিলেন স্নাতকোত্তর ছাত্র মেঘনাদ। বাল্যকালে গ্রামের নদীতে বন্যা তিনি দেখেছিলেন, সেই সুবাদে কিছুটা ধারণা তাঁর ছিল। এখন এই তুমুল প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ংকরী রূপ দেখে মেঘনাদ ভাবলেন, এ কী বিপুল অপচয়! ঠিকমতো ব্যবহার করা গেলে মানুষের কত কাজে আসতে পারত এই বিশাল শক্তিভাণ্ডার। বিজ্ঞানী তথা সমাজচিন্তক মেঘনাদের সূত্রপাত এই মুহূর্তটি থেকে। এর ঠিক দশ বছর পরে, ১৯২৩ সালে, দামোদর নদীতে পুনরায় ভয়াবহ বন্যা হয়; সেবারও তিনি ত্রাণকার্যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেন। নদী-পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর অধ্যয়ন ও ভাবনা ক্রমশ গভীরতা পেতে থাকে। ১৯২২ সালেই তিনি বন্যার পদার্থ-বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করে ‘মডার্ন ফিজিক্স’ জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি এ-ও দেখান বিজ্ঞান কীভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। ১৯৩২ সালে আরেকটি প্রবন্ধ মেঘনাদ লিখলেন ‘বাংলায় জলগতিবিজ্ঞান গবেষণা পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা’ নামে।
পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনা দামোদর সহ অন্যান্য অনেক নদীতে বাঁধ দেওয়া সমেত বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও পরে লক্ষ করা গেছে— যেভাবে এইরকম নদী পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা হয়েছিল তার ফলাফল প্রকৃতি, দেশ ও মানুষের জন্য সবটাই ধনাত্মক ছিল না। সাম্প্রতিক সময়ের একটি বড়োসড়ো নঞর্থক উদাহরণ হল নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত সর্দার সরোবর বাঁধ, অনেক আন্দোলন করেও যেটির নির্মাণ আটকানো যায়নি। বিশাল এলাকা জুড়ে অরণ্য, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাসভূমি ও জীবন-জীবিকা ওতে ডুবে গেছে। বড়ো বাঁধগুলি সামাজিক ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
ফিরে আসা যাক মেঘনাদের শিক্ষাজীবনে। ১৯১৪ সালে গণিতে স্নাতক (সাম্মানিক) ও ১৯১৬ সালে মিশ্র গণিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ হন মেঘনাদ, কিন্তু দুটি পরীক্ষাতেই তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন– দুটিতেই প্রথম হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক অদ্ভুত সম্পর্ক চিরকালই বজায় ছিল।
১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ছাত্রদের নিয়ে যোগ দেন সেখানকার রসায়ন বিভাগে। প্রায়োগিক গণিত বিভাগের তরুণ লেকচারারদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা, কেননা এঁরা দুজনেই মূলত গণিতের ছাত্র ছিলেন। পরে অবশ্য দুজনেই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে স্থানান্তরিত হন। এই দুই বিজ্ঞানী বন্ধু ও সহকর্মী মিলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ‘আপেক্ষিকতার তত্ত্ব’ জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ করেন ইংরেজিতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই অনুবাদ ১৯১৯ সালে প্রকাশ করে। সেটাই ছিল পৃথিবীতে ‘আপেক্ষিকতা তত্ত্ব’-র প্রথম ইংরেজি অনুবাদ।
বৈজ্ঞানিক সি ভি রমন লোক-মারফৎ খবর পাঠিয়ে মেঘনাদকে ডেকেছিলেন তাঁর অধীনে গবেষণাকর্ম করার জন্য, কিন্তু মেঘনাদ রাজি হননি। ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অধ্যয়নের ভিত্তিতেই তিনি নিজের গবেষণামূলক কাজ শুরু করলেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র ‘ম্যাক্সওয়েলের চাপ বিষয়ে’ প্রকাশিত হল ১৯১৭ সালে ‘ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন’ নামক পত্রিকায়, এটি ছিল বিকিরণের তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বের ওপর একটি কাজ। এরপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে মেঘনাদের গবেষণাপত্র একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। যথাযথ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের ও ভালো পরীক্ষাগারের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন উপায়ে নিজের গবেষণা চালিয়ে যান মেঘনাদ এবং ১৯১৮ সালে নিজের থিসিস জমা দেন। তার ভিত্তিতে পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯১৮ সালের ১৬ জুন বিবাহ করেন মেঘনাদ, পাত্রীর নাম রাধারাণী রায়। পাত্র গরিব পরিবারের সন্তান বলে রাধারাণীর ঠাকুমার এই বিবাহে আপত্তি ছিল, কিন্তু কন্যার পিতা এমন বিদ্বান জামাতা পেতে খুবই আগ্রহী ছিলেন।
১৯১৯ সালের শেষ নাগাদ মেঘনাদ নিজের পছন্দের বিষয়ে তাঁর স্থান পাকাপোক্ত করে ফেলতে সক্ষম হন। পরের বছর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে তিনি চারটি গবেষণাপত্র পাঠান ‘ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন’ জার্নালে। এই গবেষণাপত্রগুলির সারসংক্ষেপ ও একটি ভূমিকা প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে ‘জার্নাল অভ্ দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি’-তে। এই কাজগুলির মধ্যেই মেঘনাদ তাঁর ‘তাপীয় আয়নকরণ তত্ত্ব’ প্রণয়ন করেন, যার ফলে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বলা হয়ে থাকে, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে নতুন বিদ্যা জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা মেঘনাদ সাহারই কৃতিত্ব।
১৯১৯-এ ‘নাক্ষত্রিক বর্ণালির হার্ভার্ডীয় শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে’ তাঁর গবেষণা-নিবন্ধের জন্য রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান মেঘনাদ, এ-ছাড়াও গুরুপ্রসাদ ঘোষ পরিভ্রমণ বৃত্তি তাঁকে দেওয়া হয়। সেই অর্থ সম্বল করে বিলেত পাড়ি দেন মেঘনাদ। ভালো কোনও পরীক্ষাগারে নিজের তত্ত্বটির যথোপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও অন্যান্য গবেষণার জন্য বিদেশ যাওয়া জরুরি ছিল তাঁর কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কারের জন্য ‘নাক্ষত্রিক বর্ণালিতে রেখাসমূহের উদ্ভব সম্বন্ধে’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠান মেঘনাদ, যেটি পুরস্কৃত হয় এবং রয়্যাল সোসাইটির বিবরণীতে প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। মজার কথা হল, এই প্রবন্ধে লেখক হিসেবে হেলিওফিলুস (Heliophilus) ছদ্মনাম ব্যবহার করেন তিনি। সেটিই তখনকার রীতি ছিল।
১৯২১ সালে বার্লিন থেকে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর ঈপ্সিত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, গবেষণাগার ও সহকারী না পাওয়া নিয়ে তাঁর ক্ষোভ ছিল। ফলে দুই বছর পরে সেই আশায় তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। সেখানেও প্রথমদিকে যথেষ্ট গবেষণা-সহায়ক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় অর্থ পাননি এই বিশ্বমানের বিজ্ঞানী। চিরকালই নতুন ইন্সটিটিউট, গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক সবকিছু পাবার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে; বারংবার কর্তৃপক্ষের মাথায় এসবের প্রয়োজনীয়তা ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মেঘনাদ এলাহাবাদ যাবার পনেরো বছর পরে কলকাতায় ফিরে পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক হন, তাঁর আগে এই পদটি সি ভি রমনের অধিকারে ছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে তাদের ফেলো ঘোষণা করে সম্মান প্রদান করে।
পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের কারণে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম পাঁচ বার মনোনয়ন পেয়েছিল— ১৯৩০, ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৫১ এবং ১৯৫৫ সালে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, শেষপর্যন্ত ওই পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়নি। ঠিক কী কারণে তাঁকে এই অবহেলা সইতে হল, সে-প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। একটা মত হল তিনি নাকি নতুন কিছু ‘আবিষ্কার’ করেননি! আসলে, আবাল্য ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার ও বৈপ্লবিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই কূটনৈতিক স্তরে এই বঞ্চনা ঘটেনি তো! এমনকী মেঘনাদ সাহাকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করাতে ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি ছিল, সে তথ্য জানা গিয়েছে। নোবেল পুরস্কার কমিটিরও অনেক সিদ্ধান্তই বিতর্কের উর্দ্ধে নয়, আগেও ছিল না, এখনও না। একইরকমভাবে স্মরণ করা যেতে পারে জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত বিজ্ঞানীদেরও নোবেল কমিটি উপেক্ষা করেছিল। কেবল বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার কথা বললে মানুষটির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না।
দেশগঠনের প্রেক্ষাপটে সমাজ-চিন্তক ও বিজ্ঞান-সংগঠক মেঘনাদের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই বলেছেন, ১৯৩০-এর পর তিনি বিজ্ঞানীর সুউচ্চ পাদপীঠ থেকে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসেন দেশ ও মানুষের স্বার্থে। মেঘনাদ বুঝেছিলেন কেবল তিনি নিজে ভাবলেই হবে না, অন্যদের— বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষমতাবান লোকেদের— না ভাবাতে পারলে দেশের তথা বিজ্ঞানের কাজ এগোবে না। ক্রমাগত সে-চেষ্টা তিনি করে গেছেন। জাতীয় নেতাদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। তবে মেঘনাদ মোহনদাস গান্ধির ‘চরকায় সুতো কাটা’ অর্থনীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এইসব মান্ধাতার আমলের নীতি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে বলে তিনি মনে করতেন, এবং তা নিয়ে তিনি কখনোই নীরব থাকেননি।
মেঘনাদ সাহার সক্রিয় উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ১৯৩০ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গলের আদলে এলাহাবাদে সংযুক্ত প্রদেশ বিজ্ঞান আকাদেমি স্থাপিত হয়। তিনিই আকাদেমির প্রথম সভাপতি হন। ১৯৩৪ সালে আকাদেমির নাম পরিবর্তিত হয়ে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি হয়।
১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গেলেন মেঘনাদ এবং দেশের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর কী পরিকল্পনা আছে জানতে চাইলেন। আপাতভাবে স্বাধীনতা পাবার আগেই তেমন কোনও পরিকল্পনা কংগ্রেসের কারুর ছিল না। তখন মেঘনাদ সুভাষচন্দ্রের কাছে নিজের চিন্তাভাবনার মেলে ধরেন। তাঁর কথায় সম্মত হয়ে সুভাষ একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করতে উদ্যোগ নিলেন। ওই বছরই অক্টোবর মাসে দিল্লিতে একটি মিটিং হবার সিদ্ধান্ত হল, যেখানে মেঘনাদও আমন্ত্রিত ছিলেন। একদিন পরে পৌঁছে মেঘনাদ দেখলেন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে, আর তার চেয়ারম্যান করা হয়েছে স্যর এম বিশ্বেশ্বরাইয়াকে। এই সিদ্ধান্ত মেঘনাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি জানতেন, কংগ্রেসের কোনও শীর্ষ নেতা ওই পদে না থাকলে পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ কংগ্রেসের কাছে কোনও গুরুত্ব পাবে না। অতএব বিশ্বেশ্বরাইয়া সরে গেলেন এবং অনেক বোঝানোর পর নেহরু ওই কমিটির প্রধান হতে স্বীকৃত হলেন। মেঘনাদ নিজে শান্তিনিকেতন গেলেন রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে, যাতে তিনি মোহনদাস গান্ধিকে বুঝিয়ে এই প্রস্তাবে রাজি করান।
গঠিত হবার পর কমিটি দ্রুত তার কাজ শুরু করেছিল। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে টি সাহা এর সাধারণ সম্পাদক হন, মেঘনাদ ইন্ধন ও শক্তি-বিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান হয়ে যান। মূল কমিটির সদস্য হবার পাশাপাশি তিনি নদী-নিয়ন্ত্রণ ও সেচ উপকমিটির সদস্যও ছিলেন। কমিটির শেষ বৈঠক হয়েছিল নয়াদিল্লিতে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে। ছাব্বিশ খণ্ডের একটি বিশাল অন্তর্বর্তী রিপোর্ট বানিয়ে কমিটি জমা দেয় তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি পট্টভি সীতারামাইয়াকে। এই কমিটির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে সেটিকে ভেঙে দেওয়া হয়।
ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন, এখন নেহরু ও অন্যান্য নেতাদের ধরে জেলে ঢোকাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু বড়ো মাত্রায় যন্ত্রশিল্পায়নের চিন্তা নেহরুর মাথায় এতটাই প্রবেশ করেছিল যে, আহমদনগরের কারাগারে বসেও তিনি জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছেন ও লিখেছেন। ওখানে বসে লেখা তাঁর The Discovery of India বইতে এই কমিটির অধিবেশনগুলি ও তার কার্যকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। স্বাধীনতার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাঁর নেতৃত্বে ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মহাযজ্ঞ শুরু হবে, তবে শুরুর শুরু ছিলেন মেঘনাদ এ-কথা অনস্বীকার্য।
মেঘনাদ সাহার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি শেষ পর্যন্ত সরকারের ওপর এতটাই চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় নদী-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ওই বছরই দামোদর নদে পুনরায় বন্যা হলে মেঘনাদ একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তাঁর দ্বারা উদ্ভাবিত ‘সায়েন্স অ্যান্ড কালচার’ পত্রিকা এই ব্যাপারে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা পালন করে; বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও বিশেষজ্ঞ মতামত প্রকাশের মাধ্যমে সেই সময়কার এবং স্বাধীন ভারতের সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এই পত্রিকায় ১৯৪৪ সালে কমলেশ রায়ের সঙ্গে মিলে মেঘনাদ ‘দামোদর উপত্যকার জন্য পরিকল্পনা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার জন্য পৃথিবীর অনেক সফল ও অসফল বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা নিয়ে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেন, তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি উপত্যকা সিস্টেমের ওপর। সাহা ও রায় তাঁদের লেখা প্রবন্ধে দামোদরের ওপর বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্য কয়েকটি স্থান চিহ্নিত করেন।
এমন-কী মেঘনাদ তখনকার ভাইসরয়ের ক্যাবিনেটের সদস্য বি আর আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করে দামোদর উপত্যকার নদী-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেন। তাঁর ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন (DVC) গঠিত হয় স্বাধীনতার পরপরই, কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে। যদিও এই বাঁধ নির্মাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা অচিরেই শুরু হয়েছিল। প্রধান সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন প্রযুক্তিবিদ কপিল ভট্টাচার্য, কুমুদভূষণ রায় এবং অন্যান্যরা। দীর্ঘ মেয়াদে বড় বাঁধের সুফল অপেক্ষা কুফলের পরিমাণ এতটাই বেশি হয় এবং এতটাই স্পষ্টভাবে তা দেখা যাচ্ছে আজকের দিনে যে, মেঘনাদ সাহার মতো মেধাবী মানুষ এসব আন্দাজ করতে পারেননি ভাবতে কষ্ট হয়। বিজ্ঞানের সাফল্য তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল? প্রকৃতির ওপর বিজ্ঞানের বিজয়ের তত্ত্বকে তিনি এতটাই বিশ্বাস করতেন? কোন শ্রেণীকে শোষণ করে কোন শ্রেণীর উন্নয়নে এই বাঁধগুলি সহায়ক হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেননি? প্রশ্ন থেকে যায় অনেকগুলি।
তার আগেই, ১৯৪৫ সালে মেঘনাদ সাহা সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান আকাদেমির আমন্ত্রণ পান তাদের ২২০তম জয়ন্তী উৎসবে যোগ দেবার জন্য। সেই সুবাদে তিনি ‘রহস্যাবৃত দেশ’ রাশিয়া ভ্রমণ করেন এবং যতখানি সম্ভব মনোযোগ দিয়ে সোভিয়েত সমাজের ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর ভ্রমণকাহিনী ‘My Experiences in Soviet Russia’-তে তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মেঘনাদ। এই ভ্রমণকাহিনি একটি রীতিমত ঐতিহাসিক দলিল, নিছক বেড়ানোর গল্প নয়। বিপ্লব-পরবর্তী রুশদেশে সোভিয়েতের বিপুল কর্মকাণ্ড দেখে তিনি নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারেননি, অত্যন্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বারবার পরিসংখ্যান সহকারে তুলনা করে দেখিয়েছেন, ইউরোপের তুলনায় বেশ পশ্চাদপদ অবস্থানে থেকেও রাশিয়া কীভাবে নিজেকে চমকপ্রদভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এবং কীভাবে তাঁর দেশ ভারত রুশীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে। বিষেশত সোভিয়েত রাশিয়ার নদী পরিকল্পনা ও তার শক্তি উৎপাদনের খুঁটিনাটি মেঘনাদ প্রযুক্তিগত ভিত্তিসহ বিশদে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানতেন, ভারতের খনিজ ও জলসম্পদ কম তো নয়ই, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশি। সেই সম্পদের যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার হলে এদেশ আর গরিব অথবা পিছিয়ে পড়া থাকবে না বলে তিনি মনে করেছিলেন। তবে কাজে নামবার আগে একটি সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ জরুরি ছিল, যেটির জন্য তিনি বরাবর সরব ছিলেন। আজকের দিনে ভারতের মাটিতে বিজ্ঞান গবেষণা ও তার ভিত্তিতে যন্ত্রশিল্পায়ন যতটুকু এগিয়েছে সে-সবের জন্য মেঘনাদ ও তাঁর গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। যদিও কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বয়ংভর করার গান্ধিবাদী নীতির ব্যাপারে ওঁদের মতামত ছিল পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত।
নেহরুর সঙ্গে মেঘনাদ সাহার সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটে, দেশ স্বাধীন হবার পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ও শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের প্রতি বেশি আগ্রহী হন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ফলে জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান পরিকল্পনায় প্রধান কোনও ভূমিকা আর তাঁকে দেওয়া হয়নি। তার মধ্যেই অন্য অনেকের সহায়তা নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে কলকাতায় নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট স্থাপন করেন। ১৯৫০ সালের ১১ জানুয়ারি এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আইরিন জুলিও কুরি, যিনি মাদাম কুরির কন্যা এবং নিজেও ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজেতা।
নদী পরিকল্পনাগুলি যে ঠিকমতো কার্যকর হচ্ছে না এবং পরিকল্পনা স্তরেই কিছু গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে তা মেঘনাদ বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কীভাবে নিজের প্রতিবাদ, নিজের কথা তখনকার কর্তাদের কানে পৌঁছে দেবেন তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি জানতেন সংসদই একমাত্র জায়গা যেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নিজের মতপ্রকাশ করা যায়। অতএব, অন্য অনেকের পরামর্শ মেনে তিনি ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে বাম-সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সংসদে প্রবেশ করেন মেঘনাদ। ১৯৫৬ সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি সক্রিয় সাংসদের ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।
খ্যাতির অত্যুচ্চ শিখরে উঠলেও পূর্ববঙ্গে নিজের গ্রামকে কখনও ভোলেননি মেঘনাদ, নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তার ওপর দেশভাগের ভয়াবহ অভিঘাতে যখন উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের দলগুলি ঢেউয়ের মতো কলকাতা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে আছড়ে পড়তে লাগল, তিনি বিচলিত হলেন। ১৯৫০ সালে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হল পূর্ববঙ্গ শরণার্থী ত্রাণ সমিতি। অশক্ত শরীর নিয়েও তিনি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। উদ্বাস্তুদের বাস্তব সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণ ও ভারত সরকারকে একাধিকবার অবহিত করেছেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে তাঁর অসময়ের মৃত্যুতে দেশ শুধু একজন বৈজ্ঞানিক হারায়নি, হারাল এক জনদরদী যুক্তিবাদী সামাজিক সংগঠক ও কর্মীকেও।